-
পরবাস
বাংলা ভাষা, সাহিত্য ও সংস্কৃতি
Parabaas, a Bengali webzine since 1997 ... ISSN 1563-8685 -
ছোটদের পরবাস
Satyajit Ray
Rabindranath Tagore
Buddhadeva Bose
Jibanananda Das
Shakti Chattopadhyay
সাক্ষাৎকার -
English
Written in English
Book Reviews
Memoirs
Essays
Translated into English
Stories
Poems
Essays
Memoirs
Novels
Plays
-

পুত্রবধূর চোখে গৌরী আইয়ুব এবং প্রসঙ্গত
-

বিশ্বের ইতিহাসে হুগলি নদী
-

বেদখল ও অন্যান্য গল্প
-

Audiobook
Looking For An Address
Nabaneeta Dev Sen
Available on Amazon, Spotify, Google Play, Apple Books and other platforms.
-

পরবাস গল্প সংকলন-
নির্বাচন ও সম্পাদনা:
সিদ্ধার্থ মুখোপাধ্যায়)
-

Parabaas : পরবাস : বাংলা ভাষা, সাহিত্য ও সংস্কৃতি -
পরবাস | সংখ্যা ১০০ | অক্টোবর ২০২৫ | প্রবন্ধ
Share -
বাংলা ওয়েবজিনের কালচিহ্ন ‘পরবাস’ : স্বপন ভট্টাচার্য
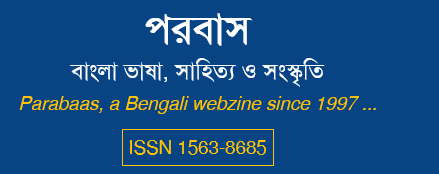
আমার লেখালেখির শুরু, আরো অনেকের মতোই স্কুলে, দেওয়াল পত্রিকায়। স্কুলে থাকতেই হাতে লেখা পত্রিকা সম্পাদনা করেছি। ছাপা অক্ষরে নিজের প্রথম লেখা দেখতে পাওয়ার রোমাঞ্চ আজও বিস্মৃত হইনি, কিন্তু সেই বয়েস থেকে শুরু করে প্রৌঢ়ত্বে উপনীত হওয়ার পরেও কোনদিন ভাবনাতেও আসেনি ছাপা ব্যতীত প্রচারযোগ্য পত্রিকা হতে পারে। বাংলা সাহিত্যের গতিপ্রকৃতি প্রায় গোড়া থেকেই পত্রিকানির্ধারিত, সেই বঙ্কিমচন্দ্রের বঙ্গদর্শনের কাল বা তার আগে থেকেই। অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তের লেখায় পড়েছি নজরুল ইসলাম সম্পাদিত ধুমকেতু-র জন্য সকাল থেকে জগুবাবুর বাজারে দাঁড়িয়ে থাকতে হত তাঁদের, বান্ডিল নামানোর সঙ্গে সঙ্গেই শেষ। তা ধুমকেতু তো আর প্রবাসী বা কল্লোলের মত যুগন্ধর পত্রিকা ছিল না, উপরন্তু সংখ্যালঘুর সম্পাদনায়, সেই পত্রিকাই যদি এমন উন্মাদনা সৃষ্টি করতে পারে, তাহলে কুলীন ছিল যারা, তাদের জন্য কতটা আকুলতা থাকতো তা অনুমান করা যায় কেবল। কমবেশি আমরাও এই উন্মাদনার শরিক হয়েছি কৃত্তিবাস থেকে কৌরব--নানা গোষ্ঠীর ছাপা পত্রিকা ঘিরে। ‘দেশ’ হোক বা ‘অমৃত’ অথবা ‘পরিচয়’ হোক বা ‘এক্ষণ’--বাছ-বিচারের পাঠকরুচি তখনও ছিল। কেউ হয়ত শুধু ‘সেই সময়’ এক কিস্তি পড়েই দেশ পড়ে ফেলতেন, কেউ শুধু দেবেশ রায় বা দীপেন্দ্রনাথ পড়েন পরিচয় হাতে পেলে।
সম্ভবত নব্বইয়ের দশকের উত্তরার্ধে স্যাম পিত্রোদা নামক এক শিকাগোনিবাসী প্রযুক্তিবিদের সহায়তা ও পরামর্শে প্রথমে রাজীব গান্ধী ও পরে মনমোহন সিংহের প্রধানমন্ত্রীত্বকালে ভারতে টেলিকমিউনিকেশন পরিষেবাক্ষেত্রে একটা বিরাট পরিবর্তনের সূচনা হয়। এমনকি আমরাও কমপিউটার জিনিসটাকে কোনদিন যদি রেস্তয় কুলোয় বাড়িতে আনার স্বপ্ন দেখতে শুরু করি, তবে ফোনে যে কোনদিন লেখালেখি সম্ভব হবে তা এই শতাব্দীর প্রথম দিকেও ভাবা যায়নি সম্ভবত। মনে আছে, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় এক টি ভি সাক্ষাৎকারে খুব জোরের সঙ্গে ঘোষণা করেছিলেন মোবাইল ফোন তিনি কোনদিন হাতে তুলবেন না। আমাদের মতো সুনীলভক্তরা যাদের আদপেই কেউ কোনোদিন খোঁজেনি, তারাও বলতে শুরু করলাম চাইলেই লোকে খোঁজ পেয়ে যাচ্ছে এমন যন্ত্র আমি হাতে নেব কেন? সেই কবিকুলই বাংলায় ওয়েবজিনের বন্যা নামিয়ে দিলেন করোনা অতিমারিকালে। বস্তুত বাংলা পত্রিকার করোনা-পূর্ব ও করোনা-উত্তর কালের মধ্যে তফাৎ একটা গবেষণার বিষয় হতে পারে। এবং সমগ্র বিশ্বসাহিত্যের জন্যেই বোধহয় কথাটা খেটে যায়। প্রিন্ট পত্রিকার দম হারিয়ে ফেলার সঙ্গে সঙ্গে প্রায় সমানুপাতিক হারে বেড়েছে তাদের ওয়েব-ভার্সনের আত্মপ্রকাশ ও রিডারশিপের বৃদ্ধির হার। হাতের কাছে ন্যাশানাল জিওগ্রাফিকের উদাহরণই তো আছে। সেটি ডাকযোগে হাতে পাবার অপেক্ষায় প্রায় প্রায় বিনিদ্র রাত্রিযাপন করেছি এককালে! আজকে বাংলাভাষায় যত ওয়েব পত্রিকা প্রকাশিত হয় তার সিংহভাগেরই জন্ম হয়েছে করোনাকালে যখন কমপিউটারে ইউনিকোড বাংলা ফন্ট আর কোন সমস্যাই নয়, এডিটিং, লে-আউট, পেজ-সেটিং, পিক্সেল বা মেমরি কোন সমস্যাই নয়, হয়ত বা সম্পাদকীয় পাতাটিও চ্যাটজিপিটি লিখিত, তখন আমরা নিজেরাই হয়ে উঠেছি এক একজন প্রকাশক। ফেসবুক বা হোয়াটসঅ্যাপের মত প্ল্যাটফর্ম ছাড়া এই জোয়ারে ভাসা অসম্ভব ছিল। সামাজিক মাধ্যম ছাড়া স্বতন্ত্রভাবে ব্লগ বা ভ্লগ বা ইউটিউব সাইট কতটা জনপ্রিয় হত তা নিয়ে সন্দেহ আছে।
‘পরবাস’ এই নিরিখে এক উজ্জ্বল ব্যতিক্রম। আমেরিকান প্রেক্ষিতেই যখন কমপিউটিং জিনিসটার আদিযুগ চলছে, পরবাস তখন একদল প্রবাসী বাঙালি, এবং আরও বিশেষায়িত করে বললে একদল প্রবাসী ও মুলত প্রযুক্তিবিদ সাহিত্যানুরাগী, ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় কীভাবে এমন একটি ওয়েব পত্রিকার কথা ভেবেছিলেন সেটাই অবাক করে দেওয়ার মতো।
১৯৯৭ এর জুন মাসে আত্মপ্রকাশ ‘পরবাস’-এর, কিন্তু তার আগে সলতে পাকানোর পর্যায়টি ধরা রয়েছে সম্বিৎ বসুর আদি পরবাস কথা--এক ব্যক্তিগত পর্যটন (সংখ্যা ৮৪) শিরোনামের গদ্যে। অত্যন্ত সুলিখিত এই নিবন্ধটি পড়লে বোঝা যায় সে যুগে একটা ওয়েব পত্রিকা করাটা ঠিক কতটা চ্যালেঞ্জের ছিল। (এই সূত্রে পরবাসের সম্পাদকের একটি সাক্ষাৎকারও পড়া যেতে পারে।) ইংরেজি ফন্টে বাংলা তখন হোঁচট খেতে খেতে লিখছেন কেউ কেউ। হয়ত মেসেজ লেখার তাগিদে একটা সংকেতবহুল বিকল্প বাংলাভাষার প্রকাশ ঘটছে এবং কেউ কেউ রোমান হরফে বাংলা নয় কেন--এই সওয়াল করছেন, তখন আমেরিকার নানা জায়গায় একদল বাঙালি প্রযুক্তিবিদ ও অ্যাকাডেমিক কি অপরিসীম ধৈর্য নিয়ে অধুনা অতীত কিছু সফটওয়্যার ব্যবহার করে বাংলিশ টাইপফেসকে ছবিতে কনভার্ট করে প্রকাশ করেছিলেন প্রথম সংখ্যা। পাঠকমহলে এতটা ঔৎসুক্য সঞ্চার করেছিল এই আত্মপ্রকাশ যে পরের সংখ্যায় পারমিতা দাসকে কম্পিউটার মাধ্যমে বাংলা বর্ণমালা (শরৎ, ১৯৯৭) শীর্ষক প্রবন্ধ লিখে প্রযুক্তির সম্ভাব্যতা বিষয়ে আলোকপাত করতে হয়। প্রথম থেকেই তাদের উদ্দেশ্য ছিল পাঠক যেন খুব সহজে কেবলমাত্র ব্রাউজারে ক্লিক করলেই বিশেষ লেখাটি বাংলা অক্ষরে পেয়ে যান—তার জন্য কোনো বিশেষ ফন্ট ইত্যাদি ডাউনলোড করতে হবে না। পরে বাংলার পাঠকরা ফন্ট ডাউনলোডে অভ্যস্ত হতে শুরু করলে পরবাসের পাতাগুলি ছবি হিসেবে দেখাবার প্রয়োজন ছিল না। ২০০০ দশকের গোড়ার দিকে পরবাসের প্রযুক্তিবিদরা ‘পরবাস-অক্ষর’ নামে একটি বাংলা ওয়র্ড প্রসেসিং সফটওয়্যারও তৈরি করেন যার সাহায্যে লেখার প্রুফ দেখা এবং প্রকাশ আরো সহজ হয়েছিল। পরবাসের ২৬ থেকে ৪৭ সংখ্যা এই সফটয়্যারের মাধ্যমে প্রকাশিত হয়। ‘পরবাস-অক্ষর’-ও বিনামূল্যে যে কেউ ব্যবহার করতে পারতেন। আজকের ‘অভ্র’-নির্ভর ইউনিকোড বাংলা বর্ণমালার যুগে দাঁড়িয়ে আমাদের ভাবতেই অবাক লাগে প্রথম পর্যায়ের পরবাসকে ঠিক কতখানি বিকল্প ভাবনার ফসল ফলাতে হয়েছিল! এই প্রসঙ্গে মনে পড়ছে সত্যজিৎ রায়কে পুরনো রোলিফ্লেক্স ক্যামেরা ব্যবহার করতে দেখে বিদেশী সাংবাদিক প্রশ্ন করেছিলেন এত ব্যাকডেটেড ক্যামেরা ব্যবহার করে তিনি ছবি বানাচ্ছেন কী ভাবে! উত্তরে সত্যজিৎ যা বলেছিলেন তা কিংবদন্তি হয়ে আছে, বলেছিলেন ওই কারণেই তিনি ও সুব্রত মিত্র পুরনো প্রযুক্তি ব্যবহারের পথে কিছু বিকল্প ভাবনা ভাবতে পেরেছিলেন (বাউন্স লাইটিং-এর কথা মনে করুন)। বাংলায় ওয়েব পত্রিকা প্রকাশ করা যে সম্ভব হবে কোনদিন প্রযুক্তির ওই টানাপোড়েনের দিনে কেবল বিকল্প ভাবনাকে রূপায়িত করার ঝুঁকি নিয়ে তা করে দেখিয়েছিল ‘পরবাস’। এই আত্মপ্রকাশের একটি ঐতিহাসিক মূল্য আছে এবং গবেষকদের নজর তা এড়াবে না বলেই আমাদের বিশ্বাস।
ডিজিট্যাল ফর্ম্যাটে বাংলা টাইপিং-এ বিপ্লব এনে দেন মেহেদী হাসান খান তাঁর ইউনিকোড ও ANSI সমর্থিত মুক্ত সফটওয়্যার অভ্র বাংলা ফোনেটিক কী-বোর্ডের মাধ্যমে। ২০০৩ সালের ঘটনা সেটা আর অ্যান্ড্রয়েড মোবাইল অপারেটিং সিস্টেম কাজ করা শুরু করে ২০০৭-০৮ থেকে। বস্তুত তখন থেকেই আমরা আমাদের কলমে অভ্যস্ত আঙুলকে কি বোর্ডে সড়গড় করতে চেষ্টা শুরু করি। এই যে দশ বছরের সময়কাল ১৯৯৭ থেকে ২০০৭ পর্যন্ত, এই সময়কালে, যখন এখন চালু বেশিরভাগ ওয়েব ম্যাগাজিনের জন্মই হয়নি, তখন ‘পরবাস’ ধীরে ধীরে সাবালকত্ব অর্জন করেছে এ কম শ্লাঘার কথা নয়। আরো বিস্ময়ের এই যে প্রথম সংখ্যা থেকে আজ পর্যন্ত যিনি এই পত্রিকা সম্পাদনা করে এসেছেন সেই সমীর ভট্টাচার্য নিজে সম্পাদকীয় ব্যতীত সম্ভবত একটিমাত্র সংখ্যায় কিছু লিখে থাকবেন। এ এক বিরলপ্রায় নজির বিশেষত বাংলায় যখন পত্রিকা সম্পাদক হলেই বিনিময় প্রথায় নামী অনামী বিবিধ পত্রিকায় নিজের অপাঠ্য লেখাও প্রকাশের সুযোগ নেওয়া যায়। পত্রিকা ঘিরে লেখকগোষ্ঠী তৈরি হয়, ‘পরবাস’ও তার ব্যতিক্রম নয়, কিন্তু ব্যাকস্টেজে যে একটি নিরপেক্ষ সম্পাদকমণ্ডলী কাজ করে তার নমুনা আমি নিজে পেয়েছি বলেই জানি।
এইভাবে আজ ‘পরবাস’ শততম সংখ্যায়। আমি এই পত্রিকায় লিখছি সম্ভবত ৮২ তম সংখ্যা থেকে। জামশেদপুরনিবাসী যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তনী শান্তনু চক্রবর্তী দত্তাত্রেয় দত্ত-র একটি সনেট সংগ্রহ আমাকে পড়তে দিয়ে একটি পাঠ প্রতিক্রিয়া লিখতে বলেন এবং আমি সানন্দে সেটা করি। এটিই পরবাসে প্রকাশিত আমার প্রথম রচনা। এর আগে শান্তনুবাবুই আমার কাব্যগ্রন্থ ‘ওষধিবাগান’-এর একটি পাঠ অভিজ্ঞতা লেখেন এই পত্রিকাতেই। পুস্তক সমালোচনা পেয়ে এবং লিখে সম্পাদকের কাছ থেকে মৌলিক রচনা লেখার ডাক আসবে এসব একালে বাংলা পত্রিকার জগতে আর কদাচিৎ হয়ে থাকে, কিন্তু সমীর ভট্টাচার্য যে সব অর্থেই পাঠক সম্পাদক তা বুঝতে পারি এবং নিজেকে পরবাসের লেখক হিসেবে দেখতে পাওয়াটা আমার সামান্য লেখক জীবনের এক বড়ো অর্জন বলে মনে করেছি। শ্লাঘা বোধ করি এটা মনে করেও যে, মূলত এই পত্রিকায় প্রকাশিত আমার লোরকা অনুবাদ ধানসিড়ি প্রকাশনার কাছে পৌঁছানোর পর তাঁরা সাগ্রহে তা ছেপেছেন। পরে আমি বোর্হেসের কবিতার অনুবাদ করেছি পরবাস-এর জন্য এবং ধানসিড়ি থেকে প্রকাশিত আমার নির্বাচিত বোর্হেস অনুবাদে সেগুলি সংকলিত হয়েছে। গল্প লিখেছি এবং নির্বাচিত গল্পের প্রথম খণ্ডে সে লেখা স্থান পেয়েছে। সুতরাং ‘পরবাস’ খুব বেশি করেই আমার লেখকজীবনের সঙ্গে জড়িয়ে গেছে। প্রিয় সে পত্রিকার শততম সংখ্যা যেন প্রতিপালকের শতবর্ষের মত অনুভূতি আনছে। কিন্তু ‘পথের শেষ কোথায়, কী আছে শেষে’-এই প্রশ্ন তো এড়িয়ে যাওয়া যাবে না।
আর্যা ভট্টাচার্যর ৮৬ তম সংখ্যায় ন্টেড ম্যাগাজিন বনাম ওয়েবজিন
শীর্ষক প্রবন্ধের পাঠ প্রতিক্রিয়ায় যা লিখেছিলাম তা পুনরাবৃত্তি না করার কোন কারণ দেখি না, কেন না প্রতিদিন দেখতে পাচ্ছি পাঠক সব ক্ষেত্রেই কমে যাচ্ছে। ডিজিট্যাল মাধ্যমে রিডারশিপ প্রিন্ট মাধ্যমের সমানুপাতিকে বাড়ছে খবরের কাগজের ক্ষেত্রে হয়তো, কিন্তু ছাপা বইয়ের বেলায় সে কথা খাটে না। ওই একই লেখার প্রসঙ্গে শুভময় রায় মশাইয়ের চিঠি যা ৮৭ সংখ্যায় প্রকাশিত হয়েছিল তা আর একবার পড়ে নেওয়া যায়। তিনি লিখেছিলেন--‘সাহিত্যপিপাসু পাঠকের কাছে কোন্ মাধ্যমে ভর করে সাহিত্য এসে পৌঁছল তা বোধহয় ততটা গুরুত্বপূর্ণ নয়। অনুসন্ধিৎসু পাঠক মালমশলা জোগাড়ে পিছিয়ে থাকবেন না। ফুটপাতের পুরোনো বইয়ের দোকান থেকে অনলাইন লাইব্রেরি, ছাপা পত্রপত্রিকা থেকে আমাদের এই ওয়েবজিন – সর্বত্রই রইবে তাঁর অবাধ বিচরণ। বৃহত্তর পাঠক সমাজ একটা পিরামিডের মত যার নিচের অংশটার ওপর ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে পিরামিডের চূড়াটি। আমার আশঙ্কা পিরামিডের নিচের ভিতটি ক্রমশই ক্ষয়ে আসছে।’ সোশ্যাল মিডিয়ায় করোনা পরবর্তীকালে যে বিপুলসংখ্যক লেখকের আবির্ভাব প্রায় রোজ নিয়ম করে আমরা দেখতে পাই তাতে শুভময়বাবুর কথাগুলোতে সংশয় জাগা অস্বাভাবিক নয়। উপরন্তু চ্যাট জিপিটি প্রমুখের আওতায় এক একজন লেখক শুনতে পাই প্রতি পনেরো দিনে এক একটি করে রহস্য রোমাঞ্চ উপন্যাস নামাচ্ছেন, কাল প্রকাশিত বইয়ের অনুবাদ এসে যাচ্ছে আজকেই। এই অবস্থায় একটা বিভাজন তো হবেই অবশ্যম্ভাবীভাবে। তবে মূল কথাটা হল পাঠক থাকলে পাঠকরুচি! বিষয়নিষ্ঠ পত্রিকার সামনে এটাই চ্যালেঞ্জ। তবে, ভুলি কি করে যে ‘পরবাস’ আরও বড় চ্যালেঞ্জ উতরে জন্ম নিতে পেরেছিল। তাকে প্রাসঙ্গিক রাখার চ্যালেঞ্জ নিতে ব্যাকস্টেজের মানুষেরা যে যথাযথ পরিকল্পনা করছেন এ বিশ্বাস আমাদের আছে।
- মন্তব্য জমা দিন / Make a comment
- মন্তব্য পড়ুন / Read comments
- কীভাবে লেখা পাঠাবেন তা জানতে এখানে ক্লিক করুন | "পরবাস"-এ প্রকাশিত রচনার দায়িত্ব সংশ্লিষ্ট রচনাকারের/রচনাকারদের। "পরবাস"-এ বেরোনো কোনো লেখার মধ্যে দিয়ে যে মত প্রকাশ করা হয়েছে তা লেখকের/লেখকদের নিজস্ব। তজ্জনিত কোন ক্ষয়ক্ষতির জন্য "পরবাস"-এর প্রকাশক ও সম্পাদকরা দায়ী নন। | Email: parabaas@parabaas.com | Sign up for Parabaas updates | © 1997-2025 Parabaas Inc. All rights reserved. | About Us