-
পরবাস
বাংলা ভাষা, সাহিত্য ও সংস্কৃতি
Parabaas, a Bengali webzine since 1997 ... ISSN 1563-8685 -
ছোটদের পরবাস
Satyajit Ray
Rabindranath Tagore
Buddhadeva Bose
Jibanananda Das
Shakti Chattopadhyay
সাক্ষাৎকার -
English
Written in English
Book Reviews
Memoirs
Essays
Translated into English
Stories
Poems
Essays
Memoirs
Novels
Plays
-

পুত্রবধূর চোখে গৌরী আইয়ুব এবং প্রসঙ্গত
-

বিশ্বের ইতিহাসে হুগলি নদী
-

বেদখল ও অন্যান্য গল্প
-

Audiobook
Looking For An Address
Nabaneeta Dev Sen
Available on Amazon, Spotify, Google Play, Apple Books and other platforms.
-

পরবাস গল্প সংকলন-
নির্বাচন ও সম্পাদনা:
সিদ্ধার্থ মুখোপাধ্যায়)
-

Parabaas : পরবাস : বাংলা ভাষা, সাহিত্য ও সংস্কৃতি -
পরবাস | Satyajit Ray | প্রবন্ধ
Share -
লেখক সত্যজিৎ : সোমজিৎ দত্ত
 আনন্দবাজার পত্রিকা য় প্রতি সপ্তাহেই একটি 'বেস্টসেলারে'র তালিকা প্রকাশিত হয় কলকাতার বিভিন্ন বইয়ের দোকানে যে-সমস্ত বইয়ের বিক্রি সর্বাধিক তারই তালিকা সেটি কথাসাহিত্য ও অন্যান্য এই দুই পর্যায়ে দুটি তালিকা প্রকাশিত হয়। কথাসাহিত্য বা ফিকশন-এর তালিকায় সপ্তাহের পর সপ্তাহ যে লেখকের কোনও না কোনও বইয়ের নাম শীর্ষস্থান অধিকার করে থাকে তিনি কিন্তু কোনো ইদানীন্তন সাহিত্যসম্রাট ন'ন -- তিনি চিত্রপরিচালক সত্যজিৎ রায়।
আনন্দবাজার পত্রিকা য় প্রতি সপ্তাহেই একটি 'বেস্টসেলারে'র তালিকা প্রকাশিত হয় কলকাতার বিভিন্ন বইয়ের দোকানে যে-সমস্ত বইয়ের বিক্রি সর্বাধিক তারই তালিকা সেটি কথাসাহিত্য ও অন্যান্য এই দুই পর্যায়ে দুটি তালিকা প্রকাশিত হয়। কথাসাহিত্য বা ফিকশন-এর তালিকায় সপ্তাহের পর সপ্তাহ যে লেখকের কোনও না কোনও বইয়ের নাম শীর্ষস্থান অধিকার করে থাকে তিনি কিন্তু কোনো ইদানীন্তন সাহিত্যসম্রাট ন'ন -- তিনি চিত্রপরিচালক সত্যজিৎ রায়।
[আনন্দবাজারের ওয়েবসাইট থেকে দেখা যাচ্ছে প্রথম তিনটি বই হলো : ৪ নভেম্বর ২০০০ - কলকাতায় ফেলুদা (সত্যজিৎ রায়), সেই সময় (সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়), কোজাগর (বুদ্ধদেব গুহ) ২৪শে নভেম্বর, ২০০১ -- পাহাড়ে ফেলুদা (সত্যজিত্), ১০টি উপন্যাস (বুদ্ধদেব গুহ), প্রথম আলো (সুনীল), এবং ৯ নভেম্বর ২০০২ -- কলকাতায় ফেলুদা, প্রথম আলো, ও মাধুকরী (বুদ্ধদেব গুহ)। ]
চিত্রপরিচালক যে, তাতে তো সন্দেহের অবকাশ নেই কিন্তু প্রশ্ন -- লেখক সত্যজিৎ কী করে বাণিজ্যিকভাবে খ্যাতকীর্তি 'স্পেশ্যালিস্ট' সাহিত্যিকদের নিয়মিতভাবে ছাড়িয়ে যাচ্ছেন, তাঁর মৃত্যুর পরে এক দশক অতিক্রান্ত হয়েছে, তা-সত্ত্বেও? বাংলায় সফল লেখক বলতে আমরা বুঝি -- সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়, বুদ্ধদেব গুহ, সমরেশ বসু, শংকর, সমরেশ মজুমদার, সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়, বিমল কর, শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়, রমাপদ চৌধুরী এবং আরো আধ-ডজন লেখক। অথচ এঁদের কারুর বইয়েরই বিক্রি সত্যজিতের বইয়ের থেকে বেশি নয় কম ! আশ্চর্য হতে হয় অন্তত কিছুটা।
একথা সত্য যে বেস্টসেলারের তালিকাই সাহিত্যিক বিচারের মূল বা প্রধান মাপকাঠি নয় একথাও সত্য যে সত্যজিৎ কিশোর-কিশোরীদের জন্য লিখতেন, প্রাপ্তবয়স্ক পাঠকপাঠিকার থেকে ছোটোরাই বেশি বইপত্র পড়ে ইত্যাদি। কিন্তু কিশোরসাহিত্য তো সুনীল, বুদ্ধদেব, সঞ্জীব, শীর্ষেন্দু, শংকর-রাও সৃষ্টি করেছেন তাঁদের কিশোরসাহিত্যের থেকে সত্যজিতের সাহিত্য কিশোর-কিশোরীদের আরো বেশি কাছে যেতে পেরেছে, একথা আশা করি অধিকাংশ শিক্ষিত বাঙালিই স্বীকার করবেন বেস্টসেলারের তালিকা শুধু জানান দিচ্ছে, এই মতের একটি দৃঢ় সংখ্যাগত ভিত্তি আছে। সুতরাং লেখক সত্যজিৎ যে চূড়ান্তভাবে সফল, তা নিয়ে সংশয়ের অবকাশ নেই কিন্তু কিছুটা বিস্ময়ের অবকাশ আছে।
বিস্ময়ের প্রসঙ্গ তুলছি কেন? সত্যজিৎ তাঁর চল্লিশ বছর বয়সের আগে সাহিত্যসৃষ্টির জন্য কলম ধরেননি কখনো। চলচ্চিত্রের চিত্রনাট্য রচনা অবশ্যই করেছেন 'কাঞ্চনজঙ্ঘা' ছবির কাহিনীও তাঁরই রচনা 'পিকু' ছবিটি পিকুর ডায়রি শীর্ষক গল্পের থেকে তৈরি। সাহিত্যে যাঁরা বহু বছর ধরে লেখালিখি করেছেন, তাঁদের প্রথম সারির লেখকলেখিকাদের কারুরই প্রথম গদ্যগ্রন্থ পঞ্চাশ বছর বয়সে প্রকাশিত হয়নি সাধারণত কুড়ি-ত্রিশের কোঠাতেই গদ্যশিল্পীর আত্মপ্রকাশ ঘটে কবিদের ক্ষেত্রে সেটা ঘটে আরো আগে ব্যতিক্রম কিছু অবশ্যই আছে। শুধু তাই নয়, প্রথম জীবনে সত্যজিতের বাংলাও খুব সাবলীল ছিল না কথাটা বিশ্বাসযোগ্য মনে না হলেও সত্য সত্যজিৎ নিজেই তা বলে গেছেন মনে পড়ছে, কোথায় যেন পড়েছিলাম যে, তিনি প্রথমদিকে তাঁর চিত্রনাট্যে নানারকম মন্তব্য ইংরেজিতে লিখে রাখতেন দৃষ্টান্ত দিয়েছিলেন : অপুর সংসার ছবিতে একটি দৃশ্য আছে, অপু তার উপন্যাসের পাণ্ডুলিপি ছিঁড়ে উড়িয়ে দিচ্ছে, খাদের ধারে দাঁড়িয়ে কাগজের টুকরোগুলো হাওয়ায় উড়তে উড়তে ছড়িয়ে পড়ছে চিত্রনাট্যের এই অংশে কাগজের টুকরো উড়ে যাওয়ার দৃশ্যটি বর্ণনা করতে গিয়ে সত্যজিৎ ইংরেজিতে লিখেছিলেন ত্ঠূং ভশংছঞ স্ঠভশছঞধশষ্ ঢঠশরুয.
অর্থাৎ নিজের অনুভূতি প্রকাশ করতে সত্যজিত্কে বাংলা চিত্রনাট্যে মন্তব্য লিখতে ইংরেজির শরণাপন্ন হতে হত। অবশ্য এর একটা কারণ হয়তো এই, যে, ছোটোবেলা থেকে প্রথম যৌবন পর্যন্ত বাংলা বইয়ের থেকে ইংরেজি বইই তিনি বেশি পড়েছিলেন। একথা মনে রাখতে হবে যে সত্যজিতের নিজের কৈশোরে বাংলার কিশোরসাহিত্য পরেকার মতো জোরালো ছিল না কিছু শক্তিশালী লেখা অবশ্যই ছিল, তবে পরজীবনে সত্যজিৎ নিজে যে-মাপের কিশোরসাহিত্যিক হয়েছিলেন তাঁর নিজের কৈশোরে ঠিক সেই মাপের কোনো কিশোরসাহিত্যিক ছিলেন না প্রেমেন্দ্র মিত্র, শিবরাম চক্রবর্তী বা নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় কুড়ি বা ত্রিশের দশকে বিপুল জনপ্রিয়তা লাভ করে উঠতে পারেননি পেরেছিলেন আরো পরে। সত্যজিতের কৈশোর ওই দুটি দশকেই কাটে। তাছাড়া প্রথম যৌবনে সত্যজিৎ চিত্রকলা নিয়ে ব্যস্ত ছিলেন তারপর বিজ্ঞাপনের জগতে প্রবেশ এবং ধীরে ধীরে চলচ্চিত্রে আগ্রহী হয়ে পড়া। চলচ্চিত্র-বিষয়ক যাবতীয় বইপত্র সবই তখন ইংরেজিতে লেখা হতো সত্যজিৎ সেসব মনোযোগ সহকারে পড়তেন এবং বিজ্ঞাপন-জগতেও ইংরেজিই ছিল তাঁর যোগাযোগের মূল মাধ্যম। খুব সম্ভবত সত্যজিতের প্রথম প্রকাশিত লেখা ইংরেজিতেই, অবশ্যই চলচ্চিত্র সংক্রান্ত।
 অতএব বাংলা গদ্যসাহিত্যে তিনি যে প্রথম জীবনে বিশেষ আগ্রহী ছিলেন না, তাতে আশ্চর্য হওয়ার বিশেষ কারণ দেখি না। বাংলাসাহিত্য সত্যজিৎ স্বেচ্ছায় আগেই পড়তে শুরু করলেও বইয়ের অলংকরণের কাজ করতে গিয়ে তাঁকে বাংলা গদ্য পড়তে হতো, কবিতাও পড়তে হতো। সম্ভবত জীবনানন্দের কাব্যগ্রন্থের প্রচ্ছদ ও অলংকরণ করতে গিয়েই সত্যজিৎ প্রথম তাঁর কবিতা পড়েন। পাঠক-পাঠিকার নিশ্চয় মনে আছে যে অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের রাজকাহিনী র যে বিখ্যাত প্রচ্ছদটি বাঙালির কাছে অবিস্মরণীয়, সেটিও সত্যজিতের সৃষ্টি বইটির ভিতরের অলংকরণও তাঁরই। পথের পাঁচালী র সংক্ষিপ্ত কিশোর সংস্করণ আম আঁটির ভেঁপু র অলংকরণ করতে গিয়েই যে পথের পাঁচালী কে চলচ্চিত্রায়িত করবার কথা প্রথম মনে হয়, তা তো আজ ইতিহাস। তবে 'পূর্ণাঙ্গ' পথের পাঁচালী সত্যজিৎ আগেই পড়েছিলেন, নাকি আম আঁটির ভেঁপু পড়বার পর চলচ্চিত্রায়নের উদ্দেশ্য নিয়েই তিনি ওই উপন্যাসটি পড়েন তা আমার জানা নেই এ-ব্যাপারে সত্যজিৎ কিছু লিখে গিয়ে থাকলে তা আমার
দৃষ্টিগোচর হয়নি।
অতএব বাংলা গদ্যসাহিত্যে তিনি যে প্রথম জীবনে বিশেষ আগ্রহী ছিলেন না, তাতে আশ্চর্য হওয়ার বিশেষ কারণ দেখি না। বাংলাসাহিত্য সত্যজিৎ স্বেচ্ছায় আগেই পড়তে শুরু করলেও বইয়ের অলংকরণের কাজ করতে গিয়ে তাঁকে বাংলা গদ্য পড়তে হতো, কবিতাও পড়তে হতো। সম্ভবত জীবনানন্দের কাব্যগ্রন্থের প্রচ্ছদ ও অলংকরণ করতে গিয়েই সত্যজিৎ প্রথম তাঁর কবিতা পড়েন। পাঠক-পাঠিকার নিশ্চয় মনে আছে যে অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের রাজকাহিনী র যে বিখ্যাত প্রচ্ছদটি বাঙালির কাছে অবিস্মরণীয়, সেটিও সত্যজিতের সৃষ্টি বইটির ভিতরের অলংকরণও তাঁরই। পথের পাঁচালী র সংক্ষিপ্ত কিশোর সংস্করণ আম আঁটির ভেঁপু র অলংকরণ করতে গিয়েই যে পথের পাঁচালী কে চলচ্চিত্রায়িত করবার কথা প্রথম মনে হয়, তা তো আজ ইতিহাস। তবে 'পূর্ণাঙ্গ' পথের পাঁচালী সত্যজিৎ আগেই পড়েছিলেন, নাকি আম আঁটির ভেঁপু পড়বার পর চলচ্চিত্রায়নের উদ্দেশ্য নিয়েই তিনি ওই উপন্যাসটি পড়েন তা আমার জানা নেই এ-ব্যাপারে সত্যজিৎ কিছু লিখে গিয়ে থাকলে তা আমার
দৃষ্টিগোচর হয়নি।
সত্যজিৎ যে বাংলাসাহিত্যের অত্যন্ত মনোযোগী পাঠক ছিলেন, সে-ব্যাপারে সংশয় নেই সাহিত্যিক ও চলচ্চিত্রকারের কল্পনা ও দর্শন যে এক বিন্দুতে এসে মিলতে পারে তার একটি উত্কৃষ্ট উদাহরণ দিতে পারা যায় : জলসাঘর চলচ্চিত্রায়িত করবার সময় সত্যজিৎ যে জমিদার বাড়িটিকে পছন্দ করেন, পরে স্বয়ং তারাশঙ্করের কাছ থেকে জানতে পারা যায় যে উনি জলসাঘর লেখেন ওই জমিদার বাড়িটিকে ভিত্তি করেই। পরে শ্যুটিং-এর সময় তারাশঙ্কর সত্যজিৎ ও তাঁর দলবলের সঙ্গে লোকেশন-এ গিয়ে পড়তে পেরেছিলেন। অনবদ্য এই ছবিটি মনোযোগ সহকারে একাধিকবার দেখলে বুঝতে পারা যায় সত্যজিতের সাহিত্যিক দর্শন কতো প্রখর ও অন্তর্ভেদী ছিল।
কিন্তু এসবই তো চলচ্চিত্রকার সত্যজিতের কথা। তিনি নিজে বাংলায় সাহিত্যরচনা করার সিদ্ধান্ত কবে কীভাবে নিলেন? ষাটের দশকের গোড়ার দিকে কবি সুভাষ মুখোপাধ্যায় সত্যজিতের সঙ্গে বসে আড্ডা দিতে দিতে সন্দেশ পত্রিকা নতুন করে শুরু করার কথা তোলেন। সত্যজিৎ রাজি হয়ে যান : বাংলা কিশোরসাহিত্য এই আড্ডার কাছে বিশেষভাবে ঋণী। কিছুদিনের মধ্যেই সত্যজিৎ ও সুভাষের সম্পাদনায় সন্দেশ প্রকাশিত হতে শুরু করে। পরে সত্যজিৎ একটি সাক্ষাত্কারে বলেন যে সন্দেশ কে ংঈংংরু করার জন্য কিশোরকিশোরীদের উপযোগী লেখা তিনি লিখতে শুরু করেন। ( ংঈংংরু কথাটা তিনিই ব্যবহার করেছিলেন, মনে আছে।) ষাটের দশকের মধ্যভাগে শুরু হয় প্রোফেসার শঙ্কু ও ফেলুদা-তোপসের চরিত্রগুলি।
 সন্দেশ পত্রিকা খুব বেশি মূলধন নিয়ে শুরু করা যায়নি। সেই কারণে প্রতিষ্ঠিত সাহিত্যিকদের লেখার সঙ্গে সত্যজিৎ ও রায়পরিবারের অন্যান্যরা নিয়মিত এই পত্রিকায় লিখতেন শুধুমাত্র প্রতিষ্ঠিত লেখকদের লেখা প্রকাশ করে পত্রিকা চালানোর সামর্থ্য প্রকাশকদের ছিল না। সত্যজিতের লেখা প্রথম থেকেই জনপ্রিয় হওয়ায় তাঁকে বেশি লিখতেই হতো। অল্পবয়স থেকেই একদিকে যেমন এমিল গ্যাবোরিও থেকে আর্থার কোনান ডয়েল পর্যন্ত ডিটেকটিভ গল্প উপন্যাস বিস্তর পড়েছিলেন, তেমন অন্যদিকে বিংশ শতকে সায়েন্স ফিকশন যা লেখা হয় তারও অধিকাংশেরই মনোযোগী পাঠক তিনি ছিলেন আর্থার সি. ক্লার্ক, রে ব্রাডবেরি ও অন্যান্য লেখকদের কল্পবিজ্ঞানভিত্তিক সাহিত্য তাঁকে প্রোফেসর শঙ্কুর কাণ্ডকারখানা নিয়ে লিখতে অনুপ্রাণিত করেছিল।
সন্দেশ পত্রিকা খুব বেশি মূলধন নিয়ে শুরু করা যায়নি। সেই কারণে প্রতিষ্ঠিত সাহিত্যিকদের লেখার সঙ্গে সত্যজিৎ ও রায়পরিবারের অন্যান্যরা নিয়মিত এই পত্রিকায় লিখতেন শুধুমাত্র প্রতিষ্ঠিত লেখকদের লেখা প্রকাশ করে পত্রিকা চালানোর সামর্থ্য প্রকাশকদের ছিল না। সত্যজিতের লেখা প্রথম থেকেই জনপ্রিয় হওয়ায় তাঁকে বেশি লিখতেই হতো। অল্পবয়স থেকেই একদিকে যেমন এমিল গ্যাবোরিও থেকে আর্থার কোনান ডয়েল পর্যন্ত ডিটেকটিভ গল্প উপন্যাস বিস্তর পড়েছিলেন, তেমন অন্যদিকে বিংশ শতকে সায়েন্স ফিকশন যা লেখা হয় তারও অধিকাংশেরই মনোযোগী পাঠক তিনি ছিলেন আর্থার সি. ক্লার্ক, রে ব্রাডবেরি ও অন্যান্য লেখকদের কল্পবিজ্ঞানভিত্তিক সাহিত্য তাঁকে প্রোফেসর শঙ্কুর কাণ্ডকারখানা নিয়ে লিখতে অনুপ্রাণিত করেছিল।
 লিখতে শুরু করার অল্প কিছুদিনের মধ্যেই প্রোফেসর শঙ্কু নামে একটি সংকলন প্রকাশিত হয় ফেলুদাসিরিজের প্রথম বই বাদশাহী আংটি প্রকাশিত হয় ১৯৬৯ সালে প্রকাশক আনন্দ পাবলিশার্স। তবে ফেলুদা-তোপসেকে নিয়ে প্রথম গল্পের নাম ফেলুদার গোয়েন্দাগিরি যা পরে এক ডজন গপ্পো বইটিতে প্রকাশিত হয়। লালমোহন গাঙ্গুলীর চরিত্রটির আবির্ভাব ঘটে আরো পরে, সোনার কেল্লা উপন্যাসে।
লিখতে শুরু করার অল্প কিছুদিনের মধ্যেই প্রোফেসর শঙ্কু নামে একটি সংকলন প্রকাশিত হয় ফেলুদাসিরিজের প্রথম বই বাদশাহী আংটি প্রকাশিত হয় ১৯৬৯ সালে প্রকাশক আনন্দ পাবলিশার্স। তবে ফেলুদা-তোপসেকে নিয়ে প্রথম গল্পের নাম ফেলুদার গোয়েন্দাগিরি যা পরে এক ডজন গপ্পো বইটিতে প্রকাশিত হয়। লালমোহন গাঙ্গুলীর চরিত্রটির আবির্ভাব ঘটে আরো পরে, সোনার কেল্লা উপন্যাসে।
 -- এক ডজন গপ্পো বইটির বিবিধ বিষয়ের ছোটোগল্পগুলিতে : এই গল্পগুলির মধ্য দিয়ে পাঠকককূল এক অতিশক্তিধর গদ্যশিল্পীর সঙ্গে পরিচিত হ'ন। আমার বিশ্বাস, ফেলুদা ও প্রোফেসর শঙ্কু জনপ্রিয় চরিত্র হলেও, অলৌকিক, ভৌতিক ও কৌতূকময় বিষয় নিয়ে সত্যজিৎ যে ছোটোগল্পগুলি লেখেন সেগুলির সাহিত্যিক মূল্য অধিক স্থায়ী। এক ডজন গপ্পো ও
আরো এক ডজন -এ প্রকাশিত সেপ্টোপাশের ক্ষিদে, খগম, বাদুড় বিভীষিকা, শিবু আর রাক্ষস, পটলবাবু ফিল্মস্টার, নীল আতঙ্ক, রতনবাবু আর সেই লোকটা'র মতো গল্প বাংলাসাহিত্যে বিরল এই গল্পগুলিকে ঠিক কিশোরসাহিত্যের পর্যায়ে ফেলা যাবে না মনে আছে, আমার পরিচিত বহু প্রাপ্তবয়স্ক মানুষকে এই গল্পগুলি বহুবার পড়তে দেখেছি। শৈলী, ও ঘটনার বিন্যাসের দিক থেকে বাংলায় লিখিত শ্রেষ্ঠ ছোটোগল্পগুলির মধ্যে এগুলিকে স্থান দিতে আমি রাজি। যদিও জানি এ-ব্যাপারে কিছু বিতর্কের অবকাশ আছে। অ্যাম্ব্রোজ্ বিয়র্সের লেখার সঙ্গে সত্যজিৎ পরিচিত ছিলেন কিনা জানি না, তবে এডগার অ্যালান পো'র গল্পগুলির প্রায় সমতুল্য কিছু যদি লেখা হয়ে থাকে তবে তা সত্যজিতের গল্পগুলিই।
-- এক ডজন গপ্পো বইটির বিবিধ বিষয়ের ছোটোগল্পগুলিতে : এই গল্পগুলির মধ্য দিয়ে পাঠকককূল এক অতিশক্তিধর গদ্যশিল্পীর সঙ্গে পরিচিত হ'ন। আমার বিশ্বাস, ফেলুদা ও প্রোফেসর শঙ্কু জনপ্রিয় চরিত্র হলেও, অলৌকিক, ভৌতিক ও কৌতূকময় বিষয় নিয়ে সত্যজিৎ যে ছোটোগল্পগুলি লেখেন সেগুলির সাহিত্যিক মূল্য অধিক স্থায়ী। এক ডজন গপ্পো ও
আরো এক ডজন -এ প্রকাশিত সেপ্টোপাশের ক্ষিদে, খগম, বাদুড় বিভীষিকা, শিবু আর রাক্ষস, পটলবাবু ফিল্মস্টার, নীল আতঙ্ক, রতনবাবু আর সেই লোকটা'র মতো গল্প বাংলাসাহিত্যে বিরল এই গল্পগুলিকে ঠিক কিশোরসাহিত্যের পর্যায়ে ফেলা যাবে না মনে আছে, আমার পরিচিত বহু প্রাপ্তবয়স্ক মানুষকে এই গল্পগুলি বহুবার পড়তে দেখেছি। শৈলী, ও ঘটনার বিন্যাসের দিক থেকে বাংলায় লিখিত শ্রেষ্ঠ ছোটোগল্পগুলির মধ্যে এগুলিকে স্থান দিতে আমি রাজি। যদিও জানি এ-ব্যাপারে কিছু বিতর্কের অবকাশ আছে। অ্যাম্ব্রোজ্ বিয়র্সের লেখার সঙ্গে সত্যজিৎ পরিচিত ছিলেন কিনা জানি না, তবে এডগার অ্যালান পো'র গল্পগুলির প্রায় সমতুল্য কিছু যদি লেখা হয়ে থাকে তবে তা সত্যজিতের গল্পগুলিই।  ছোটোগল্পের জমজমাট স্বল্প-পরিসরে সাসপেন্স তৈরির ব্যাপারে আজও সত্যজিৎ অপ্রতিদ্বন্দ্বী। শুধু তাই নয়, পটলবাবু ফিল্মস্টার গল্পে যে-ধরনের ঠশধত্রঠব হাস্যরসের উপস্থিতি দেখি, তাও বাংলায় বেশ বিরল।
ছোটোগল্পের জমজমাট স্বল্প-পরিসরে সাসপেন্স তৈরির ব্যাপারে আজও সত্যজিৎ অপ্রতিদ্বন্দ্বী। শুধু তাই নয়, পটলবাবু ফিল্মস্টার গল্পে যে-ধরনের ঠশধত্রঠব হাস্যরসের উপস্থিতি দেখি, তাও বাংলায় বেশ বিরল।
সত্যজিতের গদ্যশৈলী নিয়ে সুদীর্ঘ প্রবন্ধ রচিত হতে পারে এই অল্প পরিসরে দু-একটি কথা তুলে ধরতে চাই। তাঁর গদ্য সাবলীল, অনাড়ম্বর অথচ আবেদন অত্যন্ত তীক্ষণ। সংলাপ যে অনবদ্য তা বলার অপেক্ষা রাখে না। মহান চলচ্চিত্রকার সংলাপ রচনায় সিদ্ধহস্ত হবেন তা তো স্বাভাবিক। তবে বর্ণনা বা "ন্যারেশন"-ও তাঁর অত্যন্ত বলিষ্ঠ ও চিত্তাকর্ষক। আমাদের প্রজন্মের বাঙালি কিশোরকিশোরী সত্যজিতের গদ্য যত পড়েছে, আর কোনো লেখকের গদ্য ততো পড়েছে কি? রবীন্দ্রনাথের গদ্য ততোটা পড়েনি এটা বোধহয় বলতে পারা যায়, কারণ তাঁর ছোটোগল্প ও উপন্যাস কৈশোরের শেষ ও যৌবনের প্রারম্ভেই সাধারণত পড়া হয়। অন্যদিকে সমসাময়িক লেখকদের গদ্যও সত্যজিতের গদ্যের মতো কৈশোরে অতোটা পড়া হয় না, যা বইয়ের কাটতির দিকে তাকালে কিছুটা বোঝা যায়।
 আবারো আনন্দবাজারের বেস্টসেলারের তালিকার দিকে তাকানো যাক। গল্প-উপন্যাসে সত্যজিতের বই ছাড়া কিশোরদের জন্য লেখা অন্য কোনো লেখকের বই নিয়মিত থাকে না সেখানে ফেলুদা-শঙ্কুর প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী সেই সময় , প্রথম আলো ইত্যাদি বিপুলবপু উপন্যাস, যা পড়বার পক্ষে যেমন উপাদেয়, না-পড়ে বাড়ির বাইরের ঘরে সাজিয়ে রাখবার পক্ষেও তেমনই উপযুক্ত। কিন্তু, বাণিজ্যিক দিক থেকে ফেলুদা-শঙ্কুও জয়ী, আজও, সপ্তাহের পর সপ্তাহ, মাসের পর মাস।
আবারো আনন্দবাজারের বেস্টসেলারের তালিকার দিকে তাকানো যাক। গল্প-উপন্যাসে সত্যজিতের বই ছাড়া কিশোরদের জন্য লেখা অন্য কোনো লেখকের বই নিয়মিত থাকে না সেখানে ফেলুদা-শঙ্কুর প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী সেই সময় , প্রথম আলো ইত্যাদি বিপুলবপু উপন্যাস, যা পড়বার পক্ষে যেমন উপাদেয়, না-পড়ে বাড়ির বাইরের ঘরে সাজিয়ে রাখবার পক্ষেও তেমনই উপযুক্ত। কিন্তু, বাণিজ্যিক দিক থেকে ফেলুদা-শঙ্কুও জয়ী, আজও, সপ্তাহের পর সপ্তাহ, মাসের পর মাস।
সুতরাং অন্তত একটি প্রজন্মের বাঙালি কৈশোরের গদ্যশিক্ষায় যে সত্যজিতের বিশেষ অবদান আছেই, এবং এ-ব্যাপারে তিনি যে সম্ভবত অন্য লেখকদের থেকে এগিয়ে একথা অস্বীকার করবার উপায় নেই। যে শিক্ষার উপর ভিত্তি করে বাংলায় প্রবন্ধ লিখছি, তার সূচনাপর্বে সত্যজিতের গদ্যের উল্লেখযোগ্য অবদান ছিল, একথা গৌরবের সঙ্গে স্বীকার করব।
তবে সত্যজিতের গদ্যশৈলীর সাবলীলতা ও বলিষ্ঠতার কথা বলতে গেলে তাঁর ইংরেজি গদ্যের কথা বলতে হয়। এখানে উল্লেখ করি : খ্যাতকীর্তি বাঙালি লেখকদের মধ্যে মাইকেল মধুসূদন দত্ত, বঙ্কিম ও নীরদচন্দ্র চৌধুরী উল্লেখযোগ্য ইংরেজি লেখা লিখেছেন এর মধ্যে মাইকেল মূলত ইংরেজি কবিতা লিখেছেন বঙ্কিম একটি ইংরেজি উপন্যাস নীরদচন্দ্রকে অবশ্য ইংরেজি লেখকই বলতে হয়। সত্যজিৎ এই তালিকার শেষে তারপরে কিছু অ্যাকাডেমিক প্রবন্ধকার ছাড়া আর কোনো বাঙালি লেখক বাংলা ও ইংরেজি দুই ভাষাতেই উল্লেখযোগ্য লেখা প্রকাশ করেননি। দুই ভাষাতেই প্রকাশযোগ্য রচনা যে সহজ নয়, তা আশা করি পরিষ্কার।
 মনে রাখতে হবে প্রথম বাংলা গদ্য প্রকাশিত হয় ১৮০১ সনে অথচ ব্রিটিশ বঙ্গে আসবার আগে বাংলা পদ্য ও গীতিকাব্য অবশ্যই ছিল, কিন্তু গদ্য ছিল না। বাংলা গদ্য ইংরেজি গদ্যের প্রভাবে মূলত সংস্কৃতকে আশ্রয় করে সৃষ্ট হয়। আগেই বলেছি, শৈশব থেকেই সত্যজিৎ ইংরেজি সাহিত্য বিস্তর পড়েছিলেন। যাঁরা তাঁর ইংরেজি গদ্যগ্রন্থ চণ্ণশ যঠত্স্য, মচ্ংঠশ যঠত্স্য ও
ংঔষ্ হৃংছশয গঠঞচ্ ংঋংইণ্ণ পড়েছেন তাঁরা জানেন তাঁর ইংরেজি গদ্য কতোটা বলিষ্ঠ ও প্রাঞ্জল। এই লেখাগুলি পড়তে গিয়ে আমার বার বার মনে হয়েছে যে, সত্যজিতের ইংরেজি গদ্যের জ্ঞান তাঁর বাংলা গদ্যরচনায় সাহায্য করেছিল। যাঁরা প্রথম দুই প্রজন্মের বাংলা গদ্যলেখক অর্থাৎ রামমোহন রায়, রামরাম বসু, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর -- তাঁরা সকলেই শৈশব, কৈশোর ও প্রথম যৌবনে বাংলা গদ্যের থেকে ইংরেজি গদ্যই বেশি পড়েছিলেন বঙ্কিমচন্দ্র সম্বন্ধেও এ-কথা অনেকাংশে সত্য। রবীন্দ্রনাথের প্রজন্ম থেকে বঙ্কিমচন্দ্রের গদ্য শিক্ষিত বাঙালিসমাজে সর্বজনপাঠ্য হয়। অতএব ইংরেজি গদ্যের উপর কোনো বাঙালি লেখকের দখল যে তাঁর বাংলা গদ্যরচনায় প্রভাব বিস্তার করতে পারে তা বুঝতে অসুবিধা হয় না। এই ব্যাপারটি বিস্তারিতভাবে তুলে ধরলাম কারণ সত্যজিতের সমসাময়িক বা পরবর্তী সাহিত্যিকদের মধ্যে কারুর গদ্যেই ইংরেজি গদ্যের বিশেষ প্রভাব দেখিনি সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়কে তাঁর স্যাটায়ার-ধর্মী লেখায় কিছুটা ব্যতিক্রম বলা যায়। বাংলাগদ্যের বয়স আজ দু'শ বছর, ইংরেজি গদ্যের পাঁচশ' বছর এই দীর্ঘতর ইতিহাসের জন্য ইংরেজি গদ্যের স্থিতিশীলতা, বিস্তার ও শব্দভাণ্ডারের বৈচিত্র্য কিছুটা বেশি সত্যজিতের গদ্যের যে সাবলীলতা ও ন্যাকামি-বিবর্জিত ঋজুতা, তার উত্স অনেকটাই ইংরেজি গদ্যে তাঁর গভীর অভিনিবেশ।
মনে রাখতে হবে প্রথম বাংলা গদ্য প্রকাশিত হয় ১৮০১ সনে অথচ ব্রিটিশ বঙ্গে আসবার আগে বাংলা পদ্য ও গীতিকাব্য অবশ্যই ছিল, কিন্তু গদ্য ছিল না। বাংলা গদ্য ইংরেজি গদ্যের প্রভাবে মূলত সংস্কৃতকে আশ্রয় করে সৃষ্ট হয়। আগেই বলেছি, শৈশব থেকেই সত্যজিৎ ইংরেজি সাহিত্য বিস্তর পড়েছিলেন। যাঁরা তাঁর ইংরেজি গদ্যগ্রন্থ চণ্ণশ যঠত্স্য, মচ্ংঠশ যঠত্স্য ও
ংঔষ্ হৃংছশয গঠঞচ্ ংঋংইণ্ণ পড়েছেন তাঁরা জানেন তাঁর ইংরেজি গদ্য কতোটা বলিষ্ঠ ও প্রাঞ্জল। এই লেখাগুলি পড়তে গিয়ে আমার বার বার মনে হয়েছে যে, সত্যজিতের ইংরেজি গদ্যের জ্ঞান তাঁর বাংলা গদ্যরচনায় সাহায্য করেছিল। যাঁরা প্রথম দুই প্রজন্মের বাংলা গদ্যলেখক অর্থাৎ রামমোহন রায়, রামরাম বসু, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর -- তাঁরা সকলেই শৈশব, কৈশোর ও প্রথম যৌবনে বাংলা গদ্যের থেকে ইংরেজি গদ্যই বেশি পড়েছিলেন বঙ্কিমচন্দ্র সম্বন্ধেও এ-কথা অনেকাংশে সত্য। রবীন্দ্রনাথের প্রজন্ম থেকে বঙ্কিমচন্দ্রের গদ্য শিক্ষিত বাঙালিসমাজে সর্বজনপাঠ্য হয়। অতএব ইংরেজি গদ্যের উপর কোনো বাঙালি লেখকের দখল যে তাঁর বাংলা গদ্যরচনায় প্রভাব বিস্তার করতে পারে তা বুঝতে অসুবিধা হয় না। এই ব্যাপারটি বিস্তারিতভাবে তুলে ধরলাম কারণ সত্যজিতের সমসাময়িক বা পরবর্তী সাহিত্যিকদের মধ্যে কারুর গদ্যেই ইংরেজি গদ্যের বিশেষ প্রভাব দেখিনি সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়কে তাঁর স্যাটায়ার-ধর্মী লেখায় কিছুটা ব্যতিক্রম বলা যায়। বাংলাগদ্যের বয়স আজ দু'শ বছর, ইংরেজি গদ্যের পাঁচশ' বছর এই দীর্ঘতর ইতিহাসের জন্য ইংরেজি গদ্যের স্থিতিশীলতা, বিস্তার ও শব্দভাণ্ডারের বৈচিত্র্য কিছুটা বেশি সত্যজিতের গদ্যের যে সাবলীলতা ও ন্যাকামি-বিবর্জিত ঋজুতা, তার উত্স অনেকটাই ইংরেজি গদ্যে তাঁর গভীর অভিনিবেশ।
ডিটেকটিভ গল্প-উপন্যাসে সত্যজিতের পূর্বসূরী শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়, হেমেন্দ্রকুমার রায়, নীহাররঞ্জন রায়। তবে এই লেখকরা, বিশেষত শরদিন্দু, অনেক ক্ষেত্রে বড়োদের জন্যই লিখেছেন সত্যজিৎ কিশোরকিশোরীদের জন্য লিখতেন বলে তাঁর ডিটেকটিভ কাহিনীতে শরদিন্দুর কাহিনীর মতো জটিল রহস্য থাকতো না তবে দেশে-বিদেশে নানা জায়গায় ফেলু-তোপসে-লালমোহনের অভিযান, মগনলাল মেঘরাজের দুর্ধর্ষ ভিলেন, রোমাঞ্চকর সাসপেন্স -- সব মিলিয়ে সত্যজিতের ডিটেকটিভ গল্প একটা জমকালো জাঁকজমকের ব্যাপার, যার আকর্ষণ এড়ানো কঠিন। তাছাড়া ফেলুদাই বোধহয় একমাত্র বাঙালি ডিটেকটিভ চরিত্র, যাকে শুধু ভারতের নানা জায়গায় নয়, এশিয়া ও ইউরোপের কয়েকটি জায়গাতেও গোয়েন্দাগিরির কাজে যেতে হয়েছে। অন্যান্য ডিটেকটিভ কাহিনীলেখকদের মধ্যে কেউই বোধহয় সত্যজিতের মতো এতোদিন বিদেশে কাটাননি, তাই তাঁদের গল্পে বিদেশ বিরল।
 তবে সায়েন্স ফিকশনে সত্যজিতের লেখাকে প্রথম স্থানটি ছেড়ে দিতে হবে। তাঁর সমসাময়িক অনেক সাহিত্যিক সায়েন্স ফিকশন লিখেছেন ঠিকই, তবে প্রোফেসর শঙ্কুর মতো একটি স্থায়ী চরিত্র কেউই সৃষ্টি করতে পারেননি। সত্যজিৎ ইংরেজি সায়েন্স ফিকশন বিস্তর পড়েছিলেন কল্পবিজ্ঞানভিত্তিক রচনায় সিদ্ধহস্ত হয়ে উঠতে তাঁর বেশিদিন লাগেনি।
তবে সায়েন্স ফিকশনে সত্যজিতের লেখাকে প্রথম স্থানটি ছেড়ে দিতে হবে। তাঁর সমসাময়িক অনেক সাহিত্যিক সায়েন্স ফিকশন লিখেছেন ঠিকই, তবে প্রোফেসর শঙ্কুর মতো একটি স্থায়ী চরিত্র কেউই সৃষ্টি করতে পারেননি। সত্যজিৎ ইংরেজি সায়েন্স ফিকশন বিস্তর পড়েছিলেন কল্পবিজ্ঞানভিত্তিক রচনায় সিদ্ধহস্ত হয়ে উঠতে তাঁর বেশিদিন লাগেনি।
প্রোফেসর শঙ্কুর গল্পগুলির পটভূমিকা দেশ ও বিদেশ দুইই শঙ্কুর বন্ধু ও সহকর্মীদের মধ্যে অধিকাংশই বিদেশি একশৃঙ্গ অভিযান বা হিপনোজেন-এর মতো কল্পবিজ্ঞানভিত্তিক গল্প বাংলায় আবার কবে লেখা হবে, বা আর কখনো লেখা হবে কিনা, কে জানে।
সত্যজিতের বাংলা লেখা নিয়ে সংক্ষেপে লিখলাম চরিত্র নিয়ে আলোচনার অবকাশ আছে, তবে তার জন্য স্বতন্ত্র প্রবন্ধের প্রয়োজন। ইংরেজি লেখা নিয়েও বিস্তারিত আলোচনা হতে পারে, তবে দু:খের বিষয় ইংরেজিতে সত্যজিৎ বেশি লেখেননি, ঠিক যেমন প্রাপ্তবয়স্কদের জন্য বাংলা গল্পও তিনি কমই লিখেছেন ( পিকুর ডায়রি ও অন্যান্য )। এটা আমার কাছে বিশেষ আক্ষেপের বিষয়, তবে সে আক্ষেপকে তো ব্যাজস্তুতিই বলা যায়। এই প্রসঙ্গ দিয়েই প্রবন্ধ শেষ করতে চাই।
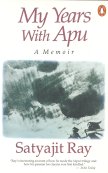 চলচ্চিত্র পরিচালনা ও অবসরে বাংলা কিশোরসাহিত্য রচনায় সত্যজিৎ এতোটাই ব্যস্ত থাকতেন যে ইংরেজি গদ্যরচনায় বিশেষ সময় দিতে পারতেন না। অথচ তাঁর চণ্ণশ যঠত্স্য, মচ্ংঠশ যঠত্স্য বা শেষ জীবনে রচিত ংঔষ্ হৃংছশয গঠঞচ্ ংঋংইণ্ণ যিনি পড়েছেন তিনিই জানেন সেই গদ্যের মহিমা। আমি তো বলবো নন-ফিকশন-এ নীরদচদ্র চৌধুরী বাদে আর কোনো ভারতীয় সত্যজিতের মতো সুঠাম ইংরেজি গদ্য লিখতে পারেননি। আমি বহু ভাবনা-চিন্তার পর এ-কথা লিখলাম, নানাযুগের ইংরেজি গদ্য পড়বার যাবতীয় অভিজ্ঞতার উপর ভিত্তি করে। সত্যজিতের গদ্যের ভারসাম্য ও ঋজুতা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ংঔষ্ হৃংছশয গঠঞচ্ ংঋংইণ্ণ বইটিতে যে
রস্মৃতিরোমন্থন আছে তা অতি সহজেই অতিপেলবতার দিকে ঝুঁকতে পারত, কিন্তু সত্যজিতের ইংরেজি-জ্ঞান এতো প্রখর ছিল যে গদ্য কখনো বলিষ্ঠতা হারায়নি। ইংরেজিতে যাকে "উইট" বলে, এই গদ্যের প্রায় প্রতিটি বাক্যেই তা বিদ্যমান। আমার ক্ষোভ : সত্যজিৎ ইংরেজিতে আরো অনেক কিছু লিখে যেতে পারতেন। শেষবয়সে শরীরের দৌর্বল্যের জন্য যখন চলচ্চিত্র পরিচালনার কাজ কঠিন হয়ে পড়েছিল, তখন হয়তো ইংরেজি লেখার দিকে মন দিতে পারতেন কিন্তু জীবনের শেষ পাঁচবছরে সভ্যতা সম্বন্ধেই কিছু গভীর সংশয় মনে বাসা বেঁধেছিল, আগন্তুক -এ যার প্রকাশ। নতুন করে আর গদ্যশিল্পীর জীবন আরম্ভ করা সম্ভব হয়নি।
চলচ্চিত্র পরিচালনা ও অবসরে বাংলা কিশোরসাহিত্য রচনায় সত্যজিৎ এতোটাই ব্যস্ত থাকতেন যে ইংরেজি গদ্যরচনায় বিশেষ সময় দিতে পারতেন না। অথচ তাঁর চণ্ণশ যঠত্স্য, মচ্ংঠশ যঠত্স্য বা শেষ জীবনে রচিত ংঔষ্ হৃংছশয গঠঞচ্ ংঋংইণ্ণ যিনি পড়েছেন তিনিই জানেন সেই গদ্যের মহিমা। আমি তো বলবো নন-ফিকশন-এ নীরদচদ্র চৌধুরী বাদে আর কোনো ভারতীয় সত্যজিতের মতো সুঠাম ইংরেজি গদ্য লিখতে পারেননি। আমি বহু ভাবনা-চিন্তার পর এ-কথা লিখলাম, নানাযুগের ইংরেজি গদ্য পড়বার যাবতীয় অভিজ্ঞতার উপর ভিত্তি করে। সত্যজিতের গদ্যের ভারসাম্য ও ঋজুতা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ংঔষ্ হৃংছশয গঠঞচ্ ংঋংইণ্ণ বইটিতে যে
রস্মৃতিরোমন্থন আছে তা অতি সহজেই অতিপেলবতার দিকে ঝুঁকতে পারত, কিন্তু সত্যজিতের ইংরেজি-জ্ঞান এতো প্রখর ছিল যে গদ্য কখনো বলিষ্ঠতা হারায়নি। ইংরেজিতে যাকে "উইট" বলে, এই গদ্যের প্রায় প্রতিটি বাক্যেই তা বিদ্যমান। আমার ক্ষোভ : সত্যজিৎ ইংরেজিতে আরো অনেক কিছু লিখে যেতে পারতেন। শেষবয়সে শরীরের দৌর্বল্যের জন্য যখন চলচ্চিত্র পরিচালনার কাজ কঠিন হয়ে পড়েছিল, তখন হয়তো ইংরেজি লেখার দিকে মন দিতে পারতেন কিন্তু জীবনের শেষ পাঁচবছরে সভ্যতা সম্বন্ধেই কিছু গভীর সংশয় মনে বাসা বেঁধেছিল, আগন্তুক -এ যার প্রকাশ। নতুন করে আর গদ্যশিল্পীর জীবন আরম্ভ করা সম্ভব হয়নি।
শেষের দিককার সত্যজিৎ তাঁর চলচ্চিত্রে আগের থেকে কম লিরিকাল শাখা প্রশাখা ও বিশেষত আগন্তুক -এ তিনি ইবসেন-এর মতো এক "থিংকার"। এই সত্যজিতের চিন্তার বাহন ইংরেজি গদ্য হতেও পারত, যেমন নীরদচন্দ্রের ক্ষেত্রে আজীবন হয়েছে -- তবে আমার মনে হয়, সত্যজিৎ লেখালিখি নিয়ে বেশি চিন্তাভাবনা করতে চাননি করলে কী কীর্তি রেখে যেতে পারতেন তা শুধুমাত্র অনুমানই করতে পারা যায়। তবে তাঁর ইংরেজি গদ্য মনোযোগ সহকারে পড়লে বুঝতে পারা যায় যে প্রাপ্তবয়স্ক ও প্রাপ্তমনস্কদের যে বইয়ের জগৎ তারও একাংশ অধিকার করে যাওয়ার ক্ষমতা বোধহয় তাঁর ছিল। সে ক্ষমতা তিনি প্রয়োগ করেননি। এটাকে একটা ট্রাজেডি বলা যায়।
এক পরিচিত ব্যক্তি আমার এই মত শুনে বলেছিলেন, "আরে, একটা লোককে সব কিছু করতে হবে তার কী মানে? উনি তো সিনেমায় যুগান্তকারী কাজ করে গেছেন ... আবার সিরিয়াস লেখা বেশি লেখেননি, এসব কথা তুলছেন কেন?" আমি বলেছিলাম -- "দেখুন, আমি আইডিয়ালিস্ট ওই আক্ষেপটা ... ওই হা-হুতাশটা আমাকে রাখতেই হবে। ঝঞ ঠয ছত্র ঠত্রঞংভশছৎ ংঋছশঞ ধী স্ষ্ চ্ধস্ছভং ঞধ ওছষ্ ঞচ্ং গশঠঞংশ ছত্ররু ঞচ্ঠত্রূংশ.
- এই লেখাটি পুরোনো ফরম্যাটে দেখুন
- মন্তব্য জমা দিন / Make a comment
- মন্তব্য পড়ুন / Read comments
- কীভাবে লেখা পাঠাবেন তা জানতে এখানে ক্লিক করুন | "পরবাস"-এ প্রকাশিত রচনার দায়িত্ব সংশ্লিষ্ট রচনাকারের/রচনাকারদের। "পরবাস"-এ বেরোনো কোনো লেখার মধ্যে দিয়ে যে মত প্রকাশ করা হয়েছে তা লেখকের/লেখকদের নিজস্ব। তজ্জনিত কোন ক্ষয়ক্ষতির জন্য "পরবাস"-এর প্রকাশক ও সম্পাদকরা দায়ী নন। | Email: parabaas@parabaas.com | Sign up for Parabaas updates | © 1997-2025 Parabaas Inc. All rights reserved. | About Us