-
পরবাস
বাংলা ভাষা, সাহিত্য ও সংস্কৃতি
Parabaas, a Bengali webzine since 1997 ... ISSN 1563-8685 -
ছোটদের পরবাস
Satyajit Ray
Rabindranath Tagore
Buddhadeva Bose
Jibanananda Das
Shakti Chattopadhyay
সাক্ষাৎকার -
English
Written in English
Book Reviews
Memoirs
Essays
Translated into English
Stories
Poems
Essays
Memoirs
Novels
Plays
-

পুত্রবধূর চোখে গৌরী আইয়ুব এবং প্রসঙ্গত
-

বিশ্বের ইতিহাসে হুগলি নদী
-

বেদখল ও অন্যান্য গল্প
-

Audiobook
Looking For An Address
Nabaneeta Dev Sen
Available on Amazon, Spotify, Google Play, Apple Books and other platforms.
-

পরবাস গল্প সংকলন-
নির্বাচন ও সম্পাদনা:
সিদ্ধার্থ মুখোপাধ্যায়)
-

Parabaas : পরবাস : বাংলা ভাষা, সাহিত্য ও সংস্কৃতি -
পরবাস | Rabindranath Tagore | প্রবন্ধ
Share -
রবীন্দ্রসংগীতের আয়নামহল : সুধীর চক্রবর্তী
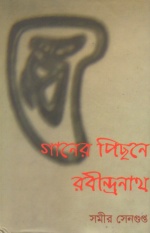 গানের পিছনে রবীন্দ্রনাথ -- রবীন্দ্রনাথের গান: রচনার কাহিনী, সমীর সেনগুপ্ত , প্যাপিরাস, কলকাতা ২০০৭, পৃ: ২৪০।
গানের পিছনে রবীন্দ্রনাথ -- রবীন্দ্রনাথের গান: রচনার কাহিনী, সমীর সেনগুপ্ত , প্যাপিরাস, কলকাতা ২০০৭, পৃ: ২৪০।
প্রয়াণের দু'বছর আগে ১৯৩৯ সালের ১৪ মে রবীন্দ্রনাথ মংপুতে মৈত্রেয়ী দেবীর সামনে বলেছিলেন : "দেখো রবিঠাকুর গান মন্দ লেখে না, একরকম চলনসই তা বলতেই হবে । ... কম গান লিখেছি? হাজার হাজার গান, গানের সমুদ্র - সেদিকটা বিশেষ কেউ লক্ষ্য করে না গো, বাংলাদেশকে ভাসিয়ে দিয়েছি। আমাকে ভুলতে পার, আমার গান ভুলবে কী করে?"। এমন মন্তব্য পড়লে কেমন যেন লাগে এখন, যখন, রবীন্দ্রনাথের গান আমাদের বঙ্গজীবনের, যাপনের, সংস্কৃতির সর্বস্ব । কিন্তু জীবিতকালে তিনি তাঁর গানের এমন প্রসার আর প্রতিপত্তি তো দেখে যান নি। সেই গানের সমৃদ্ধ কিন্তু সংকীর্ণ আসন তখন পাতা হয়েছিল সম্ভ্রান্ত কটি নারীকন্ঠে, আঙুলে গোনা কজন প্রশিক্ষকের প্রযত্নে এবং শান্তিনিকেতনের পরিসরে। হাজার হাজার গান (প্রকৃত গণনায় দু'হাজারের কিছু কম) এবং গানের সমুদ্র যে তাতে সন্দেহ নেই। সেই সমুদ্রে আমরা ঢেউ খেলেছি ডুব দিয়েছি কেটেছি সাঁতার, পেয়েছি কৃতার্থতার পুণ্য, কিন্তু সে সব ঘটেছে অনেক পরে। গানের আনন্দযজ্ঞে সবার নিমন্ত্রণের যে আয়োজন তিনি করে রেখে গেছেন, তাঁর জীবিতকালে 'সেদিকটা কেউ লক্ষ্য করে না গো' বলে এই যে অভিমান বা ক্ষোভ সেটাই সত্যি। সে কালের ইতিহাস ভালো করে অনুধাবন করলে বোঝা যায়, তাঁর সত্যিকারের আমগ্ন অনুরাগী যেমন বেশ কজন ছিলেন তেমনই বিরোধী শিবিরও ছিল বেশ দলে ভারি। সেই রকমই ছিল তাঁর গানের সমঝদারির অর্থাৎ শ্রোতাদের সংখ্যা। তাই ১৮৯৫-এ শিলাইদহে লেখা 'ঝর ঝর বরিষে বারিধারা'-র মতো চমত্কার গানটি সম্পর্কে দুজন সমসাময়িক বিশিষ্ট ব্যক্তির বিরূপ মন্তব্য আমাদের ভাবিয়ে তোলে। গানটি প্রকাশিত হয়েছিল 'ভারতী' পত্রিকার ১৩০৪ আষাঢ় সংখ্যায়। পরের ভাদ্র মাসের 'সাহিত্য' পত্রিকায় সুরেশচন্দ্র সমাজপতি গানটি সম্পর্কে লেখেন :
'স্বরলিপি'তে শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের একটি গান আছে। গানটি সুনির্বাচিত সুমিষ্ট শব্দের সমষ্টি মাত্র ভাবের বিশেষত্ব, যাহা রবীন্দ্রনাথের ন্যায় কবির নিকট আশা করা যায়, ইহাতে তাহার সম্পূর্ণ অভাব ।
এখানে লক্ষ করার বিষয় যে একটা গানের বিষয়ে আলোচনা বা বিরূপ মন্তব্য করা হচ্ছে তার সুর তাল ও গায়নকে বিবেচনার মধ্যে না এনে। তাই গানকে মনে হচ্ছে সুমিষ্ট সুনির্বাচিত শব্দসমষ্টিমাত্র অর্থাৎ এ যেন গানকে অসম্পূর্ণভাবে দেখা। আশ্চর্য যে, এই গানটাই আমরা যখন পড়ি তখন মনের মধ্যে বয়ে চলে সুরস্মৃতির স্রোত। 'হায় গৃহবাসী হায় পথহারা' উচ্চারণের পর হা আ আ আ আ রা -র যে অনবদ্য তান তা শব্দসমষ্টিকে ডিঙিয়ে মনকে যে জায়গায় নিয়ে যায় তা অনির্বচনীয়। এরপরে 'ফিরে বায়ু' অংশ থেকে তার সপ্তকের কারুণ্য যেন শিলাইদহের সেই কবেকার পদ্মাবক্ষে উপর্ঝরণ বৃষ্টিধারায় কলরোলের ধ্বনি মনকে অতলে টানে। যিনি গানের মানুষ নন তাঁর পক্ষে গানের যথার্থ উপভোগ অসম্ভব এবং ঐ সংক্রান্ত মন্তব্য অনভিপ্রেত।
কিন্তু যিনি গানের সমঝদার? আর তিনি যখন 'গীতসূত্রসার'-এর মতো বইয়ের গ্রন্থকার ও বহুতর উচ্চাঙ্গের গানের ভোক্তা কৃষ্ণধন বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতো মানুষ হন তখন তাঁর মন্তব্য ও বিরূপতা ভাবিয়ে তোলে। তিনি জ্যোতিরিন্দ্রনাথকে চিঠিতে লিখেছিলেন :
.... বিশেষ রবিবাবু-কৃত কথাগুলিতে ছন্দমাত্র নাই। ঐ সকল কথাতে ভাব ও কবিত্ব থাকিতে পারে। কিন্তু ছন্দহীন কথা গানের নিতান্ত অনুপযোগী। রবিবাবু ভাবের খাতিরে ছন্দ এড়াইয়া পদ্য রচনা সহজ করিয়া লইয়াছেন।...
সুরেশচন্দ্রের অভিযোগ রবীন্দ্রনাথের গানে 'ভাবের সম্পূর্ণ অভাব' আর কৃষ্ণধনের অভিযোগ সেই গানে 'ভাব ও কবিত্ব' থাকলেও 'ছন্দমাত্র নাই'। এখানে ছন্দ মানে কি কবিতার ছন্দ? সেকথা স্পষ্ট নয়, কিন্তু আমরা জানি গানের বাণীতে কবিতার মতো ছন্দের অতিনিরূপতা থাকে না, তার গড়ন হয়ে থাকে সুরের অনুষঙ্গে, লয়ের প্রয়োগে কাব্যছন্দের ফাঁকফোঁকর ভরিয়ে নেওয়া যায়। আসলে একটা কথা আমরা মনে রাখি না যে গানের ক্ষেত্রে সবচেয়ে আগে থাকেন স্রষ্টা, তারপরে তাঁর সৃষ্টি। তারপরে আসবে সেই গানের যথাযথ গায়ন তথা শিল্পী - তবে তো সমঝদার আসবেন। রবীন্দ্রনাথ একথা খুব ভালো বুঝেছিলেন বলে শান্তিনিকেতনে প্রতিষ্ঠা করেছিলেন সংগীতভবন। সেখানে এনেছিলেন তাঁর গান রূপায়ণে দক্ষ প্রশিক্ষক, যিনি স্বরলিপি সচেতন। তাঁরাই গড়ে তুলেছেন গানের দল ও রবীন্দ্রগান পরিবেশনের প্রকৃত পদ্ধতি। এর যোগফলে ক্রমে ক্রমে তৈরি হয়েছে শ্রোতা, ভোক্তা ও সমঝদারির ভিত। তাঁর গান খুব সহজে এদেশে মুগ্ধতার মোহরছাপ অর্জন করে নি, তাই তাঁকে অন্ত্য বয়সে সখেদে বলতে হয় তাঁর গানের সমুদ্রকে, তার বিস্তার ও অতলতা, তার বিক্ষেপ ও চাঞ্চল্য, তার অন্তর্গত মৌন অথচ গভীর বাণীকে বিশেষ কেউ লক্ষ করে না, অন্তত তখনও পর্যন্ত করে নি। তবু প্রত্যয়ী কন্ঠে বলেছেন, 'আমার গানকে ভুলবে কী করে?'
ক্রান্তদর্শীর সেই ভবিষ্যৎবাণী সফল হয়েছে। তাঁর সার্ধ শতবর্ষের আসন্ন সময়ে আমরা তাঁর গানেই আপ্লুত - যে গানের যথার্থ স্বরূপ নির্ধারণ আজও করে উঠতে পারি নি আমরা, পারি নি তার বৈচিত্র্য, শৈল্পিক অনন্যতা ও গায়ন পদ্ধতির পরিমাপ করতে। কিন্তু সেই উদ্যোগে আমাদের ক্ষান্তি নেই। সমুদ্র সদৃশ সেই গানের মহাদেশ ও তার অন্তরমহল কেবলই খুঁজে চলেছি নানা প্রয়াসে ও প্রযত্নে। এই যেমন ২৪০ পৃষ্ঠাব্যাপী একটি বইয়ে সমীর সেনগুপ্তের মেধাবী অন্বেষণ : 'গানের পিছনে রবীন্দ্রনাথ'। শিরোনাম থেকে বইয়ের উপজীব্য তত স্পষ্ট হয়ে ওঠে না তাই পড়তে হয় গ্রন্থ পরিচিতি। যাতে বলা আছে :
বহুকৌণিক মণির মতো, রবীন্দ্রনাথকেও দেখবার দৃষ্টিকোণের কোনো শেষ নেই। গানগুলির কথা ভাবি যদি - তাঁর বহুগানের পিছনে প্রচ্ছন্ন আছে গানটি রচনার ইতিহাস। স্বাভাবিক বা অস্বাভাবিক, নানা পরিস্থিতিতে গান রচনা করেছেন, সুর দিয়েছেন, গেয়েছেন তিনি। এইরকম প্রায় তিনশো গানের পিছনকার ইতিহাস সংগ্রহ করা হয়েছে এখানে - প্রতিটি তথ্যের প্রামাণিকতা প্রতিষ্ঠা করতে তাদের উত্স নির্দেশ করে দেওয়া হয়েছে। .... রবীন্দ্রনাথের অন্তর্জীবনের ইতিহাসটি বোঝবার পক্ষে এই কাহিনীগুলির গুরুত্ব তাই অসামান্য।
এবারে স্পষ্ট হল যে, সমীর সেনগুপ্ত গতানুগতিক অনুসন্ধানী নন । গানের সমুদ্রে তিনি নিপুণ ডুবুরি । গানবিদ্যাও তাঁর আয়ত্তে । সেইসঙ্গে আছে বিচারশীল এক স্থিরলক্ষ্য সঙ্কল্প।
কিন্তু মজার কথা এটাও যে দীর্ঘকাল আমরা রবীন্দ্রনাথের গান পড়েছি 'গীতবিতান' থেকে এবং তার সুরকাঠামো তথা তান মান লয় ও তাল বুঝেছি নিয়েছি 'স্বরবিতানে'র খণ্ডগুলি থেকে। দুটি সংকলনেই রবীন্দ্রগীতির কালক্রম মানা হয় নি, উল্লেখ করা হয় নি তার রচনাগত পটভূমি বা উপলক্ষ্য। রবীন্দ্রনাথ নিজেও বোধহয় সেরকম চান নি, সে কারণে তাঁর প্রত্যক্ষ নির্দেশনায় যে 'গীতবিতান' প্রকাশ পায় তাতে তাঁর গানগুলিকে তিনি উপস্থাপন করেছিলেন ভাবের দিক থেকে তাই তার বিন্যাস করেছিলেন 'পূজা', 'প্রেম', 'স্বদেশ', 'প্রকৃতি', 'আনুষ্ঠানিক' ও 'বিচিত্র' জাতীয় শিরোনামে সাজিয়ে। তার ফলে একদুই দশক আগেও প্রাণভরে শুধু রবীন্দ্রসংগীত শুনেছি আর ভেসে গেছি তার কথা ও সুরের সুস্মিত যৌগপদ্যে, তার গায়নবিশিষ্টতায় ও সাংগীতিক লাবণ্যে। জানতে চাই নি কোন গানের পরে তাঁর কোন গান রচিত হয়েছিল, সে সব গান কোন পরিবেশে কেমন মানসিক বা প্রাকৃতিকতার মধ্যে জন্ম নিয়েছিল। কারা ছিলেন তার প্রথম শ্রোতা, কেমন হয়েছিল সে সব গানের প্রত্যক্ষ প্রতিক্রিয়া। শান্তিদেব, ইন্দিরা বা শৈলজারঞ্জন তাঁদের কিছু লেখায় কয়েকটি গানের রচনা কাহিনী ও উপলক্ষ্য বিবৃত করেছিলেন। আরও কারো কারোর টুকরো রচনায় বা আত্মকথায় পাওয়া গেছে একটি দুটি গানের সৃষ্টি অনুষঙ্গ কিন্তু সমীর সেনগুপ্তই সর্বপ্রথম বড় মাপে প্রশস্ত পরিসরে গানের পিছনের রবীন্দ্রনাথকে ব্যক্ত করলেন - ব্যক্ত হল অনন্তের চিরবিস্ময়। অবশ্য তাঁর কাজ সহজতর হয়েছে পশ্চিমবঙ্গ সরকার প্রকাশিত রবীন্দ্ররচনাবলীর ৪র্থ খণ্ড প্রকাশের ফলে, কারণ এই খণ্ডেই সর্বপ্রথম রবীন্দ্রসংগীতগুলি কালানুক্রম মেনে যথাসম্ভব স্থান ও সময়ের উল্লেখে বিন্যস্ত হয়েছিল।
সমীর সেনগুপ্ত আমাদের একজন মান্য গবেষক। ১৯৪০ সালের জাতক এই কুতূহলী ব্যক্তি তুলনামূলক সাহিত্য পাঠ করেছেন যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে বুদ্ধদেব বসু আর সুধীন্দ্রনাথ দত্ত-র প্রত্যক্ষ নির্দেশে । ফলে তাঁর ভাবনাকাঠামো ও নানাদিক ধাবিত জিজ্ঞাসা প্রথম থেকেই উঁচুতারে বাঁধা ছিল । যার চমকপ্রদ উদাহরণ পাই তাঁর লেখা বুদ্ধদেব বসুর জীবন রচনার এবং শক্তি চট্টোপাধ্যায় সংক্রান্ত নানা অজানা তথ্যের উন্মোচনে । রবীন্দ্রনাথ বিষয়ে সমীরের জানাচেনার প্রয়াস একটু বিচিত্র পথগামী । যার প্রথম পরিচয় `রবীন্দ্রনাথের আত্মীয়স্বজন' ও `সমকাল ও রবীন্দ্রনাথ' বই দুটিতে । তারপরে ২০০৭ এর মে মাসে বেরোয় এই `গানের পিছনে রবীন্দ্রনাথ' বই, যাতে বিপুল বৈচিত্র্যে পরিকীর্ণ, বহুতর তথ্যে সমৃদ্ধ রবীন্দ্রগীতি সমুদ্রের ২৯৮টি গানের সূত্রসন্ধান করে তিনি আমাদের দিশা দিয়েছেন যেমন তেমনই ধন্য করেছেন । তাঁর বইটির মধ্যে যে ব্যাপারটি প্রচ্ছন্ন রয়েছে তা হল বহুপঠনের চিহ্ন । এটা স্পষ্ট যে, রবীন্দ্রনাথের গান বিষয়ে তাঁর জীবিতকালে আর মরণোত্তর সময়ে যেখানে যেটুকু মুদ্রিত তথ্য আছে তা তিনি পড়েছেন, নোট করেছেন এবং বিচার করে বুঝতে চেয়েছেন সেই তথ্য কতটা নির্ভরযোগ্য । প্রয়োজনে কোনো নামী প্রত্যক্ষদর্শীর লিখিত বয়ান তিনি খারিজ করতে বা সন্দেহ করতে দ্বিধা করেন নি । এর থেকে বোঝা যাচ্ছে রবীন্দ্রনাথ বা তাঁর প্রত্যক্ষ স্নেহভাজনদের সম্পর্কে সমীর ভক্তিপথযাত্রী নন, বরং সত্য উদ্ঘাটনে তত্পর । এতে শ্রোতাদের বা আমাদের মতো জিজ্ঞাসুদের বিশেষ উপকার হয়েছে । একটি নমুনা দেখা যাক ।
`মহারাজ এ কী সাজে এলে হৃদয়পুরমাঝে' গানটি প্রসঙ্গে অতুলপ্রসাদ সেন লিখেছেন :
`১৮৯৬ সালে তাঁহার (রবীন্দ্রনাথের) নেতৃত্বে "খামখেয়ালী সভা" নামে একটি সাহিত্য ও সংগীত মণ্ডলী স্থাপিত হয় । আমি সভার কনিষ্ঠতম সভ্য ছিলাম । ... খামখেয়ালীর আসরে বিখ্যাত গায়ক রাধিকানাথ (প্রসাদ) গোস্বামী তাঁর উচ্চাঙ্গের তানলয় মণ্ডিত গান গাহিয়া আমাদের মনোরঞ্জন করিতেন । রবীন্দ্রনাথের সংগীত প্রতিভা এমন সর্বমুখী যে গোস্বামী মহাশয়ের উপাদেয় সুরে তিনি গান বাঁধিতেন এবং সে নবরচিত গানগুলি রাধিকানাথ (প্রসাদ) খামখেয়ালীর আসরে গাহিয়া শুনাইতেন । তন্মধ্যে একটি গান মনে আছে - "মহারাজ এ কী সাজে"...'
এ সম্পর্কে সমীর সেনগুপ্তের মন্তব্য : `অতুলপ্রসাদের স্মৃতি নিশ্চয়ই তাঁর সঙ্গে প্রতারণা করে থাকবে, কারণ যে তারিখ দেওয়া হয়েছে গানটি রচিত হয়েছিল তার ১৩ বছর পরে । তা ছাড়া রাধিকাপ্রসাদের নামেও দুবার ভুল আছে । গানটি অবশ্য হিন্দিভাঙা, মূল গানটি হল "মেরে দুন্দ দল সাজে দশরথসুত রাম"' (দ্র. গবেষণা - গ্রন্থমালা - ৩)।রবীন্দ্রগানের উত্সসন্ধানে নেমে লেখক কতটা সতর্ক তা যেমন বোঝা যায় তেমনই লক্ষণীয় যে রবীন্দ্রগীতির প্রত্যক্ষ শ্রোতাদের বয়ানে কতটাই ধূসরতা রয়ে গেছে । তবে অতুলপ্রসাদের পরিবেশিত তথ্যের মধ্যে যে ইঙ্গিতটি আছে, অর্থাৎ রাধিকাপ্রসাদের গাওয়া রাগদারী গানের আদলে রবীন্দ্রনাথ বাণী লিখতেন সেই সূত্রে খুঁজে পেয়েছেন মূল গানটি । এতে কৌতূহলের বৃত্ত পূর্ণ হল এবং স্পষ্ট হল এই প্রবণতা যে মূল গানের স্মৃতিতে রবীন্দ্রনাথ কখনও কখনও ১৩ বছর পরেও গান বেঁধেছেন ।
স্মৃতিগত প্রতারণার আরেকটি নমুনা সমীর দেখিয়েছেন `আজ সবার রঙে রঙ মিশাতে হবে' গানটি প্রসঙ্গে । শান্তিনিকেতনের প্রথম যুগের ছাত্রী অমিতা সেন তাঁর `নৃত্য রচনায় রবীন্দ্রনাথ' নিবন্ধে (শারদীয় যুগান্তর ১৩৮৮) লিখেছেন :
সেবার শারদোত্সবের শেষে "আজ সবার রঙে রঙ মিশাতে হবে" গানটিতে আমরা সবাই একসঙ্গে নেচেছিলাম । রবীন্দ্রনাথ নাচছেন বাউলের ভঙ্গিতে, আমরা আমাদের রঙবেরঙের ওড়না আকাশের দিকে উড়িয়ে চঞ্চল পায়ে ঘুরে ঘুরে নাচছি আর গাইছি । ... অবন, গগন, সমর সবাই উঠে নাচে যোগ দিয়েছিলেন । দুহাতে তুড়ি বাজিয়ে বাজিয়ে পায়ে তালের ঠেকা দিয়ে নাচছেন দিনদা । আর আমাদের সঙ্গে নাচছেন এলমহার্স্ট সাহেব, বেনোয়া সাহেব । ...
সমীর সেনগুপ্ত প্রশ্ন তুলেছেন :
এটি কবেকার কথা ? শান্তিনিকেতনের কথা নিশ্চয়ই নয়, কারণ অবনীন্দ্রনাথরা তিনভাই একসঙ্গে কখনো সেখানে যান নি । এটি সম্ভবত ১৩২৯ বঙ্গাব্দে কলকাতায় অভিনয়ের স্মৃতি, অর্থাৎ ১৯২২ খৃষ্টাব্দ । পরপর দুদিন শারদোত্সব অভিনীত হয়েছিল, প্রথম দিন আলফ্রেড থিয়েটারে, পরদিন ম্যাডান থিয়েটারে । রবীন্দ্রনাথ সন্ন্যাসীর ভূমিকায় অভিনয় করেছিলেন, দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর্দা, রাজার ভূমিকায় গগনেন্দ্রনাথ, মন্ত্রী হয়েছিলেন সমরেন্দ্রনাথ । দ্বিতীয় দিন (১৮ সেপ্টেম্বর) পিতা দ্বিপেন্দ্রনাথের মৃত্যুসংবাদ পেয়ে দিনেন্দ্রনাথ বোলপুর ফিরে যান, কয়েকঘন্টার মধ্যে তৈরি হয়ে অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর্দার ভূমিকায় নামেন । অমিতা সেনের (জন্ম ১৭ই জুলাই ১৯১২) বয়স তখন দশ ।
দশ বছর বয়সের বাল্যস্মৃতি প্রতারণা করতেই পারে । তবে এলমহার্স্ট ও বেনোয়া সাহেবের প্রসঙ্গ কোনো অজ্ঞাত কারণে সমীর এড়িয়ে গেছেন । তাঁরা তো শান্তিনিকেতনেই থাকতেন ।

॥ ২ ॥
এই পর্যন্ত এসে আমরা মুখোমুখি হই এক তাত্ত্বিক প্রশ্নের । কোনো গানের উপভোগে কি সেই গানের রচনাকাল, পটভূমি বা গীতিকারের ব্যক্তিগত অনুষঙ্গ আমাদের প্রকৃতই কাজে লাগে ? ধরা যাক, `গানের পিছনে রবীন্দ্রনাথ' বই থেকে জানা যাচ্ছে `অন্ধজনে দেহো আলো' গানটি ১৮৮৬ সালে রচিত । এবারে প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশের নিজস্ব বয়ানে ১৯২২ সালে রবীন্দ্রনাথের স্বকন্ঠে শোনার স্মৃতি উদ্ধার করেছেন সমীর :
... মন যখন ক্লিষ্ট তখন কোনো কোনো সময় নিজের মনে গান করতেন । .. ৬ই পৌষ সন্ধ্যাবেলা শান্তিনিকেতনে গিয়ে পৌঁচেছি । কবি তখন থাকেন ছোটো একটা নতুন বাড়িতে - পরে এ বাড়ির নাম হয় `প্রান্তিক' । শুধু দুখানা ছোটো ঘর । খাওয়ার পরে আমাকে বললেন, তুমি এখানেই থাকবে । ... গভীর রাতে ঘুম ভেঙে গিয়ে শুনতে পেলুম গান করছেন `অন্ধজনে দেহো আলো' । বারবার ফিরে ফিরে গান চলল, সারারাত ধরে । ফিরে ফিরে সেই কথা, `অন্ধজনে দেহো আলো' । সকালে মন্দিরের পরে বললুম, `কাল তো আপনি সারা রাত ঘুমোন নি ।' একটু হেসে বললেন, `মন বড়ো পীড়িত ছিল তাই গান করছিলুম । ভোরের দিকে মন আকাশের মতোই প্রসন্ন হয়ে গেল ।'
সমীর সেনগুপ্ত খোঁজ করে জানাচ্ছেন :এ সব ১৯২২ সালের কথা । যে পারিবারিক ব্যাপারের কথা উল্লেখ করা হয়েছে সেটি হল, রবীন্দ্রনাথের কনিষ্ঠা কন্যা মীরা দেবীর সঙ্গে তাঁর স্বামী নগেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের বিরোধ, যার পরিণামে তাঁদের বিচ্ছেদ ঘটে । পিতা রবীন্দ্রনাথকে সেই দুর্ভোগের অনেকখানি বহন করতে হয়েছিল ।
এই তথ্য থেকে বোঝা গেল ১৮৮৬ সালে লেখা একটি গান ১৯২২ সালের (অর্থাৎ ৩৬ বছর পরে) গভীর রাতে রবীন্দ্রনাথ একা একা গেয়ে চলেছেন আত্মবেদনা উপশমের জন্য । গান তাঁর এতটাই জীবন সম্পৃক্ত । ঠিকই । কিন্তু শ্রোতাহিসাবে এই বাড়তি তথ্যটুকু ঐ বিশেষ গানের উপভোগে কোনো কাজে লাগে কি ? প্রসঙ্গত মনে করতে পারি শঙ্খ ঘোষের এক মন্তব্য যে,
তথ্য গোপন করা আর তথ্য নির্মাণ করা, এ দুটো সম্ভাবনা থেকে যদি মুক্তিও পাওয়া যায় কখনো, সমস্যা তবু মেটেনা । যদি ঠিক-ঠিক তথ্যও হয়, তার উপর অতিনির্ভরতাই বা সত্যের কতটা কাছাকাছি নিতে পারে আমাদের । ... অধিকাংশ সময়ে আমাদের জানাটা থেকে যায় বিক্ষিপ্ত, থেকে যায় তথ্যসমাহার, বোধের জগৎ পড়ে থাকে অস্পৃষ্ট ।
শিল্প-আস্বাদনের প্রসঙ্গে কথাটা একবার তুলেছিলেন থিয়োডোর আডোর্নো । সংগীতের আসরে তার ইতিহাস নিয়ে খবরাখবর জানাবার প্রবণতা এত বাড়ছে দেখে তাঁর মনে হয়েছিল শ্রোতার বা উপভোক্তার নিজস্ব আস্বাদনের পথে সেটা হয়ে উঠছে মস্ত এক বাধা । নিজের অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে শিল্পে পৌঁছবার পথ হয়ে যাচ্ছে সংকুচিত, নিজস্ব বিকাশ হচ্ছে রুদ্ধ, যদিও খবর জানা হচ্ছে অনেক । কথাটা হয়তো এদেশের সাম্প্রতিক রবীন্দ্রসংগীত-জগতের পক্ষেও ভেবে দেখবার যোগ্য । গান শোনানোর সঙ্গে এ নিয়ে কোনোরকম তথ্যবিস্তার যে একেবারেই চলতে পারে না তা হয়তো নয়, কিন্তু সে সব কথা গানের অন্তর্জগতে কতটা পৌঁছে দেয় আমাদের আর কতটা-বা ব্যাহত করে, সেটাও বেশ ভাববার ।সমীর সেনগুপ্ত নিশ্চয়ই এই দোষে দোষী নন । গান শোনানোর সঙ্গে তথ্য পরিবেশনের দায় তো তিনি নেন নি । তিনি কেবল ২৯৮ টি রবীন্দ্রসংগীতের নেপথ্যলোককে উন্মোচন করেছেন । কিন্তু একটা আশংকা আছে । হালফিল বাংলা গানের আসরে দেখা যাচ্ছে গায়ক হয়ে পড়ছেন বাচক । ফলে এমনও হতে পারে, যে 'গানের পিছনে রবীন্দ্রনাথ' বই থেকে তথ্য সংগ্রহ করে কোনো শিল্পী হয়তো গানের আগে বাগ্বিস্তার করে বসবেন ।
এবারে দেখা দরকার, সমীর সেনগুপ্ত তাঁর এই শ্রমশীল অথচ সরস কাজটি সম্পর্কে আত্মপক্ষে কী বলতে চাইছেন : তাঁর পর্যবেক্ষণ হল,
রবীন্দ্রনাথের গান বিষয়ে আমাদের যাবতীয় ধারণা ও অভিজ্ঞতার পিছনে প্রবল একটি সময়হীনতার উপাদান কাজ করে চলে । কেমন আমাদের মনে হয়, এই গানগুলি অনাদিকাল থেকেই যেন এই রকমই সাজানো ছিল । চিরকাল ধরেই আমাদের জন্যে এই রকম থরে থরে বিন্যস্ত ছিল পূজার গান আর প্রেমের গান, বর্ষার গান আর বসন্তের গান । ...
এর জন্যে সবচেয়ে বেশী করে দায়ী অবশ্য গীতবিতান বইখানি । এতে গানগুলির রচনাকাল দেওয়া নেই, রচনাকাল অনুযায়ী গান সাজানোও নেই । ভাব অনুযায়ী গুচ্ছাকারে সাজানো সব গান, আমরাও সেইভাবেই ভাবতে অভ্যস্ত । এই সাজানোটায় আমাদের এমনই অভ্যেস হয়ে গেছে, শুনতে গিয়ে আমাদের মনেই পড়ে না যে ষোল বছরের একটি ছেলে লিখেছিল "গহন কুসুম কুঞ্জমাঝে" , সাতাশ বছরের এক যুবক লিখেছিল, "তবু মনে রেখো" , বা প্রায় আশি বছরে পৌঁছে এক বৃদ্ধ লিখেছিলেন, "আমার অঙ্গে সুরতরঙ্গে ডেকেছে বান, রসের প্লাবনে ডুবিয়া যাই" । "শাঙনগগনে ঘোর ঘনঘটা" থেকে "এসো এসো শ্যামছায়াঘন দিন" পর্যন্ত ১১২টি বর্ষার গান রচনা করতে যে সাতষট্টি বছর সময় লেগেছিল সেকথাও আমাদের মনে পড়ে না ।তাঁর কথাগুলিতে যেমন বাঁধন আছে তেমনই আবেগ আছে, আমাদের পক্ষে চমত্কৃত বিস্ময়ের উপাদানও যথেষ্ট আছে । কিন্তু ভাবতে হবে কেন এমন হল । রবীন্দ্রনাথ নিজেই কি তা চাননি ? তবে ?
মূল কথাটা হল আমাদের দেশে কোনো নামী সংগীতকারের ভেবেচিন্তে গীতি সংকলনের সুবিন্যস্ত ঐতিহ্য নেই । রবীন্দ্রনাথের সংগীতজীবনে যেমন `রবিছায়া' থেকে শুরু করে কয়েকটি গানের বই বেরিয়েছে । তেমনই দ্বিজেন্দ্রলালের `আর্য্যগাথা', অতুলপ্রসাদের `কয়েকটি গান', রজনীকান্ত-র `বাণী', `কল্যাণী' ও `অভয়া' বেরিয়েছে তাঁদের জীবিতকালে । দ্বিজেন্দ্রলালের `গান' আর `হাসির গান' আলাদাভাবে বেরিয়েছে । অতুলপ্রসাদের `গীতিগুঞ্জ' প্রকাশ পায় তাঁর মৃত্যুর পরে । তার সংকলনে সমস্যা হয়নি, কারণ তাঁর লেখা গানের সংখ্যা মাত্র ২০৮ খানি । দ্বিজেন্দ্রলালের `আর্য্যগাথা' ২টি খণ্ডে গান ও কবিতা মিলেমিশে আছে । রজনীকান্ত-র `বাণী' `কল্যাণী' `অভয়া' মিলে এক সম্পূর্ণ গীতিসংকলন বেরোয়নি । গত একবছর আগে বর্তমান লেখকের সম্পাদনায় বেরিয়েছে পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি থেকে `দ্বিজেন্দ্রগীতি সমগ্র' । দিলীপকুমার রায়ের কোনো সামগ্রিক গীতিসংকলন বেরোয় নি । নজরুল ইসলামের গান নানা বিন্যাসে দুই বাংলায় পুস্তকাকারে বেরিয়েছে তবে তাকে প্রকৃত অর্থে `নজরুল গীতিসমগ্র' বলা যাবে না । কারণ কেউই জানেন না নজরুলের গানের সঠিক সংখ্যা কত এবং তার সঙ্গে আরেক সংকট হল তাঁর নামে অন্যের লেখা গান চলে আসছে বহুদিন, সেগুলিকে আজ আলাদা করা যাবে না । নজরুলের জীবন ছিল চঞ্চল ও অবিন্যস্ত এবং পরে অপ্রকৃতিস্থ ।
এঁদের পাশে রবীন্দ্রনাথের নিজের গান সম্পর্কে গভীর প্রত্যয় ও ভালোবাসা । তাঁর ছিল এক দৃঢ় মনের সংগঠন এবং অনুরাগীদের বৃত্ত । প্রথম থেকেই তাঁর লক্ষ্য ছিল প্রতিটি গানকে সতর্ক স্বরলিপিতে ধরে রাখা, যাতে তাঁর গানে অন্যের করা সুরের খোদকারি না এসে যায় (যা নজরুল গীতিতে ব্যাপক) এবং গায়ন ও গান পরিবেশনে একটা সুনির্দিষ্ট রূপ আর অভিপ্রেত ব্যঞ্জনা ফোটে । তাঁর গানে শিল্পীর স্বাধীনতা নেই, তানকর্তবের অধিকার নেই । সুরবিহারের যথেচ্ছ সাবলীলতা নেই এসব অভিযোগ বহুদিন প্রচ্ছন্নভাবে বলবৎ ছিল এবং বহু গায়ক গায়িকা তাঁর গান গাইতেন না । দিলীপকুমার রায়ের সঙ্গে তাঁর ঘোরতর পত্র-বিতর্ক হয়েছিল একসময়ে । তিনি দিলীপকে লিখেছিলেন :
তুমি কি বলতে চাও যে, আমার গান যার যেমন ইচ্ছা সে তেমনভাবে গাইবে ? আমি তো নিজের রচনাকে সেরকম ভাবে খণ্ডবিখণ্ড করতে অনুমতি দেইনি । ... যে রূপসৃষ্টিতে বাহিরের লোকের হাত চালাবার পথ আছে তার এক নিয়ম, যার পথ নেই তার জন্য অন্য নিয়ম । ... আমার গানে তো আমি সেরকম ফাঁক রাখিনি যে, সেটা অপরে ভরিয়ে দেওয়াতে আমি কৃতজ্ঞ হয়ে উঠব ।
সমীর সেনগুপ্ত অবশ্য সঠিক তথ্য দিয়ে বুঝিয়ে দিয়েছেন এবং সংগত বিস্ময় প্রকাশ করে জানিয়েছেন একমাত্র পঙ্কজকুমার মল্লিককে কোনো অজ্ঞাত কারণে অন্তত তিনটি গানে স্বাধীনতা দিয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথ এবং একটি কবিতায় (`দিনের শেষে ঘুমের দেশে') সুরারোপ করে চলচ্চিত্রে গাইতে দিতে আপত্তি করেন নি । যাইহোক জীবিতকালে রবীন্দ্রনাথের গানের ধরন ও সুরের চলন সম্পর্কে অনেক বিরূপ মন্তব্য তাঁকে শুনতে হয়েছে । আপন মনের খেদ তিনি কোনো কোনো আপনজনের কাছে মাঝে মাঝে ব্যক্তও করতেন । সমীর সেনগুপ্ত তেমনই এক বয়ান ছেপেছেন সাহানা দেবীর রচনা থেকে ।`এই সময়ে তাঁর গানের বিরুদ্ধে সমালোচনায় কেউ কেউ তাঁকে আঘাত করেন তার সঙ্গীতে সুরের দীনতা দেখিয়ে । আঘাত তিনি নীরবেই গ্রহণ করতেন, ফিরে আঘাত দিতে তাঁকে দেখিনি । তাঁর অসাধারণ মার্জিত রুচিতে তা বাধত । সে সময়ে একদিন আমাকে বলেছিলেন, `পদ্মফুল আর জুঁইফুলের তুলনা চলে না । দুটো সম্পূর্ণ দুই জিনিস । পদ্মফুল বড়, জুঁইফুল ছোট । এই বড় পদ্মফুলের সৌন্দর্য বা তার সব গুণের অধিকারী না হয়েও ছোট জুঁইফুল তার আপন সুগন্ধ বুকে নিয়ে আপনার সুকুমার সৌন্দর্যে আপনি বিকশিত । আমার গানকে আমি মনে করি এই ছোট জুঁইফুল ।'
এখানে আমরা বুঝে নিতে পারি একজন যথার্থ শিল্পীর অভিমান আর প্রত্যয়কে । অবয়বে ব্যাপ্ত এবং গায়নকৌশলে কারদানিবহুল গান তিনি রচনা করতে চান নি । কিন্তু তাঁর গানের অনন্যতা বোঝাতে রবীন্দ্রনাথ জানিয়ে দিয়েছেন : `সেই সৌন্দর্য ধরা পড়ে চোখের অন্য এক দৃষ্টি নিয়ে চেতনার অন্য এক স্পর্শে ।'
সমীর সেনগুপ্ত-র বই থেকে নানা তথ্য বিচার করলে বোঝা যায় যে ঠাকুর পরিবারের প্রায় সকলেই তাঁর গানের অনন্যতা ও স্বভাবস্বাতন্ত্র্য বুঝতে পেরেছিলেন । পিতা দেবেন্দ্রনাথ, অগ্রজ জ্যোতিরিন্দ্রনাথ, ভাগিনেয়ী সরলা, ভাইঝি ইন্দিরা, পৌত্র দিনেন্দ্রনাথ ও সৌম্যেন্দ্রনাথ সকলেই ছিলেন গানের ভক্ত ও প্রচারক । তবে এঁদের পাশাপাশি গগন-সমর-অবনদের সমঝদারির কথা বড় একটা কেউ বলেন না । সমীর সেনগুপ্ত-র বই থেকে অপরূপ এক সংবাদ পাঠকদের ভালো লাগে । সময়টা হল ১৯০৪ । ঠাকুরবাড়িতে গগনেন্দ্রনাথের বড়ছেলে গেহেন্দ্রনাথের বিয়ে উপলক্ষ্যে খুব ধুমধাম জাঁকজমক হয়েছিল । গড়ের বাদ্যির তিনটি দল, ঢাকঢোল ও সানাই - সেইসঙ্গে তখনকার কলকাতার পর্তুগিজ সায়েব লোবো-র দলের ব্যাণ্ড পার্টির আয়োজন হল । অভিনবত্ব এটাই যে গগনেন্দ্রনাথ লোবো সায়েবকে ডেকে বললেন ব্যাণ্ডে রবিঠাকুরের গান বাজাতে হবে । ব্যাপারটা লোবোর দলের পক্ষে অভাবিত ও অজানা । লোবো বললেন, আমাদের গানে সবসময় নোটেশন থাকে । আমাদের বেহালাবাদক, চেলোবাদক, স্যাক্সোফোন বাদক এমনকী খরতালবাদক, ড্রামবাদক পর্যন্ত নোটেশন সামনে রেখে বাজনা বাজিয়ে যায় ।
এবারে তৈরি হল সেই নোটেশন । গগনের অনুরোধে তাঁদের রবিকাকা বানিয়ে দিলেন দুটি গানের নোটেশন । গান দুটি হল `শান্ত হ রে ওরে দীন' এবং `শান্তি করো বরিষণ' । কিন্তু শুধু নোটেশনে তো হবেনা । নানা যন্ত্রে বাজবে তাই হার্মোনাইজ করা দরকার । রবিকাকার হুকুমে সেই হার্মোনাইজের কাজটি করে দিলেন ভাইঝি ইন্দিরা । বেশ কদিন মহড়ার পরে বিয়ের দিনে যখন বিদেশি যন্ত্রে রবিঠাকুরের গান বেজে উঠল তখন প্রদ্যোত্কুমার ঠাকুর, কালীকৃষ্ণ ঠাকুর, যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর ও সৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুরের রসিক ও সম্ভ্রান্তেরা হতবাক । `সকলেই বুঝলেন এ গগনেরই কীর্তি ।' এই সমঝদারির তথ্যটুকু সুন্দর ।
মনে রাখতে হবে ১৯০৪ সালে রবীন্দ্রনাথের গান সমাজে তত প্রচলিত বা প্রচারিত ছিল না । সেই তথ্যের সঙ্গে লক্ষণীয় যে ৪৩ বছর বয়েসী রবীন্দ্রনাথ নিজে তাঁর গানের স্বরলিপি করতে আগ্রহী ছিলেন । এই প্রসঙ্গে মনে পড়ে, প্রায় পুরো সংগীতজীবনেই রবীন্দ্রনাথের নিজের গানে স্বরলিপি করার উত্সাহ ছিল না । তাই যখন যেখানে যেমন যেমন তাঁর মনে গান রচনার আহ্বান এসেছে `কথা ও সুর গলায় গলায়' রূপ নিয়েছে প্রায় তদ্দণ্ডেই কাউকে না কাউকে দিয়ে স্বরলিপি করিয়ে নিতে অভ্যস্থ ছিলেন তিনি, বিকল্প হিসাবে অন্তত কোনো একজনকে গানটি শিখিয়ে দিতেন । তাঁর নিজের হাতে করা একটিমাত্র স্বরলিপি পাওয়া গেছে । তাঁর ভাইঝি ইন্দিরার কাছে তা বহুদিন গচ্ছিত ছিল । গানটি হল `এ কি সত্য সকলি সত্য', যা পতিসর থেকে কলকাতা ফেরার পথে ট্রেনে লেখা, ২৮ সেপ্টেম্বর ১৮৯৭- এ । তাঁর বয়স তখন ৩৬ বছর । ইন্দিরা জানাচ্ছেন :
আমার বিশ্বাস, এইটিই তাঁর করা একমাত্র স্বরলিপি । ... কলকাতা বাসকালে আমরা তাঁকে কখনো স্বরলিপি করতে দেখেছি বলে তো মনে পড়ে না । শান্তিনিকেতনের অধিবাসীরাও বোধহয় এ সম্বন্ধে অনুরূপ সাক্ষ্যই দেবেন ।
এই বিশেষ স্বরলিপির কালনির্দেশ করতে পারেননি ইন্দিরা কিন্তু উল্লেখ করেছেন :আধুনিক স্বরলিপিজ্ঞগণ দেখে কৌতুক বোধ করবেন যে, কবিগুরু মামুলি আকার মাত্রিক স্বরলিপির সংকেত সম্পূর্ণ মেনে চলেন নি । সেটি তাঁর স্বভাবসিদ্ধ স্বকীয়তাবশত:, অথবা তখন আকার মাত্রিক পদ্ধতির শৈশব অবস্থা ছিল বলে, সে কথা এখন নির্ণয় করা শক্ত ।
রবীন্দ্রনাথের গানে শব্দগত পরিবর্তন বা পরিমার্জনার ব্যাপারটি বেশ কৌতূহলকর । সমীর সেনগুপ্ত এ ব্যাপারে গভীর মনস্কতার পরিচয় রেখেছেন । তাঁর গবেষণা থেকে আমরা জানতে পারি যে, `আমি সুখ বলে দুখ চেয়েছিনু' গানটি `বেশ রহস্যময়' । কারণ `এই কথাগুলি দিয়ে আরম্ভ হচ্ছে এমন একটি গান কোথাও নেই' অথচ গানটি শোনার লিখিত উল্লেখ আছে । এই সূত্রে সমীরের সিদ্ধান্ত, `একটি কীর্তনাঙ্গ গান আছে "আমি সংসারে মন দিয়েছিনু", এর দ্বিতীয় চরণ হল "আমি সুখ বলে দুখ চেয়েছিনু"। তার মানে এক্ষেত্রে দ্বিতীয় চরণ প্রথম চরণ হিসাবে এসে গেছে কারোর স্মৃতিতে ।
আর একটি লক্ষ্য করবার বিষয় এই যে, গানের কথাগুলি স্বরলিপিতে যেরূপ দেখা যায়, মুদ্রিত অবস্থায় সে রূপ কতকটা বদলে গিয়েছিল ।সমীর সেনগুপ্ত তাঁর সদাজাগ্রত তথ্যসন্ধানী চোখে `গভীর রজনী নামিল হৃদয়ে' গানটির রচনাগত বিচিত্র সৃষ্টিপ্রক্রিয়া উদ্ধৃত করেছেন অমিতাভ চৌধুরীর এক লেখা থেকে । অমিতাভ সেই তথ্য সংগ্রহ করেছেন `মজুমদার পুথি' থেকে । সেই সূত্রে দেখা যাচ্ছে ঐ গানে অনবরত কাটাকুটি করেছেন রবীন্দ্রনাথ । শেষমেষ `গভীর রজনী' অংশ যখন লিখেছেন তার আগেই গানের পরবর্তী অংশ লেখা হয়ে গিয়েছিল । সমীর সংগীতের রূপবন্ধ সচেতন বলেই মন্তব্য করতে পেরেছেন - `এইভাবে সঞ্চারী আভোগ আগে লিখে পরে আস্থায়ী অন্তরা রচনা করার দৃষ্টান্ত আর আছে কিনা জানা নেই ।' `হেরিয়া শ্যামলঘন নীল গগনে' গান প্রসঙ্গে তিনি ভারি চমত্কার এক দ্যোতক মন্তব্য করেছেন । এই গানটিতে শব্দ পরিবর্তন ও কাটাকুটির বহুতর উদাহরণ উদ্ধৃত করে সমীর বলছেন : `কথার বদলের মতো সুরের বদলও বহুবার হয়েছে নিশ্চয়ই, তার কিছু কিছু আভাস আমরা এই সব কাহিনীর কোনো কোনোটির মধ্যে পাই । কিন্তু সুর দেবার সময় যে কাটাকুটি রবীন্দ্রনাথ করতেন সেগুলি পাবার কোনো উপায় নেই ।'

॥ ৩ ॥
রবীন্দ্রনাথ তাঁর গানে কীভাবে সুরপ্রয়োগ করতেন, তার মধ্যে কাটাকুটি বা বদল হয়ে অবশেষে আমাদের চেনা সুরটি কেমন করে স্থায়ীরূপ পেত সেকথা তিনি জানাননি, কেউ তা লেখেনও নি । আরেকটা প্রশ্ন অনেকের মনে জাগে যে, যখন একেবারে একা তিনি দেশে বা বিদেশে গান তৈরি করেছেন তখন তার স্বরলিপি কে করে রাখত ? জবাব পাওয়া যায় না । এ প্রশ্নের পিঠোপিঠি উঠে আসে আরেক প্রশ্ন যে, সত্যিই কি তিনি নিজের করা সুর নিজেই মনে রাখতে পারতেন না ? সমীর সেনগুপ্ত-র বই থেকে এই দ্বিতীয় প্রশ্নটির যে সব জবাব পাই তা পরস্পর বিরোধী । আগেই আমরা উল্লেখ করেছি ১৮৮৬ সালে লেখা গান `অন্ধজনে দেহো আলো' ১৯২২ সালে একা একা বারবার গাইছেন রবীন্দ্রনাথ নিশীথ অন্ধকারে, আত্মবেদনা অপনোদনের জন্য । দেখা যাচ্ছে গানটির সুর তাঁর অতদিন পরেও বেশ মনে ছিল । ১৯০৯ সালে রচিত `ঐ আসনতলে মাটির পরে' গানটি রবীন্দ্রনাথের পঞ্চাশতম জন্মদিনে (১৯১১) শান্তিনিকেতনে নিজে গাইলেন এমন বর্ণনা সমীর উদ্ধৃত করেছেন সীতাদেবীর স্মৃতি থেকে । ঐ একই গান ১৯১৪ সালে গয়ায় জনৈক বাঙালি জজ সায়েবের অনুরোধে তিনি টেবিল হারমনিয়াম যোগে গেয়েছেন । এই জাতীয় দুটি তথ্য পরিবেশন করে সমীর খুব সংগত ভাবে মন্তব্য করেছেন :
রবীন্দ্রনাথ নানা স্থানে বলেছেন এবং লিখেছেন, তিনি নিজের সুর মনে করে রাখতে পারেন না, সুর দিয়ে কাউকে শিখিয়ে না দিলে ভুলে যান কিন্তু নানাজনের স্মৃতিকথায় আমরা বারংবার দেখতে পাই, রচনা ও সুর দেবার বহুবছর পরে তিনি অনুরুদ্ধ হয়ে গান গেয়ে শোনাচ্ছেন যেমন এই গানটি (ঐ আসনতলে) গাওয়ার দ্বিতীয় ঘটনাটি ঘটেছিল গানটি রচনার পাঁচ বছর পরে - এর চেয়ে অনেক বেশি বছরের ব্যবধানেও তিনি স্বরচিত গান গেয়ে শুনিয়েছেন, এমন দৃষ্টান্ত অজস্র পাওয়া যাবে । সুতরাং `মনে রাখতে না-পারা' বলতে তিনি ঠিক কী বলতে চেয়েছেন সেটা আমাদের স্পষ্ট করে বোঝবার চেষ্টা করা দরকার ।
অবশ্য সুর ভুলে যাবার ঘটনা এবং সদ্য সদ্য সুর দিয়ে মুখরক্ষার বৃত্তান্তও আমরা পেতে পারি এবং তা `গানের পিছনে রবীন্দ্রনাথ' বই থেকে । যেমন ধরা যাক, `জীবন যখন শুকায়ে যায়' গানটির প্রসঙ্গ । এর রচনাকাল ১১ এপ্রিল ১৯১০ শান্তিনিকেতনে । ১৯১১ সালে মাঘোত্সবে জোড়াসাঁকো বাড়িতে আচার্যের কাজ করছিলেন রবীন্দ্রনাথ । সীতা দেবীর `পুণ্যস্মৃতি' বই থেকে দেখা যাচ্ছে :
উপদেশের পর দু'লাইন গান গাহিয়া রবীন্দ্রনাথ শেষ করিলেন । গানগুলি যদিও অনেক নামকরা ওস্তাদরা গাহিলেন, তবু শুনিতে কিছু ভালো লাগিল না । রবীন্দ্রনাথ পিছনে ফিরিয়া অনেকবার গানের সুর ও তাল সংশোধন করিয়া দিলেন, তাহাতেও সুবিধা হয় না দেখিয়া নিজেই গায়কদের সঙ্গে গান ধরিয়া দিলেন । "জীবন যখন শুকায়ে যায় করুণাধারায় এসো" এই গানটি প্রথম শুনিলাম সেইদিন ।
এমন যে পার্টিসিপেটারি গায়ন ও সম্পৃক্ত গান তার সুর পরে কিন্তু স্রষ্টার মনে ছিল না । তার উদাহরণ হল অন্য এক ঘটনা । ১৯১১ সালের অনেক বছর পরে ১৯৩২ সালে ২০ সেপ্টেম্বর থেকে মহাত্মা গান্ধী অনশন করেছিলেন রাজশক্তির বিরুদ্ধে । ২৬ সেপ্টেম্বর গান্ধী অনশন ভঙ্গ করেন রবীন্দ্রনাথের কন্ঠে এই গানটি শুনতে শুনতে । রবীন্দ্রনাথ নিজেই লিখে গেছেন :
... প্রায়োপবেশনের ব্রত উদ্যাপন হল । ... মহাদেব [দেশাই] বললেন, "জীবন যখন শুকায়ে যায়" গীতাঞ্জলির এই গানটি মহাত্মাজির প্রিয় । সুর ভুলে গিয়েছিলেম । তখনকার মতো সুর দিয়ে গাইতে হল । ...
সুর ভুলে যাবার ব্যাপারে এর পরের উদাহরণটিও বেশ ঐতিহাসিক । ১৯২৩ সালে ১০ সেপ্টেম্বরে প্রয়াত হন সুকুমার রায় (তাতা) মাত্র ৩৬ বছর বয়সে । রবীন্দ্রভক্ত এই প্রতিভাবানের আসন্ন মৃত্যুর আগে তাঁর শয্যার পাশে গিয়ে দাঁড়ান রবীন্দ্রনাথ । তাতা-র অনুরোধে রবীন্দ্রনাথ তাঁকে গেয়ে শোনান `আছে দু:খ আছে মৃত্যু' (রচনা ১৯০৩) গানটি - বিশ বছরের ব্যবধানে সুর ভুলে যান নি তিনি । এর পরের গানটি নিয়ে হল বিপত্তি । শোনা যাক প্রত্যক্ষদর্শী সুশোভন সরকারের জবানীতে :
ঘটনাচক্রে আমরা কয়েকজন তখন উপস্থিত ছিলাম । তাতাদা রবীন্দ্রনাথকে অনুরোধ করলেন তাঁকে একটা গান শোনাতে । গানটাও নির্দেশ করে দিলেন । গীতালি-র `দু:খ এ নয়, সুখ নহে গো, গভীর শান্তি এ যে' । বেশ মনে পড়ে রবীন্দ্রনাথ খানিকক্ষণ চুপ করে রইলেন । তারপর গানটা শোনালেন । পরে জানলাম যে ওই কবিতাটির নাকি তখন সুর দেওয়া ছিল না, রবীন্দ্রনাথ সেখানে বসেই সুর দিয়ে ছিলেন । সেখানে সঙ্গে সঙ্গে তুলে নেবার মতো কেউ ছিলেন না বলেই সম্ভবত সুরটি লুপ্ত হয়ে গেছে ।
সমীর সেনগুপ্ত এই খবর জানিয়েছেন কিন্তু ঘটনার তারিখটি জানান নি । তবে জানিয়েছেন `দু:খ এ নয়, সুখ নহে গো' গানটির রচনাকাল ১৬ আশ্বিন ১৩২১ । কিন্তু প্রশ্ন হল গীতালি-র অন্তর্গত এই রচনায় কি সুর দেওয়া কোনো গীতিরূপ ছিল না ? তাহলে সুকুমার তা শুনতে চাইলেন কেন ?
আমরা অনুসন্ধান করে অন্য কিছু তথ্য পেয়েছি, যা প্রসঙ্গত উল্লেখ করা উচিত । দেখা যাচ্ছে তাঁর প্রিয় অনুরাগী তাতাকে দেখতে বা গান শোনাতে রবীন্দ্রনাথ আগেও এসেছেন । সুকুমার রায়ের ভাই হিতেন্দ্রকিশোর রায় লিখেছেন ১৬ মার্চ ১৯২৩ সালের এক বিবরণ যেখানে জানা যাচ্ছে রবীন্দ্রনাথ তাতাকে শোনাচ্ছেন একদিন সন্ধ্যাবেলায় `আমার সকল দুখের প্রদীপ জ্বেলে' গানটি । এর পাশাপাশি পাওয়া যায় আরেকটু বিস্তারিত বর্ণনা সুকুমার রায়ের খুড়তুতো বোন মাধুরীলতা রায়ের লেখা থেকে । তাতে আছে :
২৯ আগস্ট ১৯২৩ । অবস্থা ত্রক্রমশ খারাপ হইতে লাগিল । সেদিন রবিবাবু দাদাকে দেখিতে আসিয়াছিলেন । দাদা তাঁহাকে দেখিয়া অত্যন্ত আনন্দিত হইলেন এবং পরে তাঁহার গান শুনিতে চাহিলেন । রবিবাবু দাদার পার্শ্বে বসিয়া দাদা যে সকল গান শুনিতে চাহিলেন, সেই সকল গান গাহিতে লাগিলেন । গানের পর গান চলিল । সকলে তন্ময় হইয়া গান শুনিতে লাগিল । তখন দাদার প্রশান্ত মুখখানি দেখিয়া মনে হইতেছিল যে তিনি পরম শান্তি লাভ করিয়াছেন । একটি বিশেষ গান সকলকে অত্যন্ত বিস্মিত করিয়াছিল । সেটি এই : `দু:খ এ নয়, সুখ নহে গো, গভীর শান্তি এ যে' ।
দুটি তথ্যসূত্রই পাওয়া যাচ্ছে বিষ্ণু বসু সম্পাদিত `সুকুমার রায় শিল্প ও সাহিত্য' বইতে । এ সব তথ্য যেন আমাদের বিস্মিত চেতনার কাছে বার্তা আনে যে কবির মনে স্মৃতি-বিস্মৃতির কত বিচিত্র তরঙ্গ বয়ে আসত । তিনি নিজে মাঝে মাঝে শান্তিদেব বা শৈলজারঞ্জনের কাছে নিজের গান শুনতে চাইতেন । কী গান বা কোন্ গান জানতে চাইলে বলতেন নতুন গান । তাঁকে গাইতে বললে সর্বদাই গাইতেন প্রথম জীবনের বা পুরোনো গান । ঐ সব গানের কথা ও সুর নাকি তাঁর আত্মস্থ হয়ে ছিল এবং নতুন গানগুলি সুরসমেত তাঁর মনে থাকত না । হবেও বা ।
তবে সমীর সেনগুপ্ত পরিবেশিত সংবাদ থেকে জানা যাচ্ছে একটি বিশেষ গান সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের বিশেষ নির্দেশ ছিল সেটা যেন তাঁর মৃত্যু পরবর্তী সময়ে গাওয়া হয়, গানটি যেন কাউকে শেখানোও না হয় । গানটি : `সমুখে শান্তি পারাবার / ভাসাও তরণী হে কর্ণধার' । তাঁর মৃত্যু ঘটে ১৯৪১ সালের আগস্টে আর এ গানটি লেখেন ১৯৩৯ সালের ৩ ডিসেম্বরে । লেখার প্রত্যক্ষ প্রয়োজন ছিল `ডাকঘর' নাটকের গানটি ব্যবহার করার । নাটকের মহড়া হয় কিন্তু শেষপর্যন্ত অভিনয় হয় না । ঐ নাটকে অমলের মৃত্যুর পরে তার শিয়রে ঠাকুর্দার গাইবার কথা ছিল । গানটি যখন শেষপর্যন্ত কাজে লাগল না তখন স্রষ্টা এটিকে তাঁর দেহান্ত পরবর্তী গান হিসাবে গাইবার ইচ্ছা প্রকাশ ও বিনতি জানিয়েছিলেন । এই ইচ্ছার একাধিক তথ্য আছে ।
(১) প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের বয়ানে : `শুনা যায় কবি অভিপ্রায় প্রকাশ করেন যে, গানটি তাঁহার দেহত্যাগের পূর্বে যেন প্রচারিত না হয় তাঁহার শ্রাদ্ধবাসরে ইহা প্রথম সাধারণ সমক্ষে গীত হয় ।'
(২) রথীন্দ্রনাথ ঠাকুর আরেকটু বাড়তি তথ্য জুগিয়ে লেখেন : `গানটি তাঁহার দেহান্তের পর গীত হয়, পূজনীয় পিতৃদেব এইরূপ অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়াছিলেন । তদনুসারে ইহা তাঁহার পরলোক যাত্রার পর (২২শে শ্রাবণ ১৩৪৮) সন্ধ্যায় শান্তিনিকেতন মন্দিরে ও ৩২শে শ্রাবণ শ্রাদ্ধবাসরে শান্তিনিকেতনে গীত হয় ।'
(৩) শান্তিদেব ঘোষের ভাষ্য : `১৩৪৬ সালে তিনি একবার তিন-চার মাস ধরে এই নাটকের মহড়া দিয়েছিলেন, সেই সময় অধুনা বিখ্যাত `সমুখে শান্তিপারাবার' গানটি রচিত হয় । সেই সময় একদিন বলেছিলেন যে, তাঁর মৃত্যুর তো আর বেশি দেরি নেই, এটি যদিও অমলের মৃত্যুর গান কিন্তু এ গানটি তাঁর মৃত্যুতেও আমরা কাজে লাগাতে পারব ।'
(৪) গানটি সম্পর্কে সবচেয়ে পূর্ণাঙ্গ ও প্রত্যক্ষ তথ্য জানা যায় শৈলজারঞ্জন মজুমদারের লেখা বই `যাত্রাপথের আনন্দগান' থেকে । তাঁর স্মৃতিচারণে পাই : `গানটি গুরুদেব নিজে মহড়ার সময় ঠাকুরদার ভূমিকায় অমলের অন্তিমশয্যায় তার শিয়রে বসে গেয়ে শোনাতেন । ... "সমুখে শান্তিপারাবার" এই গানটি রচনা করে গুরুদেব আমাকে দুপুর একটার সময় ডেকে পাঠিয়েছিলেন । সাধারণত এরকম সময় গান শেখাবার জন্য কখনও ডাকতেন না । আমি গানটি যথারীতি গলায় তুলে নিয়ে যখন স্বরলিপি করে নিয়ে চলে আসছি, তখন পিছন থেকে ডেকে গুরুদেব ধ্যানগম্ভীর দৃষ্টিতে তাকিয়ে বললেন - আজ আমি যা প্রত্যক্ষ করলাম তাই এখানে লিখে রেখে গেলাম, কিন্তু এ গানটি আমার অন্যান্য গানের মত তুমি কাউকে শিখিও না । আমার যখন হয়ে বয়ে যাবে তখন এ গানটি করে দিও । কিন্তু তখন তুমি আমাকে কাছে পাবে না । অন্য গানের মত এ গানটি তুমি আর কাউকে আগে শিখিও না । ... গানটি তারপর আমি চাপা দিয়ে গোপনে রেখে দিয়েছিলাম । প্রথমবার করলাম গুরুদেবের মৃত্যুসংবাদ পেয়ে । সেদিন মন্দিরে যে উপাসনা হয়েছিল তাতে এই গানটি চোখের জলে সমবেত কন্ঠে করা হয় । সে গানের দলে ছিলেন ইন্দুলেখা ঘোষ, অমলা বসু, কণিকা বন্দ্যোপাধ্যায় আর আমি ।'
আসন্ন মৃত্যু অনুভবের সংবেদে ভরা এমন এক অনাঘ্রাত গান প্রথম পরিবেশিত হল শান্তিনিকেতনের উপাসনা ঘরে এবং তার দশদিন পরে সেখানকার শ্রাদ্ধবাসরে । কিন্তু শান্তিনিকেতন পরিসরের বাইরে বৃহৎ যে বঙ্গীয় রবীন্দ্রভক্তমণ্ডলী তথা তাঁর গীতানুরাগী তাঁদের যে গানটি শোনানো গেল না । সম্ভবত এমনতর আক্ষেপ থেকে শৈলজারঞ্জন প্রস্তাব দিলেন কটি গ্রামাফোন কোম্পানিকে এই বিশেষ তাত্পর্যপূর্ণ গানটি রেকর্ড করতে । তাঁর প্রস্তাবমত এইচ. এম. ভি-তে গানটি রেকর্ড করেন কনক দাস । পায়োনিয়ার রেকর্ডস্য়ে গানটি করেন শৈল দেবী । দুক্ষেত্রেই অনাদিকুমার দস্তিদারের পরিচালনায় রেকর্ড হয় । আর শৈলজারঞ্জনের পরিচালনায় হিন্দুস্থান মিউজিক্যাল প্রোডাক্টস্ থেকে করেন অমিয়া ঠাকুর । লক্ষণীয় যে, তিনটি রেকর্ডই হয় নারীকন্ঠে । ১৯৪১ সালে বাংলায় নির্ভরযোগ্য পুরুষকন্ঠ পান নি অনাদিকুমার ও শৈলজারঞ্জন কিন্তু পেয়ে গিয়েছিলেন তিনটি নিবেদিত নারীর অশ্রুময় কন্ঠ । মৃত্যুসংবাদ শান্তিনিকেতনে পৌঁছবার পর সেই সন্ধ্যার উপাসনায় যখন প্রথম গাওয়া হল সমুখে শান্তিপারাবারের মতো তখনও পর্যন্ত অ-গীত রবীন্দ্রসংগীত তখন শৈলজারঞ্জনের সঙ্গে সমস্বরে গেয়েছিলেন তিন নারী - ইন্দুলেখা, অমলা ও সতেরো বছরের `মোহর' ।

॥ ৪ ॥
প্রতিটি তথ্যেরই একটি বিশেষ তাত্পর্য আছে, সেটি গান শোনার সময় আমাদের কাজে লাগে, আমাদের শোনার অভিজ্ঞতাকে ঋদ্ধতর করে তোলে । ... তাঁর সমস্ত গান রচনার পিছনে একটি অপার্থিব প্রতীতির চাপ আমরা অনুভব করি, মানুষটিকে প্রায় অচেনা বলে মনে হয় । ... একটু যেন ভয় ভয়ও করতে থাকে, এই মানুষটির উত্তরাধিকারের একটি অর্বুদতম ভগ্নাংশও বাঙালি হিসেবে আমার ভিতরে বাহিত হয়ে এসেছে বলে - আমাকে নতুন করে ভাবতে হয়, আমি কি এই উত্তরাধিকারের যোগ্য ?
প্রায় দু'হাজারের কাছাকাছি সংখ্যার গান লিখেছেন যিনি তার এক ভগ্নাংশ অর্থাৎ মাত্র তিনশোর কাছাকাছি গানের অন্তরমহল আলোকিত করে সমীর যে রবীন্দ্রপ্রকোষ্ঠগুলি উন্মোচন করেছেন তা লক্ষ করতে গিয়ে আমার মনে একটা খেদ জেগে উঠল । মনে পড়ল সন্ত কবীর, সুরদাস, মীরাবাই, তুকারাম বা শঙ্করদেব শুধু নয়, মধ্যযুগের বহু গীতিকারের গান পুঁথিতে বাঁধা অবস্থায় পাওয়া যায়নি, তার কারণ সে সব ছিল বাচনিক রচনা - ভক্ত পরম্পরায় কন্ঠ থেকে কন্ঠে কোন্ যুগ থেকে কোন্ যুগে, সিন্ধুপারে, কোন্ বনে, লোকালয়ে তার মাধুরীবর্ষণ ঘটেছে, কিন্তু কেউ কোনোদিন জানতে পারেনি তার অন্তরমহলের হদিশ, সৃজনবেদনা বা আনন্দ উত্স । খুব মন খারাপ হয়, যখন ভাবি, রামপ্রসাদের অমলিন গানের স্বর্ণশস্য শুধু গায়ন পরম্পরায় বেঁচে আছে এতদিন, তার রচনা পরম্পরা বা তার সৃজনের অন্তরালে আমগ্ন ভক্তহৃদয়ের কোনো স্বরলিপি তো নেই । তাঁর গান তাঁর আত্মবিকাশের ত্রক্রমোত্তরণের স্তরগুলি ধরে রেখেছে কিন্তু রচনাক্রম জানিনা বলে আমরা ধরতে পারি না তার প্রাগ্রসর সূত্র - সেসব গানের উত্স, বন্দেশ বা উপলক্ষ্য খোঁজা তো আজ অলীক স্বপ্ন । অতদূরে কেন ? ১৮৯০ সালে দেহাবসান ঘটেছে লালন শাহ ফকিরের । লোকায়ত জীবনে প্রত্যন্ত গ্রামে বসবাসকারী এই গীতিকার তাঁর অবতলের কঠিন আবরণ ভেদ করে এই তো সবে ধরা দিয়েছেন আমাদের শিষ্ট সমাজের মুদ্রণ মাধ্যমে । পাওয়া গেছে লালনের গানের খাতা (অবশ্য শিষ্যদের হস্তাক্ষরে) এবং গায়নরীতির ধাঁচা - আখড়াজীবীদের কন্ঠস্বরে । কিন্তু তাঁর গান রচনার উত্স বা স্থানকাল, প্রচার ও প্রতিক্রিয়ার খবর কই তেমন তো মেলে না ।সেদিক থেকে রবীন্দ্রনাথ ভাগ্যবান যে তাঁকে ঘিরে আজীবন ছিল নির্ভরযোগ্য বহু ভক্তের বা অনুরাগীর বৃত্ত । তাঁদের একেবারে ঘিরে থাকা কাছাকাছি সান্নিধ্যে রবীন্দ্রসংগীতের প্রস্ফুটন যেন কোনো অলৌকিক ফসলের মতো, যে সোনারতরীতে স্রষ্টার সঙ্গে শ্রোতা ও ভোক্তা একই সিদ্ধির সমুদ্রে পাড়ি দিতে পেরেছে । সেখানে সকলের ঠাঁই হয়েছে - `ছোট এ তরী' বলে কাউকে পারে রেখে যাওয়া হয়নি । সেইসব বিরল সৌভাগ্যের সহযাত্রীদের রচনা ও জানানো তথ্যের বিন্যাসে সমীর সেনগুপ্ত ভরে দিয়েছেন উত্তরপুরুষদের সঞ্চয় । বোঝা গেছে একমাত্র গানের স্বত:স্ফূর্ততায় রবীন্দ্রনাথ সবচেয়ে অনলংকৃত আর অনর্গলিত । অন্য সূত্রে পড়েছি, আশ্রমিক ক্ষিতিমোহন সেন একবার গায়ক অশোকতরু বন্দ্যোপাধ্যায়কে বলেছিলেন :
তোমরা গায়করাই চেষ্টা করলে রবীন্দ্রনাথের যথার্থ পরিচয় পেতে পারো । তাঁর কাব্যই বলো আর নাটকই বলো, বা অন্য যে কোনো গদ্যরচনাই বলো, সবকিছুর মধ্যে দিয়েই ক্ষণে ক্ষণে হয়তো দেখবে তাঁর সেই দাড়ি জোব্বা উঁকি মারছে । তিনি যে রবীন্দ্রনাথ এ কথা তিনি ভুলতে পারতেন না । কিন্তু তাঁর গান রচনার সময়, আমি কাছ থেকে দেখেছি - তাঁর আত্ম সচেতনতা সম্পূর্ণ বিলুপ্ত হতো, তখনি দেখতে পেতাম সত্যিকারের রবীন্দ্রনাথকে - যেন একেবারে খোলস ছাড়ানো ন্যাংটো মানুষ ।
এই মন্তব্যটি হয়তো সমীর সেনগুপ্ত-র চোখে পড়েনি তবে তাঁর বই-তে গানের মধ্যে আত্মহারা বা গান গাইতে আত্মস্থ রবীন্দ্রনাথের অনেক বিগ্রহ তিনি উপহার দিয়েছেন পাঠকদের । যেমন ধরা যাক নন্দলাল বসুর স্ত্রী সুধীরা বসুর স্মৃতি থেকে জানাচ্ছেন :এক জ্যোত্স্নারাতে ছাত্ররা গুরুদেবের নূতন লেখা `চাঁদের হাসির বাঁধ ভেঙেছে' গাইতে গাইতে নেপাল রোড দিয়ে চলেছে কোথাও সুরে একটু ভুল হয়েছে বা গোলমাল হয়েছে, রবীন্দ্রনাথ দেহলির উপর থেকে মুক্তকন্ঠে শুরু করলেন ঐ গানটি । সমস্ত আশ্রমে সে সুর ছড়িয়ে পড়ল গমগম করে । শান্তিনিকেতনের সমস্ত আকাশবাতাস যেন গেয়ে উঠল সে সুরে সুর মিলিয়ে । যে যেখানে ছিল স্থানুর মতো নিশ্চল হয়ে দাঁড়িয়ে রইল । একটি মানুষের কন্ঠস্বরে ভরে গেল সমস্ত আশ্রম ।... ভাগ্যে ছেলেরা একটু ভুল করে ফেলেছিল, তাইতো এ জ্যোত্স্নারাতে গুরুদেবের অপূর্ব কন্ঠস্বর শোনার সৌভাগ্য হল ।
এই বর্ণনায় একই সঙ্গে সে সময়ের শান্ত নিশুতি শান্তিনিকেতন, জ্যোত্স্নারাতের আলো, আত্মবিহ্বল গায়ক রবীন্দ্রনাথের পরিকীর্ণ কন্ঠধ্বনি আর উন্মুখ শ্রোতার দীপনা ফুটে উঠেছে । একাকী গায়কের নহে তো গান ।এই ধরনের টুকরো টুকরো নানা বৃত্তান্ত পড়তে পড়তে, জানতে জানতে, এগিয়ে চলে আমাদের গানের রবীন্দ্রনাথকে খুঁজে নেওয়া । যে-পুরুষটি অন্ধকার আর্ত আকাশের দিকে চেয়ে চেয়ে একলা গান করে চলেন, দুর্গম পথের ক্লান্তি আর দু:সহ গ্রীষ্মের তাপকে সুসহ করে নিতে পারেন গান লিখে লিখে, প্রচণ্ড ঝড়ে উন্মথিত প্রাকৃতিকতার মধ্যে দেখতে পান রুদ্রবেশে সুন্দরের আবির্ভাবকে । প্রথাবিরোধী এই স্রষ্টা রবীন্দ্রনাথ আর তাঁর সৃষ্টির বিচিত্র পথে আমাদের পদচারণা করার সুযোগ করে দিয়েছেন সমীর সেনগুপ্ত, তারজন্যে পাঠক ও শ্রোতা দু'তরফেরই কৃতজ্ঞতা তাঁর প্রাপ্য । ভেঙে দিয়েছেন তিনি আমাদের অনেক ভুল ধারণা । যেমন ধরা যাক যদুভট্টের প্রসঙ্গ । বহু মানুষের এমন বিশ্বাস যে, রবীন্দ্রনাথের গানের জীবন গড়ে ওঠার নেপথ্যে যদুভট্টের শিক্ষণ তথা গায়ন খুব বড় ভূমিকা নিয়েছে । এ ব্যাপারে জানতে পারছি :
প্রশান্তকুমার পাল ঠাকুরবাড়ির হিসেবের খাতা থেকে প্রমাণ উদ্ধার করে দেখিয়ে দিয়েছেন (রবিজীবনী ১, পৃ. ২১৬) ১২৮২ বঙ্গাব্দের জ্যৈষ্ঠ থেকে ভাদ্র অর্থাৎ মাস চারেকের বেশি যদুভট্ট ঠাকুরবাড়িতে ছিলেন বলে মনে করা মুশকিল । মদ্যপান করে দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের বয়স্য শ্রীকন্ঠ সিংহের সঙ্গে দুর্ব্যবহার করার অপরাধে তাঁকে ঠাকুর বাড়ি থেকে বিদায় করে দেওয়া হয় ।
এর বাইরে আরও যা জানতে পারি আমরা তা হল কোন্ বিরুদ্ধ পরিবেশে কি ধরনের চাঞ্চল্যের মধ্যেও রবীন্দ্রনাথ গান লিখতে পারতেন । যেমন তার একটা নমুনা দেখছি `যদি বারণ কর তবে গাহিব না' গান প্রসঙ্গে । ১৮৯৭ সালের ২৪ সেপ্টেম্বর কবি যাচ্ছিলেন চলনবিলের ওপর দিয়ে বোটে চেপে । চারদিকে উদ্দাম ঝড় উত্তাল জলস্রোত, কিন্তু তার মধ্যে তিনি রচনা করলেন `যদি বারণ কর তবে গাহিব না' । গানের পাণ্ডুলিপিতে লেখা ছিল `চলনবিল । দিনে দু'তিন বার করে ঝড় হচ্ছে । বোট টলমল ।' কিন্তু গানের বাণী সুর বা আড়িছন্দের তালে কোনোরকম বর্ষার অনুষঙ্গ নেই । তার মানে বুঝে নিতে হবে এই তত্ত্ব যে অসামান্য সংগীত রচয়িতার অন্তরলোক কোনো ভাবেই বহির্লোকের চাঞ্চল্যের স্পর্শ পেতনা - এতটাই মগ্নতা ।এত মগ্নতা এমন আত্মনিবিষ্ট গান রচনার সবচেয়ে রোমাঞ্চকর বিবরণ রয়েছে `তোমার ভুবনজোড়া আসনখানি' গানটির প্রসঙ্গে । লেখক জানাচ্ছেন :
১৯১৬ সালে রবীন্দ্রনাথ জাপানি জাহাজ তোসামারু-তে করে জাপানের পথে আমেরিকা যাত্রা করেন, সঙ্গে ছিলেন অ্যান্ড্রুজ, পিয়ার্সন ও তরুণ ছাত্র মুকুল দে । সিঙ্গাপুর ছেড়ে হংকং যাবার পথে চীন সাগরে জাহাজ প্রকাণ্ড ঝড়ের মধ্যে পড়েছিল একদিন রাত্রে ।
ব্যাপারটির ব্যাখ্যা করে সমীর বোঝান :
যখন আমরা জানতে পারি, চীন সমুদ্রে মধ্যরাত্রের ভয়ংকর টাইফুনে টলোমলো জাহাজে, যখন ক্যাপ্টেন থেকে আরম্ভ করে সমস্ত নাবিক দাঁতে দাঁত চেপে মরিয়া হয়ে বিপর্যয় ঠেকাচ্ছে, সেই মুহূর্তে একজন কবি, তাঁর বয়স ছাপ্পান্ন, সেই মহাদুর্যোগ দেখতে দেখতে জাহাজের ডেকে দাঁড়িয়ে কথা ও সুর একসঙ্গে রচনা করে গাইছেন, "তোমার ভুবনজোড়া আসনখানি - আমার হৃদয়মাঝে বিছাও আনি -" তখন, গানটি আগে শতবার শোনা থাকলেও, আমাদের বুকের মধ্যে দুরুদুরু করে ওঠে ।...কোনো মরমানুষের পক্ষে ওই মুহূর্তে ওই জায়গায় দাঁড়িয়ে ওই গানটি রচনা করতে পারা যে সম্ভব, তা আমরা এই কাহিনীটি শোনবার আগে পর্যন্ত কল্পনা করিনি ।
আসলে অক্ষুব্ধ প্রশান্ত হৃদয়ের স্রষ্টা রবীন্দ্রনাথের কথা আমরা কতভাবেই তো জেনেছি কিন্তু তাঁর সারস্বত সাধনার বহুমুখী ও শাখায়িত বিস্তারের মাঝখানে কোথায় যে কেমন করে লুকিয়ে থাকত গীতময় এক স্বপ্নের ভ্রমর যা কেবল সৃষ্টির শতদল দলে পরিব্রাজন করত তার রহস্য আমরা এখনও পুরোপুরি জানিনি । ১৯১৪ সালের ১২ অক্টোবর গয়ায় গিয়েছিলেন তিনি । কোনো কিছুর ব্যবস্থাপনা ছিল না । প্রত্যক্ষদর্শী লিখছেন :কবির সমস্ত দিন স্নান হয়নি, রৌদ্রে পথে যাতায়াতে ও বিরক্তিতে তাঁর চেহারা অত্যন্ত ম্লান ও গম্ভীর হয়ে উঠেছে । তিনি স্টেশনের একধার থেকে আর একধার পর্যন্ত প্লাটফর্মের উপর পায়চারি করে বেড়াতে লাগলেন । ... আমাকে নিকটে দেখে বললেন - জীবনে দু:খ পাওয়ার দরকার আছে ।
ঐ ক্লান্ত কাতর বিরক্ত কবি কিন্তু তিনখানি গান লিখেছিলেন । একটি ওয়েটিংরুমে বসে, অন্যটি পালকিতে চড়ে, শেষেরটি ট্রেন থেকে নেমে ফেরার পথে । গানগুলি : `পান্থ তুমি পান্থজনের সখা হে' , `সুখের মাঝে তোমায় দেখেছি' , ও `ওগো পথের সাথি, নমি বারম্বার' । এসব জানতে পেরে কী আর ভাবব আমরা ! শুনতে শুনতে মনে হবে এসব গানে কোনো ক্ষণকালের ছন্দ নেই, আছে বিশ্বজীবনের চিরচিহ্ন - যা প্রবহমান ও গতিরাগে স্বচ্ছ । জীবন এগিয়ে যাবে, শ্রোতা বদলাবে । আমাদের গানে আমরা ধরতে চাইব আমাদের অস্থির অগভীর দিকচিহ্নহীন কম্পিত নাগরিক জীবনকে । গানের তালে নৃত্যবিক্ষেপে উদ্দাম হয়ে উঠবে মর্ত্যলালসা । কিন্তু তখনও মনে থাকবে কেবল গানের পরে গান গেঁথে রবীন্দ্রনাথ রেখে গেছেন নানা রবীন্দ্রনাথের একখানা মালা ।
পরবাস, ২২-শে শ্রাবণ, ২০০৯
অলঙ্করণ: নীলাঞ্জনা বসু - এই লেখাটি পুরোনো ফরম্যাটে দেখুন
- মন্তব্য জমা দিন / Make a comment
- মন্তব্য পড়ুন / Read comments
- কীভাবে লেখা পাঠাবেন তা জানতে এখানে ক্লিক করুন | "পরবাস"-এ প্রকাশিত রচনার দায়িত্ব সংশ্লিষ্ট রচনাকারের/রচনাকারদের। "পরবাস"-এ বেরোনো কোনো লেখার মধ্যে দিয়ে যে মত প্রকাশ করা হয়েছে তা লেখকের/লেখকদের নিজস্ব। তজ্জনিত কোন ক্ষয়ক্ষতির জন্য "পরবাস"-এর প্রকাশক ও সম্পাদকরা দায়ী নন। | Email: parabaas@parabaas.com | Sign up for Parabaas updates | © 1997-2025 Parabaas Inc. All rights reserved. | About Us