-
পরবাস
বাংলা ভাষা, সাহিত্য ও সংস্কৃতি
Parabaas, a Bengali webzine since 1997 ... ISSN 1563-8685 -
ছোটদের পরবাস
Satyajit Ray
Rabindranath Tagore
Buddhadeva Bose
Jibanananda Das
Shakti Chattopadhyay
সাক্ষাৎকার -
English
Written in English
Book Reviews
Memoirs
Essays
Translated into English
Stories
Poems
Essays
Memoirs
Novels
Plays
-

পুত্রবধূর চোখে গৌরী আইয়ুব এবং প্রসঙ্গত
-

বিশ্বের ইতিহাসে হুগলি নদী
-

বেদখল ও অন্যান্য গল্প
-

Audiobook
Looking For An Address
Nabaneeta Dev Sen
Available on Amazon, Spotify, Google Play, Apple Books and other platforms.
-

পরবাস গল্প সংকলন-
নির্বাচন ও সম্পাদনা:
সিদ্ধার্থ মুখোপাধ্যায়)
-

Parabaas : পরবাস : বাংলা ভাষা, সাহিত্য ও সংস্কৃতি -
পরবাস | সংখ্যা ৯৯ | জুলাই ২০২৫ | গ্রন্থ-সমালোচনা
Share -
এ পরবাসে রবে কে হায়! : গোপা দত্তভৌমিক
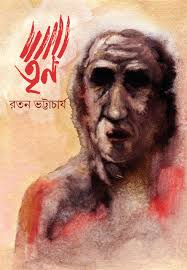 তৃণ — রতন ভট্টাচার্য; প্রচ্ছদ—ভাস্কর হাজারিকা; প্রকাশক- লিরিকাল বুকস্, কলকাতা; প্রথম প্রকাশ- জানুয়ারি ২০২২; ISBN: 978-93-87577-24-4
তৃণ — রতন ভট্টাচার্য; প্রচ্ছদ—ভাস্কর হাজারিকা; প্রকাশক- লিরিকাল বুকস্, কলকাতা; প্রথম প্রকাশ- জানুয়ারি ২০২২; ISBN: 978-93-87577-24-4
উনিশশো সাতচল্লিশে অখণ্ড ভারত ভেঙে দুটি রাষ্ট্র জন্মলাভের ইতিহাস অনেক রক্ত আর অশ্রুমাখা। স্বাধীনতার জন্য সংগ্রাম ছাড়াও হিন্দু ও মুসলমান – দুই সম্প্রদায়ের নারকীয় দাঙ্গায় এই ইতিহাস কলঙ্কিত। তবে দেশভাগের ট্রমা পশ্চিম ও পুবে দুরকম। দাঙ্গা হানাহানি কোনো দিকেই কম হয়নি, কিন্তু পশ্চিমে লোক বিনিময় হলেও পুবে তা ঘটেনি। উদ্বাস্তুদের তৎকালীন পূর্ব-পাকিস্তান ও পরে বাংলাদেশ থেকে ধারাবাহিকভাবে ভারতে আসার ক্রমিক ইতিবৃত্ত রচিত হয়েছে। উদ্বেগ, উৎকণ্ঠা এবং নিরাশ্রয়তার ভয়ানক অনুভূতি পূর্বাঞ্চলে প্রবহমান। স্বভাবতই পশ্চিম ও পুব দুদিকের সাহিত্যে সেই বাস্তব প্রতিফলিত হয়েছে। অনেকটা এক কোপে কেটে ফেলা আর ধীরে ধীরে অস্ত্র বসিয়ে পেঁচিয়ে কাটার মতো দুধরণের যন্ত্রণা দেশের দুই অঞ্চলে। পূর্বাঞ্চলে দেশভাগ পঁচাত্তর বছর পার করেও এখনো যেন দগ্দগে হয়ে আছে।সম্প্রতি হাতে এল রতন ভট্টাচার্যের লেখা ‘তৃণ’ উপন্যাস। উপন্যাসের উৎসর্গপত্রটি উদ্ধার করছি, ‘সেই সব ছিন্নমূল বাঙালিদের প্রতি বারংবার ভিটে হারানো যাদের ভবিতব্য’। খুবই স্পর্শকাতর বিষয়ে লেখা এই উপন্যাস। পূর্ববঙ্গের ভিটেমাটি ছেড়ে পশ্চিমবাংলার প্রতিবেশী রাজ্য আসামে আশ্রয় নেওয়া উদ্বাস্তুদের জীবনযন্ত্রণার ওপর আলো ফেলা হয়েছে। আমরা সকলেই জানি আসাম ও ত্রিপুরা দুটি রাজ্যেই বহু উদ্বাস্তু খেপে খেপে আশ্রয় নিতে বাধ্য হয়েছেন। স্থানীয় অধিবাসীদের সঙ্গে তাঁদের দ্বন্দ্ব ও তাড়া খাওয়ার ভয়ানক পর্বও রচিত হয়েছে এবং হচ্ছে বারেবারে। কাছাড় নয়, উজানি আসামের ‘ফরকাটিং’ নামে ছোটো শহর এই উপন্যাসের পটভূমি। কেন্দ্রে আছে ললিতমোহন চক্রবর্তীর পরিবার, কিন্তু আলো পড়েছে এই পরিবারের সঙ্গে সংযুক্ত আরো অনেক বাঙালি ও অসমিয়া নরনারীর ওপর। গত শতাব্দীর ষাটের দশকে আসামে কুখ্যাত ‘বঙ্গাল খেদা’ আন্দোলন হয়েছিল। আসামে বাঙালিদের অস্তিত্ব শিক্ষাদীক্ষা, জীবিকার্জন পড়েছিল বিশাল এক প্রশ্নচিহ্নের সামনে। ১৯৬১ সালে শিলচরে বাংলাভাষার জন্য প্রাণ দিয়েছলেন ভাষা-শহীদরা। ১৯৭১-৭২ সালে ভাষা বিলকে কেন্দ্র করে আবার উগ্র হয়ে উঠল বাঙালি বিদ্বেষ। এই উপন্যাসের কালাঙ্ক সেই সময়ে। সেই সময় পশ্চিমবঙ্গে নকশাল আন্দোলনের শেষ পর্ব চলছে, উপন্যাসে সেই প্রসঙ্গও এসেছে।
ললিতমোহন আটচল্লিশ সালে ফরিদপুর থেকে স্ত্রী ও দুই শিশুপুত্র নিয়ে ফরকাটিং-এ আসেন। কোটালিপাড়ার পণ্ডিত শ্বশুরমশায়ের সূত্রে এই শহরে তাঁর কিছু জানাচেনা ছিল। সব বাস্তুহারা পরিবারই আত্মীয়তা বা অন্য কোনো পরিচয়সূত্রে আসামের বিভিন্ন অঞ্চলে নতুন করে শিকড় বসাবার চেষ্টা করেছিল। ব্যাঙ্ক ম্যানেজার সমরেন্দ্র ফরকাটিং-এ নবাগত কলকাতার ঘটিবাড়ির ছেলে অসীমকে জানিয়েছে আসামের ‘নাইনটি এইট পার্সেন্ট’ বাঙালিই পূর্ববঙ্গ থেকে এসেছে। বেশিরভাগই দেশভাগের পর। তবে সর্বত্র বাঙালির সংখ্যা সমান নয়। শিবসাগর জেলায় বাঙালি কম। ফরকাটিং-এ জনসংখ্যার এক-তৃতীয়াংশ হবে। আবার লোয়ার আসামে প্রচুর বাঙালি, আপার আসামে ডিগবয়েও বাঙালি কম নয়। কিন্তু কেমন আছে এই বাঙালিদের অধিকাংশ? উপন্যাসে তারই উত্তর খোঁজা হয়েছে।
ললিতমোহন হোমিওপ্যাথি ও আয়ুর্বেদ চিকিৎসায় দক্ষ। ফরকাটিং বাজারে সাধনা ঔষধালয়ের স্থানীয় এজেন্ট তিনি। মোটামুটি চালু দোকান। চিকিৎসার পাশাপাশি পৌরোহিত্যও তাঁর আর একটা খণ্ডকালীন পেশা। স্ত্রী মিনতি তিন ছেলে পরিমল, নির্মল ও রবি এবং দুই মেয়ে অপর্ণা ও মলিকে নিয়ে সচ্ছল ভাবেই সংসার চলছিল। যদিও বাড়ির কর্তার দরাজ দিলের জন্য সঞ্চয় তেমন কিছু ছিল না। ললিতমোহন বড়ো উদার, সাহায্য করতে উন্মুখ, কোমলপ্রাণ ব্যক্তি। শহরে তাঁর সুনাম যথেষ্ট। আকস্মিকভাবে তাঁর ক্যান্সার ধরা পড়ার পর পরিবারটির ভাগ্যে আর্থিক দুর্দৈব ঘনিয়ে আসে। দোকান বিক্রি করে বড়ো ছেলে পরিমলকে নিয়ে কলকাতায় চিকিৎসা করাতে যেতে বাধ্য হন ললিতমোহন। ক্যান্সারের চিকিৎসা চিরকালই ব্যয়সাপেক্ষ। যোগেন্দ্রনাথ পাল দোকানটি কেনেন, তাঁর দোকানে কর্মচারী হিসেবে যোগ দেয় নির্মল, না হলে সংসার চালানো সম্ভব ছিল না।
উপন্যাস শুরু হয়েছে রঙালি বিহুর দিন অর্থাৎ বাংলা নববর্ষ। পরিবর্তিত আর্থিক অবস্থায় মা আর চার সন্তান মানিয়ে নিতে চেষ্টা করে চলে। অপর্ণা কলেজে পড়ছিল, বি. এ. ফেল করে পড়া ছেড়ে দিয়েছে। সংসারের সাহায্যের জন্য টিউশন করে। মলিও ক্লাস নাইনে উঠে পড়া ছেড়ে দিয়েছে। লেখাপড়ায় মন নেই তাঁর। পরিমল স্কুল ফাইনাল পাশ, নির্মল তাও নয়। ছোটো ছেলে রবি অবশ্য স্কুলের মনোযোগী ছাত্র। ললিতমোহন লেখাপড়াকে খুব দাম দেন, শহরের পরীক্ষার্থীদের সব খবর রাখেন, কিন্তু ‘ঘরামির ঘর ফুটো’ প্রবাদ সত্য করে তাঁর ছেলেমেয়েরাই এই বিষয়ে তাঁকে হতাশ করেছে। তার ওপর পরিমল অতি স্বার্থপর এবং চূড়ান্ত উচ্চাকাঙ্ক্ষী। কলকাতায় বাবার চিকিৎসার শেষ পর্যায়ে বাক্স ভেঙে দুহাজার টাকা নিয়ে সে উধাও হয়ে গেছে। একা ফরকাটিং ফিরে এসেছেন ললিতমোহন। আপাতত সুস্থ কিন্তু শীঘ্রই তাঁর রোগ গুরুতর আকারে ফিরে আসতে দেখবো। ফেরার পথে তাঁর সহযাত্রী ছিল অসীম। কলকাতা থেকে ফরকাটিং এ ব্যাঙ্কের চাকরি নিয়ে আসছিল। নতুন জায়গায় কিছুটা বিপন্ন ছেলেটিকে ললিতমোহন স্বভাব ঔদার্যে কছে টেনে নেন। প্রথম দিন থেকেই অপর্ণার সঙ্গে অসীমের সম্পর্কে রোমান্সের ছোঁয়া লাগে। ললিতমোহন ও মিনতি কি মেয়েদের বাইরের অনাত্মীয় যুবকদের সঙ্গে মেলামেশাতে একটু বেশি স্বাধীনতা দিয়ে ফেলেন? স্বভাবে গম্ভীর, দায়িত্বশীল নির্মলের অন্তত তেমনটাই মনে হয়েছে। স্থানীয় ধনী, অসমিয়া যুবক নন্দন হাজারিকার সঙ্গে অপর্ণার মেলামেশাও সে সহজ ভাবে নিতে পারে না। শিকড় ছিঁড়ে যাবার সঙ্গে সঙ্গে কি পারিবারিক নিয়ন্ত্রণ কিছুটা শিথিল হয়ে যায়? প্রশ্নটিকে নিহিত রাখেন ঔপন্যাসিক। প্রথম রাত্রেই বাড়ির অচেনা অতিথি অসীমের শোবার ঘরে ঢুকে মলির কথাবার্তা এক ধরণের নৈতিক বিচ্যুতির ইঙ্গিত দেয়, ‘লাইনে দাঁড়িয়ে পড়েছেন দেখছি।… তবে খুব সাবধান। দিদির ভক্তসংখ্যা কিন্তু চল্লিশ ছাড়িয়ে গেছে।’ যদিও ব্রাহ্মণ পরিবারের মেয়ের সঙ্গে কায়স্থ অসীমের বিয়ে খুব সহজ হবে না তা মফস্বল শহরের পটভূমিতে বোঝা শক্ত নয়। তবু সম্পর্কটি ক্রমশ ঘনিষ্ঠ হতে থাকে। ইতিমধ্যে রাজ্যের পরিস্থিতিও উত্তপ্ত হতে শুরু করেছে। লক্ষ্মীপুজোর দিন ঘটিবাড়ির ছেলে অসীমের সামনে চক্রবর্তী বাড়ির কোজাগরী লক্ষ্মীপুজোর এলাহি আয়োজনের সূত্রে ‘বাঙালদের লক্ষ্মীপুজো’র বৈশিষ্ট্যগুলি সযত্নে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে কিন্তু ঐ দিনই ঈর্ষায় উন্মত্ত নন্দন হাজারিকা চক্রবর্তী বাড়িতে রাত্রে কুৎসিত হামলা করে। এর আগে একদিন নিজের গাড়িতে তুলে অপর্ণার সঙ্গে অসীমের সম্পর্ক নিয়ে সে তীব্র অভিযোগ তুলেছিল। কিন্তু লক্ষ্মীপুজোর রাতে যখন পুজোয় নিমন্ত্রিত অভ্যাগতরা সবাই বাড়িতে, তখন পানোন্মত্ত হয়ে সীমা-ছাড়ানো অসভ্যতা করতে তার বাধেনি।
‘যখন আমার কাছ থেকে টাকা নিতে। আমার কিনে দেওয়া শাড়ি পরে আমার সঙ্গে সিনেমায় যেতে, হেসে হেসে কথা বলতে, গায়ের ওপর গড়িয়ে পড়তে, তখন কই একদিনও তো বলনি, নন্দনদা, তুমি আমার দাদার মতন? ... এ তোমার অসীমের কলকাতা নয়। এটা আসাম। এ পাড়ায় এমন বুকের পাটা কারও নেই যে নন্দন হাজারিকার গায়ে হাত দেয়? তাকে বার করে দেয় পাড়া থেকে? তুমি ভুলে যেও না অপর্ণা, এটা আসাম।’ অর্থাৎ সরাসরি ভয় দেখাচ্ছে নন্দন। অসমিয়ারা যে ভূমিপুত্র এবং বাঙালিরা নেহাৎ উড়ে এসে জুড়ে বসা আগন্তুক যৌন ঈর্ষাঘটিত তর্কাতর্কির মধ্যে সেই হুমকি অনায়াসে এসে গেছে। অপর্ণার লাঞ্ছনা সহ্য করেনি অবশ্য অসীম, সে নন্দনকে থাপ্পড় মেরে হাত মুচড়ে ধরেছে। পরিবর্তে নন্দন শাসানি দিয়ে গেছে, ‘তুর লাশ নে পেলালে লাইফ মোর নাম নন্দন না হয়। কাল সকালে দেখবি ধানখেতে পড়ে আছিস।’ কী ধরণের নিরাপত্তার অভাব আসামের বাঙালিদের চিরসঙ্গী, মলির তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়ায় তা বোঝা যায়।
‘কী করলেন অসীমদা? ... আসামে বসে একজন অসমিয়াকে মারলেন? কাজটা কিন্তু সাঙ্ঘাতিক হল।’
অপর্ণা জানায় টালিগঞ্জ থেকে দুটি ছেলে এসে গতবছর অসমিয়া ছেলেদের সঙ্গে মারামারিতে জড়িয়ে পড়েছিল। রাতে পাঁচশো অসমিয়া ছেলে তাদের বাড়ি ঘিরে ফেলে চিৎকার শুরু করে, কলকাতা থেকে দুটো নকশাল ছেলে এসেছে তাদের মুণ্ডু চাই। পুলিশ এসে ছেলেদুটিকে থানায় নিয়ে দুরাত্রি আটকে রাখে যেন তারা সত্যিই নকশাল, তারপর কলকাতার ট্রেনে তুলে দেয়। যারা হামলা করেছিল তাদের কিছুই বলেনি। অর্থাৎ প্রশাসনে স্পষ্ট পক্ষপাতিত্ব ছিল। ‘বঙ্গাল খেদা’র পর থেকে আসামের বাঙালিদের মনে ভয় ঢুকে গেছে। তারা জানে তারা এই রাজ্যে ‘বিদেশি’।
ক্রমশ উপন্যাসে ছোটো ছোটো ঘটনায় উন্মোচিত হতে থাকে কীভাবে বাঙালিরা কোণঠাসা হয়ে পড়ছে। কোনো এজেন্সি পাওয়া, টেন্ডার বা অর্ডার ধরার ব্যাপারে তাদের ইচ্ছে করে পিছিয়ে দেওয়া হচ্ছে যোগ্যতা থাকা সত্বেও। ব্যাঙ্কের অসমিয়া ও বাঙালি কর্মচারীদের মধ্যে তর্কাতর্কির মাধ্যমে ঔপন্যাসিক অসমিয়া অস্মিতার চারিত্র্য তুলে ধরেছেন। বাঙালিদের তারা অনেকটা ঔপনিবেশিক দখলকারী মনে করে। দেবরাজ ফুকন বলেছে, ‘আসাম ইংরেজদের অধিকারে আসার সঙ্গে সঙ্গে দু’জনকেই ইংরেজরা আসামে নিয়ে এসেছিল। ইংরেজি জানা বাঙালি আমলা আর বাংলা ভাষা। ... আঠারোশো পঁয়ত্রিশ সাল পর্যন্ত আসামের সরকারি ভাষা ছিল বাংলা ... আপনাদের গ্রেট পোয়েট রবীন্দ্রনাথ পর্যন্ত মনে করতেন যে অসমিয়া ভাষা হল বাংলা ভাষারই একটা ডায়লেক্ট ... অসমিয়া ভাষাকে তার নিজের দেশে প্রতিষ্ঠা পাবার জন্যে একদিন ভীষণ লড়তে হয়েছিল বাংলা ভাষার সঙ্গে। ... রেল, এল আই সি, সিমেন্ট ফ্যাক্টরি, অয়েল রিফাইনারি, পোস্ট অফিস, সর্বত্র বাঙালি ... অতএব আসামের সংগ্রাম চলছে চলবে।’
দেবরাজ ফুকনের কথায় হয়তো অনেকখানি সত্য আছে কিন্তু আসামের বাঙালিদের পৃথিবীতে কোথাও তো আলাদা ভূখণ্ড নেই। দেশভাগের পর পূর্ববঙ্গ থেকে তারা এসে আসামে বসবাস করেছে। আসাম তাদের দেশ। তাদের কি চিরকাল বহিরাগত উদ্বাস্তু হয়ে থাকতে হবে? রাষ্ট্রের কি এই ব্যাপারে কোনো দায়িত্ব নেই? ললিতমোহন যখন মৃত্যুশয্যায় তখন পরিবারের দায়িত্ব নিয়ে জর্জরিত নির্মলের মনে হয়েছে, ‘মিনতি ললিতমোহনের তবু একদিন আলাদা একটা দেশ ছিল। সেই দেশের স্মৃতি সবসময় তাদের মাথায় আছে। কিন্তু নির্মল, মলি, অপর্ণার তো এই আসামই দেশ। জ্ঞান থেকেই এখানে আছে। এখানকার জল হাওয়া মাটিতে একটু একটু করে বড়ো হয়েছে। আসামই তাদের জন্মভূমি। আবার যদি একটা বঙ্গাল খেদা হয় কোথায় যাবে তারা?’ ফরকাটিং-এর প্রতিটি বাঙালি পরিবারের মনে এক ভয়, আবার কি উচ্ছেদ হতে হবে তাদের? চৌধুরীকাকার সংলাপে দেশভাগ ও স্বাধীনতার পর পূর্ববঙ্গের হিন্দু উদ্বাস্তুদের ভয়ংকর নিরাশ্রয়তা উঠে এসেছে, ‘স্বাধীনতার জন্যে বড্ড বেশি মূল্য দিলাম আমরা। পঁচিশ বছর পার হয়ে গেল। এ বছর স্বাধীনতার রজত জয়ন্তী হল। কিন্তু আমরা হাজার হাজার লক্ষ লক্ষ পূর্ববঙ্গের মানুষ, আমরা এখনও তৃণের মতো ভেসেই চলেছি। আমাদের কথা কেউ ভাবল না। আমরা মানুষ না। আমাদের ঘর-দুয়ার নাই, স্বাধীনতা নাই। নিজস্ব মতামত নাই। আমরা যেন দাবার ঘুঁটি।’ আসামের উদ্বাস্তু বাঙালির সঙ্গে এখানে একাকার হয়ে যায় দণ্ডকারণ্য, মানা ক্যাম্প, মরিচঝাঁপি। আবার সেই সীমা ভেঙে আজকের পৃথিবীতে নানা ধরণের সন্ত্রাস ও অত্যাচারে ঘরছাড়া লক্ষ লক্ষ মানুষ আমাদের সামনে এসে দাঁড়ায়। মায়নামার থেকে উৎখাত হওয়া রোহিঙ্গারা পলকা নৌকো করে প্রাণ হাতে নিয়ে টেকনাফ নদীতে ভেসে যায়। হাজার বছরেও আরাকান তাদের দেশ হল না। পালাতে গিয়ে ভূমধ্যসাগরে ডুবে মা আর ভাইয়ের সঙ্গে মারা যায় সিরিয়ার অ্যালান কুর্দি। সমুদ্রতটে উপুড় হয়ে পড়ে থাকে দুবছরের শিশুটির দেহ। ‘তৃণ’ উপন্যাসের সময়কাল থেকে পৃথিবীজোড়া উদ্বাস্তুদের অস্তিত্বসংকট আরো তীব্র, আরো মারাত্মক হয়েছে।
ললিতমোহনের মৃত্যুর পর অসীম ও অপর্ণা যখন ভবিষ্যতে ঘর বাঁধার কথা ভাবতে শুরু করেছে তখনি সিনেমাহলে ভাড়াটে গুন্ডারা অসীমের ওপর ছুরি নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ে। রক্তে ভেসে যায় তার শরীর। অপর্ণা সঙ্গেই ছিল। হাসপাতালে অসীমের চিকিৎসার সময় দুজন বিপদের মুখে দাঁড়িয়ে আরো ঘনিষ্ঠ হয়। অসীম পুলিশের কাছে নন্দন হাজারিকার নাম করেনি, অপর্ণাকে লোকাপবাদ ও কলঙ্ক থেকে বাঁচতে চেয়েছে। কিন্তু এই দুর্ঘটনাই তাদের বিচ্ছিন্ন করে দিল। পিতৃমাতৃহীন অসীমকে বড়ো করেছেন তার নিঃসন্তান বড়োমামা ও বড়োমামিমা। খবর পেয়ে কলকাতা থেকে বড়োমামিমা ছুটে আসেন। উচ্চশিক্ষিতা, অভিজাত, ধনী, নানা ধরনের সমাজসেবায় যুক্ত বড়োমামিমা প্রথম থেকেই বুঝিয়ে দেন অপর্ণার সঙ্গে অসীমের সম্পর্কে তিনি খুশি নন। অপর্ণাকে প্রায় যেন দেখতেই পান না তিনি। অসীমকে তার আপ্রাণ শুশ্রুষা করা কোনো দামই পায় না তাঁর কাছে। রিফিউজি পরিবারের জৌলুসহীন মেয়েকে রীতিমতো অবজ্ঞা করেন। অপর্ণা অনুভব করে এই অপমান। ‘আমি জানি, আমায় কেউ ভালবাসে না। আমি দেখতে ভাল না। কুৎসিত। আমরা গরিব। আমার বাবা নেই। আমি ...।’ যে শব্দটি অপর্ণা বলেনি তা হল ‘দেশহারা’ ‘ছিন্নমূল’ ‘রিফিউজি’। বড় মামিমা অসীমকে নিয়ে কলকাতা ফিরে যান। কথা ছিল পনেরো দিনের মধ্যে চলে আসবে অসীম। কিন্তু মাস গড়িয়ে যায়, অসীম আর ফেরে না। হয়তো তার পরিবার তাকে বুঝিয়ে ফেলেছে অভিজাত সম্পন্ন বংশে অপর্ণার মতো গরিব উদ্বাস্তু মেয়ে জানায় না। পূর্ববঙ্গের দেশছাড়া, ভিটেমাটি ছাড়া, নিঃস্ব পরিবারগুলিকে পশ্চিমবঙ্গের অভিজাত ধনাঢ্যরা যে নীচু চোখে দেখতেন তাতে তো কোনো সন্দেহ নেই। এখনো বিতৃষ্ণা পুরো দূর হয়েছে বলা যায় না।
ইতিমধ্যে ভাষা বিল নিয়ে আসামে গণ্ডগোল পাকিয়ে ওঠে। অসমিয়া ছাত্রনেতা অনিল শর্মাকে কে বা কারা খুন করে রেললাইনের ধারে ফেলে রেখে গিয়েছিল। সব দোষ বাঙালিদের ওপর এসে পড়ে। যদিও একটি অসমিয়া মেয়েকে নিয়ে প্রতিদ্বন্দ্বিতার জেরে কোনো অসমিয়াই খুনটা করেছিল। কিন্তু এই ছুতোয় বাঙালিদের দোকানপাট লুঠ করে ভাঙচুর চলে। কারফিউ জারি হয় আর তার মধ্যে বাঙালি বসতি দেবনগরের ঘরবাড়িতে আগুন লাগানো হয়। নির্মল, অপর্ণাদের বাড়িও সম্পূর্ণ পুড়ে যায়। উপন্যাসের শেষে অঞ্চলের সব বাঙালিরাই পুনরায় ছিন্নমূল হয়ে নতুন কোনো আশ্রয়ের সন্ধানে চলে। ফরকাটিং-এ থাকলে হয়তো প্রাণ যাবে, ধ্বস্ত হবে মেয়েদের সম্মান, আর তাদের কোনো ভরসা থাকে না। মিনতি ও ছেলেমেয়েদের নিয়ে ট্রাকে চাপেন। এবার আশ্রয় খুঁজবেন পশ্চিমবঙ্গে। ট্রাকটা যেন পূর্ববঙ্গের হিন্দু উদ্বাস্তুদের প্রতীক, ‘সেই উনিশশো সাতচল্লিশ সাল থেকে অবিরাম ছুটেই চলেছে। ভেতরে অসহায় ক্লান্ত গুটিকয়েক মানুষ। তারা চলেছে মাটির সন্ধানে। বসবাসের জন্য নিজস্ব নিরাপদ এক টুকরো মাটি।'
উপন্যাসটি পাঠকের মনে গভীর বিষাদ ঘনিয়ে আনে। আসামে বাঙালিদের নিরাপত্তাহীনতা নিয়ে পশ্চিমবঙ্গে খুব বেশি লেখালেখি হয়নি। ‘তৃণ’ ব্যতিক্রমী উপন্যাস। রতন ভট্টাচার্য লিখেছেন খুব কম, মাঝেমাঝেই লেখার জগৎ থেকে নিজেকে গুটিয়ে নিতেন। বিষয়বস্তু সম্বন্ধে নিবিড় অভিজ্ঞতা, আশ্চর্য নির্ভার গদ্য, জীবন্ত চরিত্রের মিছিল, ঘটনা ও মনের গহনে সন্ধানী আলোকসম্পাত তাঁর গল্প উপন্যাসের বৈশিষ্ট্য। ‘তৃণ’ তাঁর লেখক চারিত্র্যের সব বৈশিষ্ট্যগুলিই ধারণ করেছে। আশ্চর্য প্রাণবন্ত তাঁর সংলাপ রচনার ক্ষমতা, এই উপন্যাসে বাংলা ও অসমিয়া দুটি ভাষাই ব্যবহৃত হয়েছে আবার অসমিয়া-বাংলা মিশ্র ভাষাও কম নেই। একটি পরিবারকে কেন্দ্র করে আসামের লক্ষ লক্ষ হিন্দু বাঙালির অস্তিত্বের সংকট বড়ো বাস্তবভাবে ফুটে উঠেছে এই উপন্যাসে। ঠিক এমনটি আর কোথাও পাইনি।
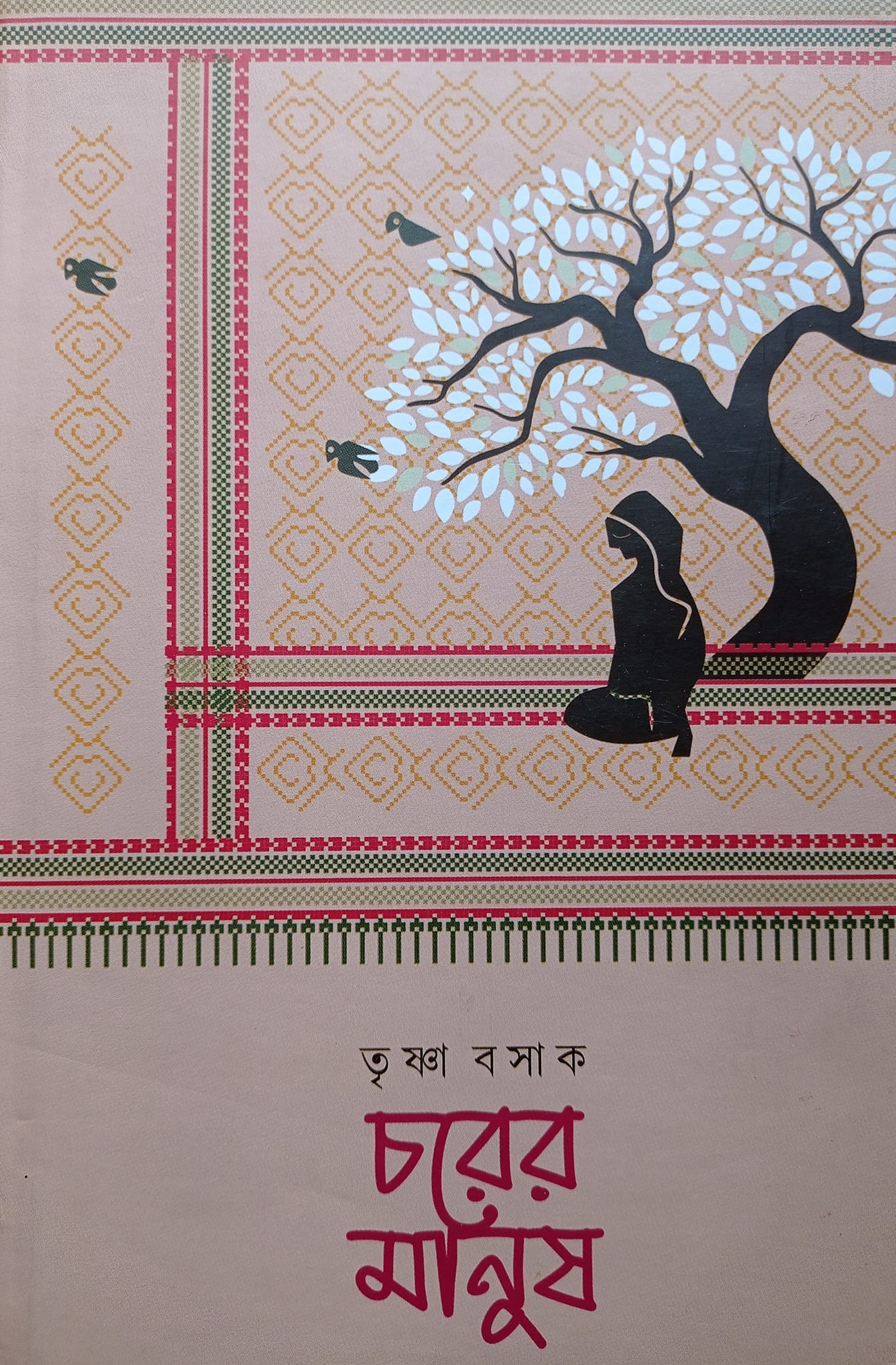 চরের মানুষ — তৃষ্ণা বসাক; প্রচ্ছদ - সুপ্রসন্ন কুণ্ডু; প্রকাশক- ধানসিড়ি, কলকাতা; প্রথম প্রকাশ- অক্টোবর ২০২১; ISBN: 978-93-91051-49-5
চরের মানুষ — তৃষ্ণা বসাক; প্রচ্ছদ - সুপ্রসন্ন কুণ্ডু; প্রকাশক- ধানসিড়ি, কলকাতা; প্রথম প্রকাশ- অক্টোবর ২০২১; ISBN: 978-93-91051-49-5
তৃষ্ণা বসাকের ‘চরের মানুষ’-ও বিষয়বস্তুর দিক দিয়ে ব্যতিক্রমী। পূর্ব পাকিস্তান ও পরে বাংলাদেশের হিন্দু পরিবারগুলির জীবনছবি রয়েছে এই উপন্যাসে। তারা ঠিক সরাসরি উদ্বাস্তু নয়, কিন্তু অদ্ভুত এক দ্বিধা ও নিরাপত্তাহীনতার মধ্যে তাদের বসবাস। ১৯৪৭ সালের পর দলে দলে হিন্দুরা দেশ ছেড়েছে, যে অংশটি মাতৃভূমি আঁকড়ে পড়ে আছে, সম্ভবত কোনো উপায় নেই বলেই তারা রয়ে গেছে। ওদেশে তবু পেটের ভাত জুটছে ভারতে এলে তাতেও টান পড়বে এই মনোভাব থেকেই তাদের অধিকাংশের ভিটেমাটি আঁকড়ে থাকা। রতন ভট্টাচার্যের মতো জন্মসূত্রে পূর্ববঙ্গীয় নন তৃষ্ণা। কিন্তু ক্রমশ তাঁদের জীবনসমস্যা টেনেছে তাঁকে। শুধু দেশহারা হওয়া নয়, আপন দেশে পরবাসী হয়ে থাকার বেদনা তাঁকে গভীরভাবে স্পর্শ করেছে। দীর্ঘদিন আসামে বাস করার পরও যেমন বাঙালিদের কাছে সেই রাজ্যের মাটি আপন হচ্ছে না তেমনি পূর্ব পাকিস্তান ও পরে বাংলাদেশ কতটুকু স্বভূমি হয়ে উঠছে হিন্দু পরিবারগুলির কাছে এই জরুরি প্রশ্ন তুলেছেন তিনি। ‘চরের মানুষ’ উপন্যাসের স্থানপট মোটামুটি ময়মনসিংহ আর ঢাকায় ঘোরাঘুরি করেছে। কালপট গতশতকের ষাটের দশক থেকে একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধ পেরিয়ে এসেছে। সেদিক দিয়ে একই কালপর্ব দুটি উপন্যাসের, ‘তৃণ’ও ‘চরের মানুষ’--অন্তত আংশিকভাবে।‘চরের মানুষ’ উপন্যাসের কেন্দ্রে আছে প্রধানত দুটি পরিবার। ময়মনসিংহ শহরের সুরেশ ডাক্তার, তার স্ত্রী লক্ষ্মীরানি, তাদের সাত মেয়ে আর দুই ছেলে — সচ্ছল সংসার। সুরেশ ডাক্তারের মেয়ে টুনু ওরফে ছায়া এই উপন্যাসের প্রধান চরিত্র। সাত মাসে জন্ম হওয়াতে তাকে সবাই ভাবে রোগা ভোগা। খানিকটা বোকা বলেও মনে করে। কিন্তু টুনুর অনুভবের শক্তি কিছু কম নয়। ‘তৃণ’ যেমন শুরু হয়েছে ‘রঙালি বিহু’-র দিন ‘চরের মানুষ’ শুরু হয়েছে অক্ষয় তৃতীয়ার সকালে। কাসুন্দি বানানোর তোড়জোড় শুরু হয়েছে সুরেশ ডাক্তারের অন্তঃপুরে। কত পালপার্বণ পুজো দিয়ে ঘেরা হিন্দুদের জীবন, কোনো পুজো বা ব্রততেই পান থেকে চুন খসার জো নেই। দ্বিতীয় পরিবারটি ময়মনসিংহের ধূপতারা গ্রামের তারাচরণ ও পারুলবালার। দরিদ্র হলেও পারুলবালা সন্তানগরবে গরবিণী, কারণ তার পাঁচ ছেলে তিন মেয়ে। পুত্রসন্তান হওয়া মানেই মায়ের গৌরব বেড়ে যাওয়া, কন্যাসন্তান কেউ চায় না — তারা এসে পড়ে। তাদের পড়াশোনা শিখিয়ে স্বাবলম্বী করার কথা কেউ ভাবে না, মোটামুটি লেখাপড়া, ঘরের কাজ শিখিয়ে পাত্রস্থ করার কথাই ভাবা হয়। তৃষ্ণা এমনও এক সামাজিক পারিবারিক সংস্কৃতির কথা বলেছেন যেখানে সামন্ততান্ত্রিক ঐতিহ্য পুরোপুরি লেগে আছে। পুরোনো দিনের সংস্কার, বিশ্বাস এবং অভ্যাস জড়ানো এক পশ্চাৎপদ জনসমষ্টি। যে দেশে তারা বসবাস করে সেখানকার সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলমান সম্প্রদায়ের সঙ্গে তাদের যোগাযোগ ক্ষীণ। কোথায় যেন অবিশ্বাস, অনাস্থার দুর্ভেদ্য প্রাচীর উঠে রয়েছে দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে। প্রথম থেকেই ঔপন্যাসিক এই পারস্পরিক অবিশ্বাসকে স্পষ্ট করেছেন। সুরেশ ডাক্তারের বড়ো ছেলে মৃত্যুঞ্জয়কে খুন করেছে নজর আলি। সুরেশ ডাক্তার বলেন বউকে খুন করে পুলিশের তাড়া খেয়ে ঝোপে লুকিয়ে ছিল নজর আলি, মৃত্যুঞ্জয় সেখানে গিয়ে পড়াতে ভয় পেয়ে গিয়ে মেরে দিয়েছে। কোনো মুসলমান গিয়ে পড়লেও মারত। কিন্তু সেই কথা কি বিশ্বাস করে কেউ? টুনুদের বাড়ির রাঁধুনি মানোর মা সরাসরি বলেছে, ‘শুনো টুনু, তোমার বাবার এ দ্যাশে পসার রাখতে হইব। উনি এ বয়সে ইন্ডিয়ায় গিয়া কিছু করতে পারব? তাই মুসলমান প্যাশেন্টদের হাতে রাখার জন্য ওইসব কইছে।’ টুনু যে প্রতিবেশী মুসলমান বাড়ির বন্ধু পপির সঙ্গে খেলতে যায় সেটাও লুকিয়ে। বাড়ির কেউ পছন্দ করে না। মানোর মা ধমক দেয়, ‘কুথায় যাবা জানি। মোসলমানের উঠানের বাতাস না-খাইলে তোমার প্যাটের ভাত হজম হয় না তো।’ দুর্গাবাড়ি যাবার সময় টুনুর জেঠি বৌমেয়েদের নিয়ে রিকশা ভাড়া করার সময় সন্ত্রস্ত দৃষ্টিতে দেখে নেয়, রিকশার পিছনে লেখা ‘এলাহি ভরসা’। ‘মুসলমানদের নিয়ে পদে পদে চলা। রিশকাউলা, কামলা, মিস্তিরিমজুর।’ মৃত্যুঞ্জয়ের মৃত্যুর বর্ষপূর্তিতে স্মরণসভা করার জন্য তার মুসলমান সহপাঠীরা জেঠির রিকশার সামনে এসে কথা বলতে চাইলে জেঠি সরাসরি প্রত্যাখ্যান করে। ছেলেগুলির মুখে চোখে অপমান ফুটে ওঠে। ওদের মলিন মুখ টুনুকে ব্যথা দেয়। কিন্তু রিকশাওলার স্বগতোক্তিতে ফুটে ওঠে বাড়ির বড়োদের অনাস্থা। ‘আপনাগো মতো বাবুলোকেরা সব লেঙ্গুর তুলে পলায়েছেন, তায় হইল মুশকিল। যারা যারা পইড়া আছেন, তাদের আর কত সওন লাগে। আপনাগো কেউ টিকতে দিবে ভাবেন?’
পারুলবালার বোন আশালতার উক্তিতে ফুটে ওঠে এক অদ্ভুত নৈরাশ্য ‘আমাদের একদিন না একদিন যাইতে হইবই। ত্যালে জলে কুনোদিন মিশ খায়?’ তবে খবর পাওয়া যায় বাঙালির মুখের ভাষা কাড়তে চলেছে পাক সরকার। তিরাশি বছরের ফজলুল হক খণ্ডিত দেশের প্রধানমন্ত্রী হয়ে কলকাতায় এসে আবেগাপ্লুত হয়ে বলে বসেছিলেন, ‘দুই বাংলার মধ্যে যে ব্যবধান আছে, তাহা একটি স্বপ্ন ও ধোঁকা মাত্র। করুণাময় খোদাতালার দরবারে আমার একটি প্রার্থনা তিনি যেন এই ব্যবধান দূর করেন।’ তড়িঘড়ি করাচি থেকে ডেকে পাঠানো হল হক সাহেবকে। রাষ্ট্রদ্রোহিতার অভিযোগে মন্ত্রিসভা বাতিল হল। টীকাটুলির বাসায় নজরবন্দী হয়ে রইলেন তিনি। গ্রেফতার করা হল আওয়ামি লিগ নেতা শেখ মুজিবর রহমানকে। ক্রমে স্বৈরাচারী শাসক আয়ুব খান বলবেন, ‘সারি জবান মিলিজুলি কর এক জবান বানানা চাহিয়ে, উয়ো উর্দু নেহি, উয়ো বাংলা ভি নেহি, উয়ো পাকিস্তানি জবান।’ কিন্তু দেশজোড়া এই উথালপাথালে কেমন নির্বিকার নির্লিপ্ত এই উপন্যাসের চরিত্ররা। আশালতা বলেছে, ‘হেরা ভাবছিল, হিন্দুগো তাড়ায়ে খুব সুখে থাকব। এখন নিজেদের ভিতরেই কাজিয়া বাধসে। এই সকল ব্যাপারে আমাদের কীসের লেনাদেনা? দ্যাশ যখন আর আমাদের হাতে নাই, তখন অগো মেকুর অরাই সামলাক।’ পারুলবালার ছেলে অমর পড়ে করুটিয়া কলেজে। মুসলমান সহপাঠীরা বাঙালি জাতীয়তাবোধের জাগরণের লড়াইতে তাকে ডাক দেয়, কিন্তু অমরের মনে তো সংখ্যাগরিষ্ঠ সম্প্রদায়ের ওপর বিন্দুমাত্র আস্থা নেই। এমনও কি শেখ সাহেবও তার বিশ্বাসের পাত্র নন। ‘কট্টর মুসলমানরা ময়মনসিংহ না বলে মোমেনশাহি বলতে পছন্দ করেন। আওয়ামি মুসলিম লিগের প্রধান শেখ মুজিবর সেই ঐতিহাসিক কাউসিলের রিপোর্টে মোমেনশাহি লিখেছেন — অমর দেখেছিল।’ ভাষা আন্দোলন তার মনে দাগ কাটে না। সে জানে নজরুলের কবিতার ‘মহাশ্মশান’ কেটে ‘গোরস্থান’ করা হয়েছে। রবীন্দ্রনাথকে হিন্দু কবি বানানো হয়েছে। তার ছোটোভাই সকালে উঠে দুলে দুলে পড়ত — ‘ফজরে উঠিয়া আমি মনে মনে বলি / সারাদিন আমি যেন নেক হয়ে চলি।’ তবু সহপাঠীদের সে বিদ্বিষ্ট স্বরে বলে, ‘আজ তোমরা ভাষারে মা ডাকো, দেশরে মা ডাকো, একদিন তোমরাই পদে পদে এর বিরোধিতা করস। বন্দোমাতরম্ গাওনি, সাহেব খেদানোর কোনো আন্দোলনে যোগ দিতে চাওনি, তা নাকি হিন্দুদের আন্দোলন। ভারতমাতার ছবি ছিল বলে মিছিলে পর্যন্ত হাঁটোনি। ... কী কইরা আমাদের পাশে পাইবা মনে করো?’
পাঠকের কাছে স্পষ্ট হয়ে যায় ‘তৃণ’ উপন্যাসে আসাম যেমন উদ্বাস্তু বাঙালির কাছে পরবাস, ‘চরের মানুষ’ উপন্যাসে নিজের ভিটেবাড়িতে বসেও হিন্দু বাঙালি পরবাসী। তাদের জীবন ঘুরপাক খায় ব্রতপার্বণ, পুজো আর নানাবিধ খাদ্য রন্ধন ও ভোজনের আয়োজনে। সুরেশ ডাক্তারের সম্পন্ন সংসারে তিনবেলাই ভাত আর নানা ধরনের মাছের সুস্বাদু পদ তৈরি হয়, নিরামিষের ব্যবস্থাও কিছু কম যায় না। আবার পারুলবালার দরিদ্র সংসারে শুধু হাতের গুণে নানারকম সামান্য সবজিপাতি বা শুকনো মাছ দিয়ে নানা উপাদেয় খাদ্য তৈরি হয়। পূর্ববঙ্গের মানুষের যে রান্নাবান্না ও খাওয়ার দিকে মাত্রাতিরিক্ত ঝোঁক আছে তা তৃষ্ণা লক্ষ্য করেছেন। উচ্চশিক্ষিত হিন্দুরা প্রায় সবাই দেশ ছেড়েছে। যারা রয়ে গেছে তাদের স্কুল-কলেজের পড়ার বাইরে বইপত্রের সঙ্গে সংযোগ ক্ষীণ। বাড়িতে বাইরের বই বলতে খুঁজে পাওয়া যাবে শুধু পঞ্জিকা। সাংস্কৃতিক দৈন্যের ছবি পরিস্ফুট করেন ঔপন্যাসিক। আপন সমাজের প্রতিই বা তাদের দায়িত্ববোধ কতটুকু। বারম্বার একতরফা সাম্প্রদায়িক আক্রমণের শিকার হয়ে আত্মবিশ্বাস ও পারস্পরিক দায়বোধের জমি নষ্ট হয়ে টিঁকে আছে ভীতু, কোনোমতে প্রাণ বাঁচানো স্বার্থবাদী একটি গোষ্ঠী। ঢাকার বিখ্যাত বসাকবাড়ির ইতিহাস বর্ণনা করেছেন তৃষ্ণা। সোনা এবং অন্যান্য ব্যবসায়ে সম্পদশালী সেই বাড়িতে বারবার আক্রমণ চালানো হয়েছিল। হিন্দু ব্যবসায়ীদের হাত থেকে ব্যবসার রাশ অবাঙালি মুসলমান ব্যবসায়ীদের হাতে তুলে দেবার জন্য। বারবার গৃহদেবতাকে বুকে নিয়ে তাদের পালাতে হয়েছে। ফিরে আসার পর কেমন ভুলভুলাইয়ার মতো করে ফেলেছে তারা বাড়িঘর। খানিকটা দুর্গ দুর্গ যাতে আড়াল থেকে যুদ্ধ চালানো যায়। গলিঘুঁজির বাঁকে বাঁকে গ্রাম থেকে তুলে এনে গরিব আত্মীয়দের বসানো হয়েছে। দাবার বোর্ডে রাজার সামনে যেমন একসার বোড়ে থাকে, তেমনি তারা সাজানো থাকে এ বাড়ির মালিকদের সামনে। ঘাতকের দল ঢুকলে সামনে তাদেরই আগে পাবে। তাদের হত্যার অবসরে নারায়ণ বুকে চেপে গৃহপতিরা পালিয়ে যেতে পারবে। শহিদুল জহিরের বিখ্যাত গল্পও ‘ইন্দুর বিলাই খেলা’ মনে পড়ে। এক অদ্ভুত নিপাতনে সিদ্ধ ব্যতিক্রমী জীবন অবশ্য এই বাড়ির সুন্দরী মেয়ে শিউলির। সিনেমায় নেমে ‘শবনম’ নামে সে বিখ্যাত হয়েছে পূর্ব ও পশ্চিম উভয় পাকিস্তানেই। বোঝা যায় শিউলি চরিত্রে পড়েছে বাস্তবের ঝর্ণা বসাক নামে বিখ্যাত চিত্রাভিনেত্রীর ছায়া। তাঁরও চলচ্চিত্রের নাম ‘শবনম’।
যে সমাজ এমনও ভীরু কাপুরুষের মতো পিঠ বাঁচাতে ব্যস্ত থাকে, পিতৃতন্ত্র তার ওপর জেঁকে বসে থাকবেই। বিভিন্ন পুঙ্খতায় তৃষ্ণা এই পিতৃতান্ত্রিক দাপটের কুশ্রী ছবি ফুটিয়ে তুলেছেন। শুধু পুত্রসন্তান জন্মানোর জন্য আকুলিবিকুলি নয়, এই দাপট পুরুষকে দিয়েছে পরিবারের মেয়েদের যৌন নির্যাতন করার গোপন অধিকার। মায়ের স্থান মহোচ্চে — সেটাও পিতৃতন্ত্রেরই কৌশল। বাড়ির বৌদের গায়ে যখন তখন হাত তোলা যায়, চড় থাপ্পড় মারা যায়। বিয়ের পণে মোটর সাইকেল বা ঘড়ি পেতে দেরি হলে ততোদিন স্ত্রীর স্বামীর শয্যায় অধিকার থাকে না। পুত্রবধূদের যৎপরোনাস্তি নির্যাতন করে শাশুড়ি পরম আহ্লাদ পায়। সুরেশ ডাক্তারের ভালোমানুষ মেয়ে টুনুর সঙ্গে বিয়ে হয়েছে পারুলবালার সবচেয়ে উপযুক্ত ডাক্তার ছেলে অমরের। পড়াশোনায় মেধাবী, কঠোর পরিশ্রমী, পরিবারের প্রতি দায়িত্ববান অমরের নৈতিক চরিত্র কলুষিত। অনেক কষ্ট করে জীবনে দাঁড়িয়েছে তাই সম্ভোগের ব্যাপারে সে সম্পূর্ণ বিবেকবর্জিত। নারী তার কাছে শুধু মাত্র ভোগের বস্তু। নবোঢ়া স্ত্রীকে শারীরিক কোনো সৌন্দর্যের ঘাটতি নিয়ে অনায়াসে সে কুবাক্য বলতে পারে। বড়ো বৌদি বা কিশোরী শ্যালিকার সঙ্গে দৈহিক ঘনিষ্ঠতায় তার অবৈধ উৎসাহ। নার্সদের নিজের বিছানায় টেনে আনাতেও তার ক্ষান্তি নেই। দরকার পড়লে টুনুকে ত্যাগ করতেও তার বাধবে না বোঝা যায়। সুন্দরী নার্স শোভনা তরফদারকে নিয়ে ইন্ডিয়ায় পালাতে চেয়েছিল সে। ‘এই মুসলমানের দ্যাশে আমাগো কুনো ভবিষ্যৎ নাই। টুনুর বাপে অরে যেত দিব না।’ শোভনা কিন্তু সপাটে উত্তর দিয়েছিল, ‘কে কইসে এইডা মুসলমানের দ্যাশ? এ আমাগো সগ্গলের দ্যাশ। যারা বাংলাভাষায় কথা কয় তাদের দ্যাশ। মায়ের বিপদে মারে ফেলায়ে পলাইতে চান কেমন পুরুষমানুষ আপনে?’
একাত্তরের মার্চ মাসে খানসেনারা অপারেশন সার্চলাইট শুরু করলে এই সাহসী মেয়েটি সেনা ব্যারাকে ধর্ষিত হয় ও প্রাণ হারায়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপক ও ছাত্রদের ওপর পাশবিক হামলার বর্ণনা দিয়েছেন তৃষ্ণা। বাংলোগুলির গেট ভাঙা, হলগুলি থেকে চীৎকার আর কান্নার শব্দ। কত যে লাশ, কত মেয়ের ইজ্জত নিয়ে ছিনিমিনি চলছে। সেদিন তিনশো ছাত্রকে খুন করা হয়েছিল। বহু অধ্যাপক প্রাণ হারান। শহর থেকে গ্রামেও চলে গেছে খানসেনা আর তাদের সহযোগী রাজাকাররা। সদ্যোজাত পুত্রকে নিয়ে টুনু তখন শ্বশুরবাড়িতে। রাজাকাররা এসে তার জ্যাঠাশ্বশুর আর তার দুই ছেলেকে মেরে রেখে গেছে, জল চাইলে ওদের গলা দিয়ে খেজুর কাঁটা ঢুকিয়েছে আর বার করেছে। জঙ্গলে গা ঢাকা দিয়ে থাকলেও টুনু নিস্তার পেত না, দেওরের শেখানো কলমা আবৃত্তি করে সে বেঁচে যায়। পাক সেনারা মুসলমান মনে করে তাকে নিষ্কৃতি দেয়। যদিও হত্যা ও ধর্ষণের এই নারকীয় তাণ্ডবে মুসলমান নরনারী যে সবাই নিস্তার পেয়েছিল এমন তো নয়। তিরিশ লক্ষ মানুষের নিধন, দুই লক্ষ মেয়ের ধর্ষণের সিংহভাগ শিকার মুসলমানরাই। অমর যথারীতি গা বাঁচিয়ে পালাতে সক্ষম হয়। যে উদার হৃদয় বি. পি. সাহার হাসপাতালে সে চাকরি করত, যিনি নানাভাবে সাহায্য করেছেন অমরকে, ছেলের মতো ভালোবেসেছেন, অনায়াসে অমর খানসেনাদের তাঁর বাড়ি চিনিয়ে দেয়। উন্মত্ত আর্মি বি. পিকে, তাঁর মুসলিম জামাইকে খুন করে, তাঁর শিশু নাতিকে নিয়ে কোনোমতে পালায় এক নার্স। বি.পি-র মেয়ের পিছনে তাড়া করে মিলিটারি। মেয়েটা ডুকরে ওঠে অমরকে চিনতে পেরে। ‘ডাক্তারবাবু, আমারে বাঁচান।’ ইতিকর্তব্য ঠিক করতে অমরের দেরি হয় না। ‘একে বাঁচাতে যাওয়ার অর্থ নিজের মৃত্যু ডেকে আনা। তাছাড়া যে মেয়ে মুসলমানের সঙ্গে বেরিয়ে গেছে তাকে মুসলমানের হাত থেকে বাঁচাতে যাওয়ার কোনো মানে হয় না। তাকে নিজেকে বাঁচতে হবে।’ অমরের কাছে মানুষের ধর্মীয় সংজ্ঞার বাইরে কোনো পরিচয় নেই। তবে চোখের সামনে টুনুকে অপহৃত হতে দেখলেও নিশ্চয়ই সে কোনো না কোনো ভাবে গা বাঁচানোর ফিকির খুঁজত। অমরের মতো মানুষ যেকোনো মূল্যে নিজেকে রক্ষা করার পথ খুঁজে নিতে পাকা। শিলিগুড়িতে পালিয়ে গিয়ে এক জ্ঞাতি দাদার বাড়িতে ওঠে সে, পরে চাকরি জোগাড় করে কার্সিয়াং টি. বি. হাসপাতালে। তারপরই শ্বশুরকে হুমকি চিঠি দেয় অবিলম্বে শিশুপুত্রসহ টুনুকে যেন প্লেনে করে তার কাছে পাঠানো হয়। ‘নইলে জেনে রাখবেন আমি আপনার কন্যাকে ডাইভোর্স দিতে বাধ্য হব।’ উপন্যাসের শেষে রয়েছে টুনুর ভারতে যাবার ইঙ্গিত। স্বামীর দেশই তো মেয়েদের আসল দেশ। টুনুর কিন্তু মন মানে না, ‘এই যে দেশটা নদীর কূলে-কূলে এত স্নেহমায়ার আঁচল বিছিয়ে আছে, এটা তার দেশ না? ওই যে গানে বলছে ‘মা তোর বদনখানি মলিন হলে, ও মা আমি নয়নজলে ভাসি’ — এটা তার জন্যে নয়?’ সুরেশ ডাক্তার নিজের দেশ ছেড়ে যাননি। টুনুও বুকের মধ্যে দেশের প্রতি ভালোবাসা বয়ে বড়ো হয়েছে। তার মধ্যে অন্ধ মুসলমান-বিদ্বেষ নেই। আর ভারত তার কাছে রুটির দেশ। টুনু তিনবেলা ভাত খেতে ভালোবাসে। বুড়ো পণ্ডিতমশায়ের একটা কথা তার খুব পছন্দ ‘রুটি বাঙালির পরাজয়।’ তবু হয়তো তাকে বাধ্য হয়ে স্বামীর ঘর করতে সেই দেশেই যেতে হবে। কেমন হবে সহানুভূতিহীন অমরের সঙ্গে তার প্রেমহীন দাম্পত্য? নিজের পরিবার, সদ্য স্বাধীন দেশ থেকে শিকড় ছিঁড়ে তাকে আবার কোন্ দুর্দৈবে নিক্ষিপ্ত হতে হবে কে জানে! সাত মেয়ের বিয়ের সুব্যবস্থায় ব্যস্ত সুরেশ ডাক্তারের কখনো কখনো মনে হয়েছে শুধু বিয়ে দিয়ে পরগোত্র করা ছাড়াও মেয়েদের লেখাপড়া শিখিয়ে আত্মনির্ভরশীল করার পথ কি দেখানো যায় না? টুনু কি কখনো পারবে তেমন আত্মনির্ভরশীল হতে?
তৃষ্ণা বসাক ‘চরের মানুষ’ উপন্যাসের দ্বিতীয় খণ্ড লিখবেন কিনা জানি না, তবে পাঠকের মনে নানা প্রশ্ন তোলপাড় করে। পশ্চিমবঙ্গের লোক হয়ে তিনি অনায়াস দক্ষতায় পূর্ববঙ্গের বিশেষ অঞ্চলের মুখের ভাষা আয়ত্ত করেছেন। নগর ও গ্রামের লোকযাত্রার খুঁটিনাটি বর্ণনা ছবির মতো এঁকে দিয়েছেন। একটি বিপন্ন জনগোষ্ঠীর নানাবিধ পিছুটান, দুর্বলতা, আত্যন্তিক ভয়, সংখ্যাগুরু সম্প্রদায়ের সঙ্গে অনতিক্রম্য দূরত্ব গভীর অভিনিবেশে লক্ষ্য করেছেন। সুরেশ ডাক্তার বা শোভনার মতো ব্যতিক্রমী মানুষদের গভীর মমতায় নির্মাণ করেছেন। ‘চরের মানুষ’ উপন্যাসের ক্যানভাসে নানা বিপর্যয় কাটিয়ে বাংলাদেশ নামে রাষ্ট্রটির জন্মের গৌরবময় ইতিহাস স্বাধীন দেশের পতাকায় লাল সূর্যের মতোই জ্বলজ্বল করে উঠেছে। কিন্তু কয়েক দশক পার করে আবার সে দেশে এখন স্থিতাবস্থা বিপর্যস্ত। যে বাঙালি জাতীয়তাবাদের কথা উপন্যাসে রয়েছে তা সম্ভবত আবার বিপন্ন। ধর্মীয় এবং সাম্প্রদায়িক পরিচয় আবার মানবিক পরিচয়কে দূরে ঠেলছে। সে দেশের সংখ্যালঘু হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টানদের নিরাপত্তা নিয়ে এখন শুধু ভারত নয়, আন্তর্জাতিক মহল চিন্তিত। এই পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে ‘তৃণ’ ও ‘চরের মানুষ’ দুটি উপন্যাসই বড়ো প্রাসঙ্গিক মনে হয়েছে।
- মন্তব্য জমা দিন / Make a comment
- মন্তব্য পড়ুন / Read comments
- কীভাবে লেখা পাঠাবেন তা জানতে এখানে ক্লিক করুন | "পরবাস"-এ প্রকাশিত রচনার দায়িত্ব সংশ্লিষ্ট রচনাকারের/রচনাকারদের। "পরবাস"-এ বেরোনো কোনো লেখার মধ্যে দিয়ে যে মত প্রকাশ করা হয়েছে তা লেখকের/লেখকদের নিজস্ব। তজ্জনিত কোন ক্ষয়ক্ষতির জন্য "পরবাস"-এর প্রকাশক ও সম্পাদকরা দায়ী নন। | Email: parabaas@parabaas.com | Sign up for Parabaas updates | © 1997-2025 Parabaas Inc. All rights reserved. | About Us