-
পরবাস
বাংলা ভাষা, সাহিত্য ও সংস্কৃতি
Parabaas, a Bengali webzine since 1997 ... ISSN 1563-8685 -
ছোটদের পরবাস
Satyajit Ray
Rabindranath Tagore
Buddhadeva Bose
Jibanananda Das
Shakti Chattopadhyay
সাক্ষাৎকার -
English
Written in English
Book Reviews
Memoirs
Essays
Translated into English
Stories
Poems
Essays
Memoirs
Novels
Plays
-

পুত্রবধূর চোখে গৌরী আইয়ুব এবং প্রসঙ্গত
-

বিশ্বের ইতিহাসে হুগলি নদী
-

বেদখল ও অন্যান্য গল্প
-

Audiobook
Looking For An Address
Nabaneeta Dev Sen
Available on Amazon, Spotify, Google Play, Apple Books and other platforms.
-

পরবাস গল্প সংকলন-
নির্বাচন ও সম্পাদনা:
সিদ্ধার্থ মুখোপাধ্যায়)
-

Parabaas : পরবাস : বাংলা ভাষা, সাহিত্য ও সংস্কৃতি -
পরবাস | সংখ্যা ৫০ | ফেব্রুয়ারি ২০১২ | গ্রম্থ-সমালোচনা
Share -
গ্রন্থপরিচয়: প্রেসিডেন্সি কলেজের ইতিবৃত্ত, কথায় কথায় রাত হয়ে যায়, বাংলার মাকড়সা, The Incredible Banker : ভবভূতি ভট্টাচার্য
|| কার হাতে কোন্ বাঁশি বাজে কোন্-সে অচিন সুরে ..... ||
 প্রেসিডেন্সি কলেজের ইতিবৃত্ত; ড. বিশ্বনাথ দাস; প্রকাশনালয়ঃ থীমা , কলকাতা-৭০০০২৬; প্রথম প্রকাশঃ কলকাতা বইমেলা, ২০১১ ISBN 978-81-86017-79-1
প্রেসিডেন্সি কলেজের ইতিবৃত্ত; ড. বিশ্বনাথ দাস; প্রকাশনালয়ঃ থীমা , কলকাতা-৭০০০২৬; প্রথম প্রকাশঃ কলকাতা বইমেলা, ২০১১ ISBN 978-81-86017-79-1
শ’ তিনেক পৃষ্ঠার একখানি ছিমছাম বই। চমৎকার বাঁধাই, প্রচ্ছদে এক প্রাচীন দুষ্প্রাপ্য ফোটোগ্রাফ (প্রায়-অচেনা! )। অন্দরেও বেশ কিছু দেখবার মত ফোটো। মহাফেজখানা থেকে তুলে আনা ‘পরিশিষ্ট’। মুদ্রণ-প্রমাদ প্রায় নেই। আর, সবচেয়ে বড় কথা মাতব্বরি এক্কেবারেই নেই--যেটা কিনা কলকাতার প্রেসিডেন্সি কলেজ সম্বন্ধে লিখতে বসলেই প্রায়-সকল প্রাক্তনী করে ফেলেই থাকেন (কথাটা একটু মাফি মেঙ্গেই বললাম, কিন্তু)। আর, বিষয়খানা কী? না, ‘বাঙলা তথা ভারতে আধুনিক শিক্ষার পথিকৃৎ’ প্রেসিডেন্সি কলেজের এক ইতিহাস রচনা, যার উদ্যোগ গত অল্প-কম দু’শো বচ্ছরে কোনো ব্যক্তি বা সংস্থা করেনি! যাক্, গিবনকে পেতে বিশ্বকে তো বারোশ’ বছর অপেক্ষা করতে হয়েছিল; আর বর্তমান পথিকৃৎ-উদ্যোগটি এলো কোনো ঐতিহাসিক নন এক মান্য রাশিবিজ্ঞানীর হাত ধরে, এইটেই লক্ষণীয়!
বাঙলা তথা ভারতের শিক্ষার ইতিহাসে কলকাতার প্রেসিডেন্সি কলেজের গুরুত্ব কতখানি, এ’কলেজ চিরকাল উন্নাসিকতারই জন্ম দিয়ে এসেছে কিনা, এটা শুধু উচ্চবর্ণীয় শহুরে হিন্দুদেরই প্রতিষ্ঠান থেকে গেছে কিনা—এ’সব বিতর্ক চলে আসছে, চলতে থাকবে,—থাকুক। তার জন্যে ইতিহাস লেখা বিলম্বিত হবে কেন? আর লেখক তো অতি মুন্সিয়ানায় এ’সকল বিষয়কে ছুঁয়ে ছুঁয়েও বেণী না ভিজিয়ে চলে গেছেন—এক পাক্কা ঐতিহাসিকের নৈর্ব্যক্তিকতা নিয়ে। এইটাই শ্রদ্ধা জাগায়। তবু এই নৈর্ব্যক্তিকতা সুখপাঠ্যতার মূল্যে হয়নি—এ’টি আনন্দের কথা, কারণ মাঝে মাঝেই anecdote-এর টক্ঝাল ছোঁয়ানো আছে পাঠ তর্তরে এগিয়ে নিয়ে যেতে। যেমন, অক্সফোর্ড-হার্ভাডেরও আগে, ১৮৯৭-এ’ প্রেসিডেন্সিতে সহশিক্ষা চালু হতে ‘বঙ্গবাসী’ লিখেছিল “.....এর ফলে ছাত্রছাত্রীরা নিজ মতে বিবাহ করা শুরু করিলে ছাত্রদিগের পিতারা বরপণ হইতে বঞ্চিত হইবেন...! ” বা, প্রথমযুগের কিংবদন্তী অধ্যক্ষ টনী সহকর্মী-জায়া লেডি অবলা বসুর ঝলমলে শাড়ি দেখে নিজাম-বেগম বলে ভুল করে পরে শুধরে নিয়েও “এরফলে বাড়িউলি না ভাড়া বাড়িয়ে দেয়” ভেবে ভীত হয়েছিলেন!
না, বইখানি এমন লঘু সুরে মোটেও লেখা হয়নি। মূল পাঠে লেখক বেছে বেছে উৎসাহব্যঞ্জক যে যে বিষয়গুলির গভীরতর পাঠে গেছেন, তাতে তাঁর বাঙালি পাঠকের নাড়ি বোঝার ক্ষমতা প্রমাণ করে। উদাহরণ, ডিরোজিও ও ইয়ং বেঙ্গল; সুভাষ-ওটেন বিতর্ক; হিন্দু হস্টেল, কাকা ও নকশাল আন্দোলন; সিপিএমের স্বজনপোষক বদলিনীতি ও অটোনমি বিতর্ক .........থেকে ‘ইয়ুনিভার্সিটি’। এ’বিষয়ে বিস্তৃততর আলোচনা বর্তমান প্রবন্ধের কলেবর অকারণ বাড়াবে মাত্র, তবে ১৯১৬-এ সুভাষ-বহিষ্কারের বহু বচ্ছর পরে, ১৯৪৫-এ লেখা ভগ্নহৃদয় ওটেনের “সুভাষ” কবিতাখানির সংযোজন মন কাড়ে!
বইখানিতে বেশ কিছু আকর্ষণীয় তথ্যের সংযোজন সুধী পাঠকের উৎসাহ জাগাতে পারে। যেমন,
• প্রেসিডেন্সি প্রাক্তনীদের প্রথম সম্মেলন ১৮৭৫-এ’, যতীন্দ্রমোহন ঠাকুরের মরকতকুঞ্জে (যেখানে পরে ‘রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়’ হয়েছে)। দ্বিতীয় বছরের সম্মেলেনেই কিশোর রবীন্দ্রনাথের প্রথম বঙ্কিমদর্শন ও মুগ্ধতা!
ইত্যাদি ইত্যাদি ইত্যাদি।• বেঙ্গল এঞ্জিনিয়রিং কলেজ (১৮৮০) ও (পরবর্তীকালের) গোয়েঙ্কা কলেজে (১৯০৭) স্থানান্তরিত হয়ে যাবার আগে প্রেসিডেন্সি কলেজে ছিল একটি একটি এঞ্জিনিয়রিং ও বাণিজ্য বিভাগ!
• একদম শুরু থেকে আইন বিভাগ চালু থাকলেও (বঙ্কিম, স্যর গুরুদাস এই বিভাগেরই ছাত্র ছিলেন) ১৮৮৫-তে বিভাগটি বন্ধ হয়ে যায় “বেতন বেশি ” বলে!
• ১৯১৪-এ কলেজে একটি টেনিস কোর্ট খোলা হয়। ১৯১০-২০-র দশকে রোয়িং-এ কলেজের ছাত্রদের পারদর্শিতা ছিল চোখে পড়ার মত!
• মুরারিপুকুরের অনেক আগে, ১৯০৬-নাগাদ ভগিনী নিবেদিতার মদতে (এবং স্যর জগদীশচন্দ্র ও আচার্য প্রফুল্লচন্দ্রের পরোক্ষ আস্কারায়) প্রেসিডেন্সির কেমিস্ট্রি ল্যাবে বারীন ঘোষ-হেম ঘোষেরা বোমা বানানোর নিরীক্ষা করতেন!!
• প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় থেকেই কলেজে সমরশিক্ষার ব্যবস্থা ছিল ও শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় (ইংরিজি) / বিনয় কুমার সেনের ( ইতিহাস ) মত পরবর্তিকালের কিংবদন্তী অধ্যাপকগণ ছাত্রাবস্থায় এর উৎসাহী সদস্য ছিলেন।
• ১৯৪৪-এর আগে এই কলেজে শুধু পাশ কোর্সও পড়া যেত।
• ১৯৫৫-এ, প্রেসিডেন্সি কলেজের শতবার্ষিকী অনুষ্ঠানে রাষ্ট্রপতি রাজেন্দ্র প্রসাদ ভাষণ দিয়েছিলেন বাঙলায়!
পরিশ্রমের ছাপ বইখানির সর্বাঙ্গে। এ’বই এতোদিন পাইনি কেন?—এ’আক্ষেপের পাশাপাশি লেখককে কুর্নিশ জানাতেও ছাড়ব না।
সশ্রদ্ধ।
|| আমার বলার কিছু ছিল না.......তুমি চলে গেলে....... ||
 কথায় কথায় রাত হয়ে যায়; পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়; আনন্দ পাবলিশার্স; কলকাতা-৭০০০০৯; প্রথম প্রকাশঃ ১৯৯৯; পৃষ্ঠাঃ ২৯৯; ISBN 81-7215-977-3
কথায় কথায় রাত হয়ে যায়; পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়; আনন্দ পাবলিশার্স; কলকাতা-৭০০০০৯; প্রথম প্রকাশঃ ১৯৯৯; পৃষ্ঠাঃ ২৯৯; ISBN 81-7215-977-3
মাত্র তিন মিনিট দশ সেকেণ্ড সময়, ব্যস্! ৭৮-রেকর্ডের এই দৈর্ঘ্যের মধ্যেই লিখে ফেলতে হবে গানখানি, তা সে কাব্যগুণের নিরীখে যত মহৎ সৃষ্টিই হোক্না কেন!
কিন্তু হয়েছে, তবু হয়েছে, এই দৈর্ঘ্যের মধ্যেই ঊনিশ শ’ চল্লিশ-পঞ্চাশের দশকে “মেনেছি গো হার মেনেছি” বা “কতদিন দেখিনি তোমায়” বা “চরণ ফেলিও ধীরে ধীরে প্রিয়”-র মত জনপ্রিয় গানের সৃষ্টি হয়েছে, সুর-বাণী মণ্ডিত শিল্পসুষমায় যে-সব গানকে আজও অতি উচ্চকোটীতে স্থান দিতে হবে।
আর এই সঙ্গীত পরিমণ্ডলেই সাল্কের এক সদ্য গোঁফ-গজানো তরুণ উঠে এসেছিলেন, যিনি শুধু ওই তিন মিনিটের গণ্ডি ডিঙিয়ে তিন দশকেরও বেশি সময় ধরে বাঙলা ‘আধুনিক’ (ফিল্মি ও নন্ফিল্মি) গানের গীত রচনায় রাজ করে গেছেন-‘৭৮’ থেকে ই.পি / এল.পি. ক্যাসেট হয়ে সি.ডি. যুগ পর্যন্ত! এ’বই সেই পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়েরই আত্মকথন।
কোন্কালে বিচরণ করেছেন পুলকবাবু? রবীন্দ্র-নজরুল-পরবর্তী যুগের বাঙলার কাব্যগীতির মহাকাশে তখন জ্বলজ্বল করছেন অজয় ভট্টাচার্য-মোহিনী চোধুরী-প্রণব রায়-সুবোধ পুরকায়স্থের মত দিকপালেরা। তদ্দিনে হৈ হৈ করে এসে গেছেন শ্যামল গুপ্ত-গৌরীপ্রসন্নের মত হস্তীগণ যাঁরা পরবর্তী দুই-তিন দশক ছেয়ে থাকবেন। আর এই ‘বাজারে’ সেই সদ্য তরুণ বুক পকেট থেকে চিরকুট বের করে হেমন্ত মুখোপাধ্যায়কে দিলেন পুজোর গানঃ “ও’ আকাশ প্রদীপ জ্বেলো না”!
বাকিটা ইতিহাস।
আর হ্যাঁ, এই গীতিকারই এর ত্রিশ বছর পরে লিখবেন মান্না দের পুজোর হিট গানঃ “আমায় একটু জায়গা দাও, মায়ের মন্দিরে বসি....”। এই ভার্সিটিলিটি, এই সময়ের সঙ্গে পা ফেলে চলার, সম্ভবতঃ , আরেকমাত্র উদাহরণ উর্দু/হিন্দি কাব্যগীতিতে মজরুহ সুলতানপুরী। তবু, পুলকবাবুর আক্ষেপ, এবং সঠিক আক্ষেপ, যে বাঙলায় কোনো ‘গীতিকার’ কেবল ‘গান লিখিয়ে’ হয়েই থেকে গেছেন, হিন্দি/উর্দু জগতের মত ‘কবি’-র শিরোপা পাননি। সেখানে মজরুহ বা সাহির লুধিয়ানভি বা কাইফি আজমি ‘গীতকার’-এর পাশাপাশি স্বীকৃত কবিও বটেন। কিন্তু বাঙলায় পুলক-গৌরীপ্রসন্ন কোনোদিনই বিষ্ণু-বুদ্ধদেবের সম্মান-স্বীকৃতি পাননি।
### এ’প্রসঙ্গ থাক্। ‘পরবাস’-এর এ’-প্রজন্মের অনেক পাঠক হয়ত আজ পুলক বন্দ্যোপাধ্যায় নামটির সঙ্গে তেমনভাবে পরিচিত নন। তবু আজও “ও’ দয়াল বিচার করো” বা “ক’ফোঁটা চোখের জল ফেলেছ যে তুমি ভালবাসবে” বা “রঙ্গিলা বাঁশিতে কে ডাকে” গানগুলি শুনলে তাঁদেরও মন উদাস হয়ে যায় না কি? এইখানেই কাব্যগীতির জয়! গীত-সুর-গায়ন মিলেই না এক “ললিতা গো ওকে আজ চলে যেতে বল্না” সৃষ্টি হয়—যে-সব গানের আবেদন বিশ-ত্রিশ দশক পেরিয়ে আজও সমান মনকাড়া।
কার জন্য গান লেখেননি পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়? হেমন্ত-মান্না-ভূপেন-লতা-আশা থেকে কুমার শানু-উদিত নারায়ণ থেকে কবিতা কৃষ্ণমূর্তি। আর সুরকার? বন্ধুবর সুধীন দাশগুপ্ত, নচিকেতা ঘোষ অগ্রণী হলেও সেকালে শচীন কর্তা–কমল দাশগুপ্ত যেমন পুলকের কথায় সুর বসিয়েছেন, তেমনি একালেও নামী-অনামী অনেকে। আর, বহুযুগ ধরে বাঙলা গানের সঙ্গে ওতঃপ্রোত জড়িয়ে থাকা মানুষটির কলমে অনায়াস উঠে এসেছে কত হারিয়ে যাওয়া কথা—রবিন চট্টোপাধ্যায়-সত্য চৌধুরী-যূথিকা রায়ের গল্প। আর কত তথ্য! কয়েকটা পরিবেশন করিঃ
• ফিল্মে উত্তমকুমারের প্রথম নেপথ্য-গায়ক কিন্তু হেমন্ত বা মান্না দে নন। ‘আধুনিক’-এ সেকালের এইচ.এম.ভি.র ‘লক্ষ্মী’ তরুণ বন্দ্যোপাধ্যায়।
• সত্যজিৎ রায় ও পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়ের জন্মদিন একই—২রা মে। “আমি শ্রী শ্রী ভজহরি মান্না” গানখানি সত্যজিতবাবুর এতই প্রিয় ছিল, যে ওইদিন মানিকদাকে প্রণাম জানাতে ফোন করলেই উনি পুলকবাবুকে বলতেন, “এই বছর আবার ওই রকম একখানি গান চাই কিন্তু”!
• সেকালে যূথিকা রায় রেকর্ড বিক্রিতে ছিলেন এক নম্বরে! শুধু রয়ালটির টাকায় উনি কলকাতায় বাড়ি কিনেছিলেন!
• বন্ধুবর হিমাংশু দত্তের ‘রাতের ময়ূর ছড়ালো যে পাখা’ গানটির দ্বারা ‘অনুপ্রাণিত’ হয়ে শচীনদেব বর্মণ “তুম ন জানে কিস্জহাঁ মেঁ খো গয়ে” [ফিল্মঃ সাজা ] গানটি করেন, যেটি সর্বভারতীয় হিট।
• প্রথম জীবনে এইচ.এম.ভি.-র রেকর্ড-বেচা ভ্রাম্যমাণ ফেরিওয়ালা ছিলেন তালাত মামুদ। বাঙলা গান রেকর্ড করার জন্য ‘তপনকুমার’ নাম নেন।
• উত্তমের লিপে মান্না দে-কে নেওয়ার পেছনে পুলকবাবুর প্রত্যক্ষ উদ্যোগ ছিল, কারণ এতে প্রযোজকরা গোড়ার দিকে এক্কেবারে রাজি ছিলেন না। কিন্তু “শঙ্খবেলা”-র “কে প্রথম কাছে এসেছি” বদলে দিলো চিত্রটা । তারপর “এন্টনী ফিরিঙ্গি” তে উত্তমকুমার নিজেই মান্নাবাবুকে ডেকে নেন। দুই-ই কিংবদন্তী।
### এ’ নিবন্ধের উদ্দেশ্য পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়ের গীতিকার-জীবনের মূল্যায়ন করা নয়। সেটা শ্রোতা করবেন, ‘সময়’ করবে, করেছে। তাঁর এই আত্মজীবনীখানি পড়ে যে জিনিসটা উঠে আসে তা তাঁর পেশার প্রতি তন্নিষ্ঠ নিবেদন। গোড়ার দিকে একবার প্রযোজকের সঙ্গে পাওনা-গণ্ডা নিয়ে মতবিরোধ হওয়ায় ইচ্ছে করে আল্তু-ফাল্তু গান লিখে দিলেন পুলক। সুরকার কমল দাশগুপ্তের হাতে পড়তে উনি ডেকে পাঠালেন পুলককে, বললেন, “এ’কী গান লিখেছিস তুই পুলক? শ্রোতাদের বিশ্বাসভঙ্গ করবি? তারা তো আর জানে না যে প্রযোজক তোকে ঠকিয়েছে।” লজ্জায় অধোবদন হন পুলক। সেই শিক্ষা আজীবন ধরে রেখেছিলেন। আরেকটি ঘটনা থেকেও শিক্ষা নেওয়ার আছে। বম্বেতে শচীনকর্তার কোটা ছিল বছরে দু’টি কিংবা তিনটি ছবি, ব্যস্। এরপর কোনো সম্ভাব্য প্রযোজক এক শীতসকালে ব্রিফকেস ভর্তি টাকা নিয়ে এসেছে কর্তাকে সাইন করাতে। তেলেবেগুনে জ্বলে উঠে শচীনদেব তাঁর অননুকরণীয় সিলেট্যিয়া হিন্দিতে বললেন, “নিকাল যাও, আভ্ভী নিকাল যাও। হম নেহি করেঙ্গা তুমারা পিকচার!" প্রযোজক পালাতে পথ পাননা। উপস্থিত পুলক পরে মিন্মিন্করে বললেন, “দাদা, আরেকবার ভেবে দেখলে হত না? সক্কালবেলা বাড়ি বয়ে আনা অত্তগুলো টাকা একেবার ফিরিয়ে দিলেন?” শচীনদেব এবার একটু ঠাণ্ডা হয়ে বললেন, “পাতকুয়া দেখস, পুলক? পাতকুয়া? পাতকুয়ায় জল জমতে দিতে হয়। নৈলে শুধু তুলেই নিতে থাকলে শীগগির কুয়া শুকনো হয়ে যাবে!”
এই সংযম ছিল বলেই বম্বের মত প্রতিযোগিতার বাজারে দীর্ঘ তিন দশক শচীনদেব রাজত্ব করে গেছেন!
এ’ সব-ই পুলকবাবুর জীবন থেকে নেওয়া শিক্ষা, কোনো পুঁথি থেকে নয়। এ’সকল অনুভূতিমালিকা বইখানিকে এক উচ্চতায় নিয়ে গেছে।
‘আনন্দ’-র বই। প্রোডাকশন, তাই, উচ্চমানের। সুব্রত গঙ্গোপাধ্যায়-কৃত প্রচ্ছদখানিও বেশ হয়েছে। কেবল শেষে একখানি বর্ণানুক্রমিক নামসূচি থাকার বিশেষ দরকার ছিল। এবং ওনার জীবনপঞ্জীর চুম্বক।
পুনঃ –- কেবল, গ্রন্থপাঠ শেষে, এই মানুষটি সত্যিসত্যিই তাঁর গানের এক লাইনের মত গঙ্গায় ঝাঁপ দিয়ে চলে গেলেন, —এটা ভাবতেই মনটা ভারাক্রান্ত হয়ে ওঠে। সে কি এই রোমান্টিক শিল্পীর আজকের ‘রিমেক’-এর যুগের প্রতি অভিমানে?
|| ভয় পেয়ো না, ভয় পেয়ো না, তোমায় আমি কাটবো না ||
 বাংলার মাকড়সা; ড. সুমিত চক্রবর্তী; প্রকাশনালয়ঃ পশ্চিমবঙ্গ জীববৈচিত্র পর্ষদ; কলকাতা-৭০০০৯৮; প্রথম প্রকাশঃ ২০০৯; ISBN: নেই।
বাংলার মাকড়সা; ড. সুমিত চক্রবর্তী; প্রকাশনালয়ঃ পশ্চিমবঙ্গ জীববৈচিত্র পর্ষদ; কলকাতা-৭০০০৯৮; প্রথম প্রকাশঃ ২০০৯; ISBN: নেই।
তেতাল্লিশ সংখ্যা ‘পরবাস’-এ’ আমরা ‘পশ্চিমবঙ্গ জীববৈচিত্র্য পর্ষদ’-এর এক ‘পুস্তিকা’-র কথা বলতে গিয়ে বাক্যহারা হয়েছিলাম (“বাঙলার জলার গাছ”)! এনাদের প্রকাশিত এ’গোত্রের আরও কয়েকটি বই ইতোমধ্যে আমাদের হস্তগত হয়েছেঃ “ঝোপঝাড়”, “ভোজ্য ছাতু (মাশরুম)” , “ঘাস ও বাঁশ” ইত্যাদি নিয়ে ছোট ছোট ‘পুস্তিকা’। সবক’টা-ই শ’-সওয়া শ’ পৃষ্ঠার বই। সবক’টা-ই বাংলাকে ঘিরে।
কী, নামগুলো শুনলেই পড়তে সাধ জাগে না বইগুলো?
আজ “বাংলার মাকড়সা” নিয়ে বলতে ইচ্ছে করছে। ওই দেখুন না, প্রচ্ছদচিত্রখানিই এতো চমৎকার (শ্রী হিরণ মিত্র-কৃত) যে বইটি হাতে না তুলে নিয়ে উপায় নেই। এই সিরিজের বইগুলির ধাঁচটা একই প্রকার—ডাইনের পাতায় লিখন, আর বাঁয়ে ড্রইং। আর, এই বইটির বিশেষত্ব হল, দুটিই লেখককৃত (বা, চিত্রি-কৃত)। সুমিতবাবুকে তাই দশে বিশ দিতে হয়, কারণ বিজ্ঞান-লিখিয়ে , না বিজ্ঞান-চিত্রী—কোন্ভূমিকায় উনি সফলতর তা যাচবার মত বিদ্যে আমার নেই; কেবল মুগ্ধ হয়ে গ্রন্থখানির ‘ঘ্রাণ’ নিতে পারি—আক্ষরিক ও আলংকারিক অর্থে।
ছেলেবেলার কথা মনে পড়ে গেল। স্কুলপাঠ্যে গোপাল ভট্টাচার্য মশায়ের ‘মেছো মাকড়সা’ পড়ে অবাক হয়েছিলাম। শহুরে বালকের রান্নাঘরের কোণে দেখা প্রাণীটির যে এক ‘জলীয়’ প্রজাতিও হয়ে থাকে, পরে গ্রামে বেড়াতে গিয়ে সেটি সত্যি সত্যি দেখতে পেয়ে কী লাফ-ঝাঁপঃ “বাবা, ওই দেখো, ওই দেখো—মেছো-মাকড়সা”! সেই প্রথম বইয়ের পাতা থেকে একটি জীব প্রকৃতির মস্ত ল্যাবরটরিতে লাফ মেরে চলে গেল কিনা! সেই ‘অপু’-পনার স্বাদ আজ ফের পেলাম সুমিত চক্রবর্তীর এই বই পড়তে পড়তে।
সালাম!
কোথায় যেন পড়েছিলাম, মেয়েরা মৃত্যুভয়ের চেয়েও মাকড়সাকে বেশি ভয় করে! ওটা ‘মেয়েরা’ নয়, ‘মানুষ’ হবে, কারণ মাকড়সাকে ভয় করে না এমন মনুষ্য অদ্যাবধি চোখে তো পড়লো না (সকলেই তো আর পোথালিল সেবাস্টিয়ান নন। ওনাদের কথা স্বতন্ত্র—ওনারা মহারথী!)। প্রকৃতি-মায়ের কী লীলা দেখ, দাঁত নয়, নখ নয়, ফোঁস্ নয়, কেবল ‘দর্শন’-ই আত্মরক্ষার হাতিয়ার; মাকড়সার বিষ তো ‘এহ বাহ্য’। সব মাকড়সাই তো আর ‘ব্ল্যাক উইডো’-র মত বিষাক্ত নয়, আর তারাও কেবল আত্মরক্ষার্থেই বিষ ঢালে। তারজন্যই কি মাকড়সাকে ভয় পাই—যে মাকড়সা কবে কেটে বিষ দেবে? শুধু দর্শনেই কুপোকাৎ, নই ?
কিন্তু ভয় তো আসে অজ্ঞতা থেকে, না? যাকে যত কম জানি, তাকে ততই বেশি ভয় করি। মাকড়সা সম্বন্ধীয় এই বই সেই ভয় অপনোদনেই নিয়োজিত। পরমযত্নে তরুণ লেখক আমাদের মত গোলা লোকেদের চিকণভাষায় বিজ্ঞানের কথা শুনিয়েছেন। ‘জাল বোনা’ ও ‘ভবঘুরে’—এই দুই বিভাগে বত্রিশ প্লাস আঠেরো, মোট পঞ্চাশ রকমের মাকড়সার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিয়েছেন। আর হ্যাঁ, বাঙলা নামে। cyrtophora moluccensis বা phintellavittata –র নাম আজকের দিনে ওয়েব ঢুঁড়ে বার করে নেওয়া বড় কঠিন কাজ নয়; কিন্তু এটাই যে আমাদের চেনা ‘বড় তাঁতি মাকড়সা’ বা ‘রঙিন লাফাড়ু মাকড়সা’— সেটা সুমিতবাবু না বলে দিলে জানতাম কী করে? আর হ্যাঁ, প্রতিটি প্রবিষ্টি (entry)-তেই অনিবার্যভাবে এসেছে ‘কোথায় পাওয়া যায়’, ‘পরিচিতি’ (এই অংশটিই বড়) , ‘মাপ’ ও ‘সদৃশ প্রজাতি’ এই চারটি প্রভাগ। এক এক পৃষ্ঠার মধ্যে এর চেয়ে বেশি কচ্কচালে দাঁতভাঙা পাঠ্যপুস্তক হয়ে যেত, এই পড়া/দেখার আনন্দটা থাকত না। এই পরিমিতিবোধ সম্ভ্রম জাগালো।
কিছু-না-কিছু ভুল ধরা ‘গ্রন্থ-সমালোচক’-এর ‘কর্তব্য’-এর মধ্যে পড়ে! একটা চ্যালেঞ্জ নিয়েছিলামঃ এতো বৈজ্ঞানিক নামের কচাকচির মধ্যে কিছু বানান ভুল কি আর নেই? ‘World Spider Catalog’-এ’ পঁচিশটা পর্যন্ত টেস্ট-চেক করে হার মেনে নিয়েছি। নাঃ, একটাও বানান ভুল নেই! (মোটেও কম কথা নয়।) শেষে আটচল্লিশখানি রঙিন চিত্র রয়েছে। একেকটি তো এতো সুন্দর যে পেলে ডেস্কটপ-ব্যাকগ্রাউণ্ড করে রাখি । ‘পরিশিষ্ট’-এ ৫০টি প্রামাণ্য কেতাবের এক দীর্ঘ তালিকা রয়েছে, আমা-হেন শখের পাঠকের তার সঙ্গে কোনো রিস্তা-নাতা নেই, পণ্ডিতগণ সে-সব বুঝুন। আর রয়েছে লেখকের হাতে লেখা ‘মেঠো-বই’-এর একটি পাতার নমুনা—গোটা খাতাখানিই দেখতে ইচ্ছে করছে।
সব মিলে, তাই, তরুণ-বিজ্ঞানী সুমিত চক্রবর্তীর এই ‘মেঠো-বই’ মনের মণিকোঠায় জায়গা করে নিল।
সাবাস!
পুনঃ –- আগের বইয়ে এক চমৎকার ব্লার্ব ছিল। এটায় পেলাম না, সেই আক্ষেপ রয়ে গেল।
|| এসে গেলেন রবি সুহ্ম., ভারতের শেল্ডন? ||
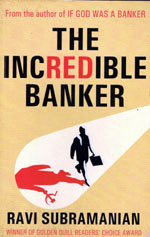 The Incredible Banker; Ravi Subramanian; Rupa & Co.; New Delhi-110002; First published 2011; ISBN: 978-81-291-1877-6
The Incredible Banker; Ravi Subramanian; Rupa & Co.; New Delhi-110002; First published 2011; ISBN: 978-81-291-1877-6
সর্বপ্রথম কেতাবটির চমৎকার প্রচ্ছদখানিতে দৃষ্টি আটকে গিয়েছিল । কথায় বলে, শিকারি বিড়ালের গোঁফ দেখলেই চেনা যায়। অতএব, ট্রাই। নতুবা, রবির এই সিরিজের প্রথম বইখানি (If God was a Banker) পড়ে যে মুগ্ধ হয়ে গিয়েছিলাম, সেকথা বলা চলে না; যদিও তরতরানির গুণে এটার মত সেটাও লেটার মার্কস পাবেই।
আর সুখপাঠ্যতার সেই গুণখানি ট্রিলজির উপান্তে এসে বেড়েছে বই কমেনি। এইটেই রবির লেখার আসল গুণ। নৈলে, যে-গোত্রের কাহানি শোনাতে বসেছেন নবীন ব্যাঙ্কার রবি সুহ্মমন্যন, তাতে পাঠশেষে মোদ্দামাল কিছু থেকে যায় না। এটা অবশ্য নিন্দার্থে বলা নয়।
ভারতীয় ভাষার মধ্যে বাঙলায় কারাজীবন নিয়ে যুগান্তকারী লিখে গিয়েছিলেন জরাসন্ধ; পুলিশ ও ক্রিমিন্যাল নিয়ে পঞ্চানন ঘোষাল। অন্য ভারতীয় ভাষায় এ’হেন specialized area নিয়ে তেমন আর লেখা হয়েছে কিনা জানিনা। তবে ভারতীয়দের লেখা ইংরিজিতে এই ব্যাঙ্কার-লেখক ব্যাঙ্কিং পরিমণ্ডল নিয়ে লিখে সাড়া ফেলে দিয়েছেন বটে, সেটা রবির বইয়ের আকাশছোঁয়া বিক্রি দেখেই মালুম। আর হ্যাঁ, এটি ‘পাস-টাইম’ লেখক হিসেবেই, পেশায় তিনি এখনও এক ব্যাঙ্কারই।
না, এই নিবন্ধে উপন্যাসখানির সামান্যও বলে দেব না, তাতে রসভঙ্গ হবে। কারণ suspense গল্পটির মূল উপজীব্য। রহস্য গল্পখানির পরতে পরতে জড়িয়ে আছে—শেষ পৃষ্ঠা পর্যন্ত। আর সে রহস্য ভেদে কোনো শার্লক হোমসের আমদানি করেননি লেখক, এটা ভালো লাগল। এই মডেলটিকে স্বাগত জানাই। আর, গল্পের পরিধি বাড়িয়ে নিয়েছেন রবি কোথা থেকে কোথায়? না, বম্বের ঝাঁ-চকচকে বিদেশি ব্যাঙ্কের আঙ্গিনা থেকে মেদিনীপুরের জঙ্গলে মাওবাদী রমরমা পর্যন্ত। মূল রহস্যখানি সামান্য কষ্টকল্পিত মনে হলেও, চরিত্র-চিত্রায়ণ বেবাক বাস্তব, তাই গ্রহণীয়। ডিটেইলের প্রতি তাঁর সজাগ দৃষ্টি শিল্পের পর্যায়ে গেছে, এটা সম্ভ্রম জাগায় । আর পরম মুন্সীয়ানায় গল্পের ক্যামেরাখানি সময়ের সারণী বেয়ে আগেপিছে করে মন্তাজের অনুভূতি এনে দিয়েছেন লেখক। তবে, নিজে ব্যাঙ্কার বলে ব্যাঙ্কিং-সম্বন্ধীয় অধ্যায়গুলিতে লেখক যতখানি স্বচ্ছন্দ, মাওবাদীদের অধ্যায়গুলোয় তত নয়—সেগুলি একটু প্রক্ষিপ্ত ও হ্রস্ব মনে হয়েছে।
বস্তুতঃ, গল্প শোনানো এক অতি উচ্চ পর্যায়ের আর্ট। এই আর্টে কালোত্তীর্ণ বলেই বাঙালি আজও, যেমন, শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়কে, মাথায় করে রেখেছে; ইঙ্গ-ভাষায় সমান্তরাল উদা. সিডনি শেল্ডন। এই আর্টে নবীন রবি সসম্মান উৎরেছেন। প্রকাশকের ঘরের লক্ষ্মী এখন রবি সুহ্মমন্যন! তাঁর উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধি কামনা করি, তাতে যদি লক্ষ্মীর পাশাপাশি সরস্বতীর আবাহনে কলমখানি আরও একটু শানিয়ে নিতে হয়, তাও।
পুঃ — তাঁর ‘কলিন্স স্কুল’-এ’ পড়ানোর অভিজ্ঞতা নিয়ে যুগান্তকারী উপন্যাস লিখেছিলেন বিভূতিভূষণঃ “অনুবর্তন” । রবির ক্ষেত্রে ডোমেইনটা ‘স্কুল’ নয়, ‘ব্যাঙ্ক’। গভীরতায় যদিও এ’লেখা ‘অনুবর্তন’-কে ছোঁয় না (এটা বাঙালি বলেই বললাম না কিন্তু)। তবু, রবি, সময় এসেছেঃ এবার এই ব্যাঙ্ক ছেড়ে বেরোনোর। নতুবা অনুবর্তন-ই কিন্তু করে যেতে হবে।
- এই লেখাটি পুরোনো ফরম্যাটে দেখুন
- মন্তব্য জমা দিন / Make a comment
- মন্তব্য পড়ুন / Read comments
- কীভাবে লেখা পাঠাবেন তা জানতে এখানে ক্লিক করুন | "পরবাস"-এ প্রকাশিত রচনার দায়িত্ব সংশ্লিষ্ট রচনাকারের/রচনাকারদের। "পরবাস"-এ বেরোনো কোনো লেখার মধ্যে দিয়ে যে মত প্রকাশ করা হয়েছে তা লেখকের/লেখকদের নিজস্ব। তজ্জনিত কোন ক্ষয়ক্ষতির জন্য "পরবাস"-এর প্রকাশক ও সম্পাদকরা দায়ী নন। | Email: parabaas@parabaas.com | Sign up for Parabaas updates | © 1997-2025 Parabaas Inc. All rights reserved. | About Us