-
পরবাস
বাংলা ভাষা, সাহিত্য ও সংস্কৃতি
Parabaas, a Bengali webzine since 1997 ... ISSN 1563-8685 -
ছোটদের পরবাস
Satyajit Ray
Rabindranath Tagore
Buddhadeva Bose
Jibanananda Das
Shakti Chattopadhyay
সাক্ষাৎকার -
English
Written in English
Book Reviews
Memoirs
Essays
Translated into English
Stories
Poems
Essays
Memoirs
Novels
Plays
-

পুত্রবধূর চোখে গৌরী আইয়ুব এবং প্রসঙ্গত
-

বিশ্বের ইতিহাসে হুগলি নদী
-

বেদখল ও অন্যান্য গল্প
-

Audiobook
Looking For An Address
Nabaneeta Dev Sen
Available on Amazon, Spotify, Google Play, Apple Books and other platforms.
-

পরবাস গল্প সংকলন-
নির্বাচন ও সম্পাদনা:
সিদ্ধার্থ মুখোপাধ্যায়)
-

Parabaas : পরবাস : বাংলা ভাষা, সাহিত্য ও সংস্কৃতি -
পরবাস | সংখ্যা ৬৬ | মার্চ ২০১৭ | গল্প
Share -
শুধু শিরোনাম : অঞ্জলি দাশ
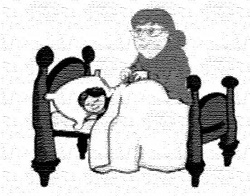
রুটিন চেক-আপ করে ডক্টর সেনগুপ্ত চলে গেছেন। সোমা মেডিক্যাল ফাইল সই করাতে এলো। কী কী ওষুধ লাগবে একবার চোখ বুলিয়ে নিয়ে পিন্টুকে এক কাপ চা দিতে বললাম। শরীরটা এখনও ঠিকমতো বশে আসেনি। ইনফ্লুয়েঞ্জার ওই এক সমস্যা। এক সপ্তাহ মেডিক্যাল লিভে বাড়িতে কাটানোর পর আজই অফিসে জয়েন করেছি। আর দু’একদিন রেস্ট নিলে হতো। কিন্তু বেশিদিন এই হোম থেকে দূরে থাকলে আমারও শান্তি হয় না। চিন্তা লেগেই থাকে। মেডিক্যাল ফাইল সরিয়ে নিয়ে আরও একটা ফাইল এগিয়ে দিলো সোমা। এটা নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসের জন্যে। আমি সাত দিন ছিলাম না, তালিকাও দীর্ঘ। সোমা খুব হিসেব করে চলে। বাড়তি কিছুই থাকে না। আমি চোখ বন্ধ করে সই করি। সেভাবেই আজও সই করতে গিয়ে একটু থমকে গেলাম। লিস্টের একেবারে শেষে ‘রুলটানা খাতা আর ডটপেন’ লেখা আছে। এটা আগে কখনো দেখিনি। অফিসিয়াল কাগজ কলম ইত্যাদি তো আলাদাভাবে আসে। তাহলে এই খাতা আর পেন! সোমা বুঝতে পেরে হাসলো।
— ম্যাডাম, রুলটানা খাতা আর ডটপেন আমাদের নতুন অতিথির জন্যে।
মনে পড়লো মিহিরবাবু ফোনে জানিয়েছিলেন, একজন বয়স্ক মহিলা এসেছে।
— খাতা-কলম দিয়ে সে কী করবে?
— আর বলবেন না, রোজ আমার কাছে কাগজ চেয়ে নিয়ে নিজের মনে কী সব লেখে।
— ইন্টারেস্টিং।
— মহিলা সত্যিই খুব ইন্টারেস্টিং। কারো সঙ্গে খুব একটা মেশে না। চুপচাপ নিজের মতো থাকে। কোনো ঝামেলা নেই।
— তুমি মিহিরবাবুকে ফাইল দুটো দিয়ে এসো, আমি চা-টা খেয়ে নিই। তারপর চলো তাকে একবার দেখে আসি।
সোমা জানলার দিকে আঙুল দেখিয়ে বললো, ওই দেখুন।
বাউন্ডারি ওয়ালের গা ঘেঁসে গোটা তিনেক আম আর দুটো কাঁঠাল গাছ। কাঁঠাল গাছ দুটোর মাঝামাঝি একটা কাঠের বেঞ্চ করা আছে। সেই বেঞ্চের ওপর বসে একটা বাচ্চাকে মুড়ি খাওয়াচ্ছে মহিলা। জানলা দিয়ে মুখের একটা পাশ দেখা গেল। এক মাথা কাঁচাপাকা চুলে একটা হাত খোঁপা বাঁধা। বয়স বোঝা গেল না।
— কোথায় পাওয়া গেল?
— শিয়ালদা সাউথ স্টেশানের সিঁড়িতে, রাত তিনটের সময় এক্সপ্রেস ট্রেনের একটা বহুকালের পুরোনো টিকিট হাতে নিয়ে বসেছিল। ডিউটিরত পুলিশকে জিজ্ঞেস করছিল, কলকাতা যাওয়ার ট্রেন কখন আসবে? তাতেই পুলিশ বুঝে গেছে কিছু গোলমাল আছে। তারপর তো এখানে।
— বাচ্চাটা কার?
— ও তো আমাদের সাবিত্রীর ছেলেটা। দুজনের খুব ভাব হয়ে গেছে।
আড়াই বছর আগে উনিশ বছরের উড়িয়া মেয়ে সাবিত্রী এখানে এসেছিল ছ’মাসের অন্ত:সত্ত্বা অবস্থায়। প্রিন্সেপ ঘাট থেকে তুলে এনেছিল পুলিশ। মেয়েটা নিজের বাচ্চাটাকে দু’চক্ষে দেখতে পারে না। একবার নাকি কান্না থামাতে পারছিল না বলে গলা টিপে ধরেছিল। অন্য মেয়েরা গিয়ে বাঁচায়। সেই থেকে অন্যদের কাছেই মানুষ হচ্ছে ছেলেটা।
চা শেষ হতে মনে পড়লো কয়েকটা জরুরি ফোন করতে হবে। সোমা দাঁড়িয়ে আছে, যাবেন ম্যাডাম, নাকি ডেকে আনবো? বললাম, ডাকতে হবে না আমি যাবো। কয়েকটা ফোন করে নিই।
সারাদিন প্রবল কাজের চাপে হোমের নতুন মেম্বারের সঙ্গে আর সাক্ষাৎ করে উঠতে পারিনি। প্রত্যেকদিন রাতে কোয়ার্টারে যাওয়ার আগে সবকিছু একবার ঘুরে দেখি। সেই রুটিনমতো ন’টা নাগাদ সোমাকে সঙ্গে নিয়ে সাত নম্বর ঘরে এসে দেখি সবাই ঘুমোচ্ছে, নতুন মহিলা নিজের বিছানায় বসে একটা পুরোনো খবরের কাগজ খুলে নিয়ে দেখছে। পাশে সাবিত্রীর ছেলে ঘুমোচ্ছে। অফিসে গোটা দুয়েক খবরের কাগজ আসে। তারি একটা হয়তো চেয়ে নিয়েছে। এ ঘরে পাঁচজন থাকে, সবাই অনেকদিনের পুরোনো। এদেরই কাছে থাকে সাবিত্রীর ছেলেটা। নতুন মহিলাকে এখানেই জায়গা দেওয়া হয়েছে। সোমাকে জিজ্ঞেস করলাম, বাচ্চাটা এর কাছে ঘুমোয় নাকি?
— গত দু’দিন ধরে তাই তো দেখছি।
কাছে গিয়ে জিজ্ঞেস করলাম, নাম কী? একবার আমার দিকে তাকিয়ে নিয়ে আবার কাগজের দিকে চোখ নামালো। বললো, সুকান্ত।
— মানে! আমি অবাক হয়ে সোমার দিকে তাকাতে সোমা হাসলো।
— ওটা সাবিত্রীর বাচ্চার নাম। ইনি দিয়েছেন নামটা। আগে তো ওকে সবাই গোবর বলে ডাকতো। এর নিজের নাম দয়াময়ী। অবশ্য এটাই আসল নাম কি না বলতে পারবো না। কারণ নাম জিজ্ঞেস করাতে তিনবার তিনটে নাম বলেছে, দয়াময়ী, রমা আর সুলতা। আমি তা থেকে দয়াময়ী লিখে নিয়েছি।
এবার চোখ তুলে হাসলো। সামনের দিকের একটা দাঁত নেই। পিঠের ওপর কোমর ছড়ানো একরাশ চুল, অধিকাংশ সাদা। চেহারায় দীর্ঘদিনের অযত্নের ছাপ, বয়স আন্দাজ করা কঠিন। ষাটের কাছাকাছি হতে পারে।
— চুল খোলা কেন? প্রথমবার উত্তর পাওয়া গেল না, আবার জিজ্ঞেস করতে কাগজের দিকে চোখ রেখেই বলল। চুল ভেজা। ভাঙা ভাঙা গলার স্বর।
কোয়ার্টারে ফিরতে ফিরতে সোমাকে জিজ্ঞেস করলাম, মাথার গোলমাল নেই তো?
— তা নেই। সব কাজই তো স্বাভাবিকভাবে করে। কিছু বললে বুঝতে পারে। ঠিক প্রশ্নের ঠিক উত্তর দেয়। তবে মাঝে মাঝে কিছু অসংলগ্ন কথা যে বলে না তা নয়। বাকি তো ওই একটা, মাঝে মাঝে কাগজ চেয়ে নিয়ে নিজের মনে কি যেন লেখে। সে জন্যেই একটা খাতা এনে দেয়ার কথা ভেবেছি। হাতের লেখা দেখে মনে হয় মহিলা যথেষ্ট শিক্ষিতা।
প্রায় এক বিঘে জায়গা নিয়ে এই ‘পথহারা’। ভবঘুরে মহিলাদের আশ্রয়। সংস্থাটা সরকারি হলেও অন্যকিছু সুহৃদয় সাহায্যও আসে স্বত:স্ফূর্ত ভাবে। সেগুলো গ্রহণ করা হয়। হোমের মেন গেট দিয়ে ঢুকেই প্রথমে বাঁদিকে আমার কোয়ার্টার। চারটে ঘর, অ্যাটাচড বাথরুম, রান্নাঘর, বাঁধানো কুয়োতলা নিয়ে পুরোনো একতলা বাড়িটা আমার খুব পছন্দের। সামনে বাঁশের বেড়া দিয়ে ঘেরা এক টুকরো বাগান। সেখানে একপাশে কিছু ফুলের গাছ। দারোয়ান যত্ন করে ফুল ফোটায়। অন্যপাশে একটা ঝুপসি আম গাছ। প্রচুর আম হয়। একজন সর্বক্ষণের কাজের লোক আছে। সে-ই আমার বাজার রান্নাবান্না সবই করে।
জমিসহ বাড়িটা একজনের দান করা। প্রায় পনের বছর আগে সরকারি উদ্যোগে এই হোম শুরু হয়। আমি এখানে জয়েন করেছি চার বছর হতে চললো। আমাকে বাদ দিয়ে আর আটজন কর্মচারি এই হোমে। কিন্তু যেকোন প্রয়োজনে সোমাই সবসময় হাজির।
সোমা আমার সঙ্গেই থাকে। ও আগে বাড়ি থেকে যাতায়াত করতো। তিন সাড়ে তিনঘন্টা লাগতো আসতে। দু’কামরার ভাড়া বাড়িতে মা আর দাদার সংসারে বৌদি আসার পর ওর থাকার সমস্যা হচ্ছিল বলে আমিই ওকে আমার কোয়ার্টারে এসে থাকতে বলেছিলাম। সপ্তাহে একদিন ছুটি, বাড়িতে যেতো। মা মারা যাওয়ার পর আর যায় না। আমার মতো সোমাও এই হোমকে খুব ভালোবাসে। মিহিরবাবু প্রথম থেকেই এখানে আছেন। ওঁর মুখে প্রায়ই শুনি, ‘আপনি আসার পর হোমের অবস্থা পালটে গেছে। এর আগে যেসব অফিসার ছিলেন, তাঁরা সবাই আর পাঁচটা সরকারি চাকরির মতো রুটিন ডিউটিই করতেন।’
আমি চেষ্টা করি এদেরকে সুস্থ স্বাভাবিক জীবনে ফিরিয়ে আনতে। এদের গা থেকে অবহেলার চিহ্নগুলো মুছে দিতে।
।। দুই ।। প্রায় মাসখানেক পরের ঘটনা। কোয়ার্টারের বারান্দায় বসে সকালবেলায় চা খাচ্ছি, কানে এলো চীৎকার চেঁচামেচি। আমি আর সোমা দুজনেই গেটের কাছে এসে দেখার চেষ্টা করলাম, সাত নম্বর রুমের সামনেই জটলা। চায়ের কাপ হাতেই সোমা দৌড়ে গেল দেখতে। ও ফিরছে না দেখে আমিও পায়ে পায়ে গিয়ে দেখি দয়াময়ী নিজের বিছানা আঁকড়ে উপুড় হয়ে আছে। সপ্তাহে একদিন ওদের বিছানাপত্র ঝেড়েঝুড়ে চাদর পালটে দেয় যে মেয়েটা, সেই বাসন্তী বকবক করছে আর সোমা দয়াময়ীকে বুঝিয়ে সুঝিয়ে ওঠানোর চেষ্টা করছে।
— কী হয়েছে সোমা?
— দয়াময়ী বিছানা তুলতে দেবে না।
— কেন?
এবার অপ্রসন্ন মুখে বাসন্তী এগিয়ে এলো, আর বলবেন না ম্যাডাম, বিছানার নিচে রাজ্যের জঞ্জাল জমিয়ে রেখেছে। তাতে হাত দিতে দেবে না।
অনেক অনুনয় করে ওকে উঠে আসতে রাজি করালাম এই শর্তে যে, কেউ তার একটা কিছুও ফেলবে না। আমার মুখের দিকে একবার দেখে নিয়ে দয়াময়ী বিছানা ছেড়ে উঠে এলো। বাসন্তী বিছানা তুলে প্রচুর ভাঁজ করা কাগজ বার করে আমার হাতে দিল। একটার ভাঁজ খুলে দেখি সেটা চিঠি--‘শ্রী চরণেষু’ দিয়ে শুরু করে মাঝে অর্থহীন কিছু শব্দ, কোথাও সংখ্যার পর সংখ্যা সাজানো। সবার শেষে ‘ইতি’ পনরই ফাল্গুন’… ..এইরকম চিঠি লেখার ধরন আমি আগে আর একজনকেও দেখেছি। দ্বিতীয় কাগজটার ভাঁজ সবে খুলেছি, সেখানেও ওই একই সম্বোধন শুরু। প্রায় ঝাঁপিয়ে পড়ে আমার হাত থেকে কাগজগুলো কেড়ে নিলো দয়াময়ী। ততক্ষণে চটপট বিছানা ঠিকঠাক করে দিয়েছে বাসন্তী।
কাগজগুলো আঁচলের নিচে ঢেকে অপরাধীর মতো মুখ করে দয়াময়ী আবার গিয়ে বিছানায় বসলো। ভালো করে তাকালাম ওর দিকে। এই এক দেড় মাস ওর চেহারায় একটা চকচকে ভাব এসেছে। ধুলো পড়ে মলিন হয়ে যাওয়া একটা ছবির ধুলো মুছে নিলে যেমন আসল ছবিটা বেরিয়ে আসে ঠিক তেমনি। অনেকগুলো ব্যাপার মিলে ওই ছবিটা যেন আমার আগে দেখা। হঠাৎ মনে হলো দয়াময়ী, রমা, সুলতা, সুকান্ত এই নামগুলো কোনো না কোনো ভাবে ওই মানুষটার জীবনে জড়িয়ে নেই তো? আর ওই চিঠি? একটু একটু করে বিস্মৃতির জলতল থেকে ভেসে উঠছে দয়াময়ীর আড়ালে দাঁড়িয়ে থাকা অন্য একজন বেভুল মানুষ, মণিদীপা। আমার মণিপিসি। মণি পিসির মায়ের নাম সুলতা আর ঠাকুরমার নাম দয়াময়ী। আর রমা সুকান্তদার মায়ের নাম।
ওই চিঠির খসড়া আমাকে পিছনে টেনে নিয়ে যাচ্ছে। ঘরে ফিরে অনেক স্মৃতির ভেতর থেকে প্রায় কুড়ি একুশ বছর আগে বিচ্ছিন্ন দু’এক টুকরো স্মৃতি উঠে এলো চোখের সামনে। সেটা আমার ছোটবেলাকার, বাংলাদেশের ঘটনা... একদিন রাত পোহানোর আগে মেঘের ডাকে ঘুম ভাঙল। বিছানায় শুয়েই টের পেলাম প্রথমে ঝিরঝিরে, তারপর ঝমঝম করে বৃষ্টি শুরু হলো, ঝরতেই থাকল। বুঝলাম আজ আর স্কুল যাওয়া হলো না। জলখাবার খেয়ে, হেমেন্দ্র কুমার রায় নিয়ে সোজা ছাদের ঘরে। সবে প্রথম পাতা উলটেছি, নিচে বাইরের দরজায় কড়া নাড়লো। এমন বৃষ্টি মাথায় করে কে এলো! কান খাড়া করে শুনতে চেষ্টা করলাম। ততক্ষণে সিঁড়িতে ছপছপ শব্দ। শাড়িটাড়ি ভিজে শপশপ করছে। তাই নিয়ে ঘরে ঢুকলো। কাঁচুমাচু মুখে বললো, একটা তুচ্ছ জিনিস চাইব দিবি?
জানি তুচ্ছ জিনিসটা কী। কেননা প্রায়ই এই তুচ্ছ জিনিসটা আমাকে দিতে হয়। কথা না বাড়িয়ে নি:শব্দে আমার একটা খাতা আর একটা কলমও এগিয়ে দিলাম। যথারীতি খাতা থেকে নিখুঁতভাবে একটা পাতা ছিঁড়ে নিয়ে চিঠি লিখতে বসলো। চেনাজানা সবাই জানে মণিপিসি প্রেমপত্র লেখে। কাকে লেখে সেটাও জানে। কাজেই আমার অসীম কৌতূহল। আড়চোখে দেখলাম শুরুটা, ‘শ্রীচরণেষু…’ এইরকম অদ্ভুত সম্বোধনের প্রেমপত্র সেই কৈশোরে বড় ধন্দে ফেলেছিল আমাকে। তখন প্রেম শব্দটা উচ্চারণ করতে ঠোঁট কাঁপে, চুম্বন শব্দটা ছাপার অক্ষরে দেখলেও বুক শিরিশির করে। সেইসময় নিয়মিত মণিপিসির এই বিচিত্র প্রেমপত্র রচনার সাক্ষী আমি তখন ক্লাস এইট। কৌতূহল একটু বেশি। কিন্তু যতই উঁকিঝুঁকি মারি ও সতর্কভাবে হাত চাপা দেয়। আঁচল আড়াল করে আমার দিকে থেকে থেকে আড়চোখে তাকিয়ে, পনেরো মিনিট ধরে চিঠি লেখা চললো। শেষটুকু দেখতে পেলাম ‘ইতি ১১ই ভাদ্র’।
চিঠি লেখা হলো, ভাঁজ হলো। এ পর্যন্ত ঠিকঠাক চলছিল। কিন্তু তারপর শুরু হলো ওর পাগলামি। সেই চিঠি দিয়ে নৌকা তৈরি হলো। আমার দিকে তাকিয়ে লাজুক হেসে বললো, আয় না মিঠি এটাকে রওনা করিয়ে আসি। গেলাম ওর পিছু পিছু। ততক্ষণে আমাদের বাড়ির সামনের নয়ানজুলি স্রোতস্বিনী। তার বুকে ভাসলো মণিপিসির প্রেমের নৌকো। ও আপনমনে বললো, যা স্রোত, ঠিক পৌঁছে যাবে। কোথাও আটকাবে না, না রে? নিশ্চিন্ত মুখ। আমিও মাথা নেড়ে সায় দিলাম। কারণ ওর কথার বিরুদ্ধে কিছু বললে আমার ওপর রেগে যাবে। মাকে গিয়ে বলবে, জানো বৌদি মিঠিটা এমন পেকেছে, ওর দ্বারা আর পাশটাশ হবে না। কিচ্ছু পড়াশুনা করে না। লুকিয়ে শুধু গল্পের বই পড়ে। তার পর উলটো পালটা বকতে বকতে বাড়ি চলে যাবে। সুতরাং আমি অন্য প্রসঙ্গে গেলাম, আচ্ছা মণিপিসি চিঠিতে ইতির পর তোমার নাম লিখলে না তো?
— ইস, তাই লিখি আর মণিদীপা ভিজে মরুক। তারপর বৃষ্টির জলে ভেসে যাক আর কি। তুই একটা গবেট। আমার মাথায় টোকা মারলো।
— ভেসে যাবে মানে?
আবার বারান্দার সিঁড়িতে গুছিয়ে বসলো মণিপিসি। যেমন করে অঙ্ক বোঝায়, সেইভাবে বোঝাতে শুরু করলো।
— একটু তলিয়ে ভাব মিঠি, আমার নামটাকে নিয়ে তোদের ওই নয়ানজুলির জল চলতে চলতে প্রথমে নদীতে, তারপর সমুদ্রে গিয়ে পড়বে। ভেবে দেখ সেই অথৈ সমুদ্রে আমার নামটা ঢেউয়ের সঙ্গে লড়াই করতে করতে সমুদ্রের তলায় ঝিনুক, প্রবাল, শ্যাওলার মাঝখানে। সেখানে না কেউ আমাকে চেনে, না আমি কাউকে চিনি। ভাব, ভেবে দেখ মিঠি, সব্বাই আমাকে দেখছে, আমার দিকে তাকিয়ে ফিসফিস করে কী সব বলছে। সেখানে হাজার চোখের সামনে আমি একা। আর কেউ নেই। নেইতো নেই...।
এবার নিজের তলপেটে হাত দিয়ে দেখায়, এখানে কিছু নেই, ঘর ফাঁকা, দেয়ালের ফটোগুলোর জায়গায় চৌকোনা ফর্সা ছাপ। দেখলেই বুকের ভেতর খাঁখাঁ করে। দেয়ালের গায়ে শুধু পেরেকের ছোট ছোট গর্ত...।
বুঝলাম শুরু হয়ে গেল। এতক্ষণে স্বাভাবিক পৃথিবী ছেড়ে মণিপিসি তার ‘নেই’-এর জগতে ঢুকে পড়েছে। মা টের পেলে আমাকে বকতে শুরু করবে, বলবেন নিশ্চয় তুই এমন কিছু বলেছিস যাতে ও বিগড়েছে। মণিপিসির হাত ধরে টানতে টানতে বললাম, চলো না ছাদের ঘরে যাই। তোমাকে একটা জিনিস দেখাবো।
— দেখানোর কিচ্ছু নেই তোর। আমার সংগে চালাকি হচ্ছে। তুই খুব শয়তান হয়েছিস।
— না না, চালাকি না। অ্যালজেব্রা, তুমি সেদিন যে ভ্যানিশিং মেথড শিখিয়ে দিয়েছিলে, সেটা কিছুতেই মনে করতে পারছি না। আর একবার বলে দেবে? এবার আর ভুলবো না।
ম্যাজিকের মতো মণিপিসির মুড পালটে গেল। বললো, চা খাওয়াবি? বললাম, মা খাওয়াবে, আমি বলে আসছি। তুমি ওপরে চলো।
প্রায় টানতে টানতে ওকে ছাদের ঘরে নিয়ে গেলাম। মণিপিসির ওই একটাই রিলিফ। অঙ্ক। দাদা বলে, ওই অঙ্কই ওর মাথাটাকে গোলমাল করে দিয়েছে। যারা অঙ্ক করতে খুব ভালোবাসে একসময় না এক সময় তাদের মাথা খারাপ হয়ে যায়। জানিস পৃথিবীর ইতিহাসে এমন অনেক উদাহরণ আছে। মণিপিসিরও সেই অবস্থা। ও তো আর পুরোপুরি পাগল নয়।
শুধু অঙ্কের কারণে মণিপিসির এই অবস্থা! কিন্তু ওই চিঠি লেখা? আমার বন্ধু তুলি বলে, ধ্যাৎ তোর দাদার যেমন কথা। আসলে লাভস্টোরি। এর মধ্যে একটা লাভস্টোরি আছে।
তুলির মুখের ভাষা ওইরকমই। শুনে শুনে আমাদের অভ্যেস হয়ে গেছে। দাদা যা-ই বলুক তুলির কথার মধ্যে লুকোনো রহস্যই আমাকে টানে। আমার উৎসাহ দেখে তুলি বলে, তোকে আমি বলবো সব কথা।
— তুই এসব কী করে জানলি?
— একটু চোখকান খোলা রাখলেই সব জানা যায়। আমি কি তোর মতো ?
— তা তুই কোথায় চোখ কান খোলা রাখলি?
— আমি সুকান্তদার কাছে ইংরেজি পড়তে যেতাম, মণিপিসি আমার হাত দিয়ে কতবার চিঠি পাঠিয়েছে সুকান্তদাকে।
চিঠির ব্যাপারটা শুনেই তুলির তথ্যের ওপর আরো বিশ্বাস জন্মায়। বুকের ভেতর শিরশিরানি টের পাই।
— তুই পড়েছিস সে চিঠি? শ্রীচরণেষু লিখতো?
— তা কি করে জানবো, চিঠি তো খামের মধ্যে। আঠা দিয়ে আটকানো খাম। আমি খুব সাবধানে সুকান্তদার মায়ের চোখে এড়িয়ে সুকান্তদাকে দিতাম। রমামাসিমা তো মণিপিসিকে দু’চক্ষে দেখতে পারতো না।
— কী করে বুঝলি?
— মণিপিসি মাঝে মাঝে ওদের ঘরে যেতো তো। কিছু জিজ্ঞেস করলে মাসিমা গম্ভীর গলায় উত্তর দিতো। তারপর মণিপিসি চলে গেলে গজগজ করতো, এহান থিক্যা বাইর হইতে পারলে বাঁচি। পোলাডার মাথা খাওনের লাইগ্যা ঘুরঘুর করে কালী।
সুকান্তদারা সবাই খুব ফরসসা। আর মণিপিসি শ্যামলা, তাই ওর সম্বন্ধে বিশেষণ।
সুকান্তদারা মণিপিসিদের বাড়ির একতলায় ভাড়া থাকতো। সুকান্তদার বাবা একটা প্রাইমারি স্কুলে মাস্টারি করতেন। সুকান্তদা ইংরেজিতে অনার্স নিয়ে বিএ পাশ করার পর চাকরির চেষ্টায় পাশাপাশি টিউশানি করতো। দাদাও যেতো সুকান্তদার কাছে ইংরেজি পড়তে। আমার জানার পরিধি এটকুই। মাঝেমধ্যে দেখেছি আমাদের বাড়ির পাশে যেখানে বারোয়ারি পুজো হয়, সেখানে সফেদা গাছের তলায় দাঁড়িয়ে মণিপিসি আর সুকান্তদা গল্প করছে। তুলির মতো সেটাকে কোনোদিন আমার ‘লাভস্টোরি’ মনে হয়নি।
একদিন শুনলাম সুকান্তদারা ভোর রাতে কাউকে না জানিয়ে ‘ইন্ডিয়া’য় চলে গেছে। তখন ওই শব্দবন্ধ প্রায়ই শোনা যেতো। মণিপিসি সেসময় এখানে ছিল না, এটুকু মনে আছে। অঙ্ক নিয়ে বিএসসি পাশ করার পর বিএড পড়তে ঢাকায় যায় মণিপিসি। সুকান্তদারা চলে যাওয়ার কিছুদিন পর মণিপিসি বাড়ি ফিরলো। অন্যবার বাড়ি ফিরেই ও আমার মায়ের সঙ্গে দেখা করতে আসতো, এবার এলো না। আমি তখন ক্লাস সিক্সে পড়ি। স্পষ্ট মনে আছে সেই সময় মণিপিসির সাংঘাতিক কিছু অসুখ করেছিল, কেননা ওকে হাসপাতালে ভর্তি করতে হয়েছিল। তখন কদিন ধরে চেনাজানাদের মধ্যে কেমন একটা থমথমে ভাবে, চারপাশে কানাঘুষো, ফিসফাস।
এইসব দেখে আমি খুব ঘাবড়ে গিয়েছিলাম। তুলিকে যে কিছু জিজ্ঞেস করবো, তখন সে সাহসও হতো না। সেই সময় স্কুলের স্পোর্টস, পড়াশুনা এইসব নিয়ে মেতে থাকতে থাকতে ব্যাপারটা মাথা থেকে বেরিয়ে গিয়েছিল। মাঝে মাঝে শুধু মনে হতো মণিপিসি আর আসে না তো।
ডাক্তারবাবুর সুশ্রী শ্যামলা মেধাবী মেয়েটিকে পাড়ার সবাই খুব ভালোবাসতো। আমার মায়ের সঙ্গেও ওর খুব বন্ধুত্ব ছিল।
মায়ের কান বাঁচিয়ে তুলির টুকরো টুকরো তথ্য আমার মধ্যে একটা আলোছায়াময় গল্প রচনা করলো মণিপিসিকে নিয়ে। তখন যার কিছুটা বুঝি কিছুটা অধরাই থেকে যায়। সেই বয়সে অনেক কিছুই বোধের অগম্য। তুলি আমাদের তুলনায় একটু বেশিই অকালপক্ক ছিল।
তুলি ইঙ্গিতে বলেছিল, জানিস তো পেট ফুলে গিয়েছিল মণিপিসির।
যেটা একজন অবিবাহিতা মেয়ের পক্ষে চরম লজ্জা আর অসম্মানের, এটুকু বুঝতাম।
বলেছিল, আত্মহত্যা করবে বলে ধুতরো ফুলের বীজ খেয়েছিলো মণিপিসি।
যে-কারণে ওকে হাসপাতালে ভর্তি করতে হয়েছিল। সেখানে তার লজ্জার কারণ মুক্ত করা হয়েছিল। বাড়ি ফিরে আসার পর নিজের পেটে হাত বোলাতো আর বলতো, নেই। সুকান্তদাদের ফাঁকা ঘরে গিয়ে চুপচাপ বসে থাকতো।
মণিপিসি যে আর মায়ের সঙ্গে ঘন্টার পর ঘন্টা গল্প করতে আসে না, বা পুজোর সময় বারোয়ারি পূজোর মণ্ডপে ফল কাটতে বা পদ্মের কলি ফোটাতে আসে না সেটা গা সওয়া হয়ে গেল। তারপর কিছুদিন বাদে আবার একসময় আসতেও শুরু করলো মায়ের কাছে। আমাকে মাঝে মধ্যে অঙ্কও দেখিয়ে দিতে লাগলো। কিন্তু তবু মনে হতো সব কিছু পালটে গেছে। মণিপিসি যেন সেই আগের মানুষটি নেই। আচরণ স্বাভাবিক নয়। কিছু একটা বলতে বলতে অন্যমনস্ক হয়ে যায়, পারম্পর্যহীন কথা বলে। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয়, অঙ্ক বোঝাতে বললে তখন আবার সেই আগের মণিপিসি। সব অঙ্ক মিলিয়ে দেয়। মেলাতে পারেনি শুধু নিজের জীবনের অঙ্ক।
আজ মনে হলো পৃথিবীটা সত্যিই গোল। নাহলে আমিই বা আমার সমবায়ের চাকরি ছেড়ে এই হোমে জয়েন করবো কেন, আর সেখানেই কেন আশ্রিত হয়ে আসবে মণিপিসি। যদিও তখনও আমি পুরোপুরি শিওর হতে পারছিলাম না ও মণিপিসি।
।। তিন ।। হোমের মেয়েদের মধ্যে যারা ঠিকঠাক নিজের ঠিকানা বলতে পারে, তাদের বাড়িতে চিঠি দিয়ে যোগাযোগ করার চেষ্টা করি আমরা। বারবার। অধিকাংশ ক্ষেত্রে কোনো উত্তর আসে না। বুঝতে পারি পরিজনের কাছে এরা অবাঞ্ছিত। ঘর এদের প্রতি বিমুখ, তাই এরা পথের আশ্রয়ে। দিশাহীনভাবে ঘুরে বেড়ায়।
মণিপিসির ক্ষেত্রেও কি তাই? ভাবতে কষ্ট হয়। তখন সম্ভবত মানসিক রোগের চিকিৎসার তেমন ভালো ব্যবস্থা ছিল না। হয়তো সেভাবে চিকিৎসা হয়নি, কিন্তু ওর পরিবার তো ওকে অবহেলা করেনি কোনোদিন। ভালোবাসা দিয়ে আগলে রাখতো। হতে পারে বাবা মা আর বেঁচে নেই, কিন্তু ওর দাদা-বৌদি তো ছিল। ও কী করে পথের আশ্রয়ে এসে দাঁড়ালো?
মাঝে মাঝে আমার কোয়ার্টারে ডেকে আনি। পুরোনো দিনের কথা মনে করিয়ে দেয়ার চেষ্টা করি। মণিদীপাকে খুঁজে পেতে সাহায্য করি। ও উদাসীনভাবে শোনে। কোনো রেসপন্স করে না। একদিন সোমা একটা কাগজে কীসব হিসেব লিখে রেখে উঠে গেছে। দেখি, মণিপিসি কাগজটার দিকে লক্ষ্য করতে করতে মুখ টিপে হাসছে। জিজ্ঞেস করলাম, কী ব্যাপার? কোনো উত্তর না দিয়ে কাগজটা টেনে নিয়ে কলম দিয়ে হিসেবটা ঠিক করে দিলো। এরপর থেকে সোমা ইচ্ছে করে টুকটাক কিছু হিসেবপত্তর ওকে করতে দেয়। ও খুব উৎসাহ নিয়ে নির্ভুল সেটা করে দেয়। কিন্তু বারবার ঠিকানা জানতে চাওয়ার পর ও বারাসাত আর খুলনা মিলিয়ে এমন একটা ঠিকানা বলে, যার কোনো অর্থ হয় না। আসলে ওর ভাবনাগুলো এলোমেলো হয়ে গেছে। কোনোটার সঙ্গে কোনোটা জুড়তে পারে না। কোনো স্মৃতি নেই, কিছু নাম সম্বল ওর।
অগত্যা নিজে উদ্যোগী হয়ে দুটো কাগজে বিজ্ঞাপন দিলাম। কেউ খোঁজ নিতে এলো না। একমাস পরে আবার দিলাম, যোগাযোগের জন্যে হোমের নম্বরের পাশাপাশি আমার মোবাইল নম্বরও দিলাম এবার। কেননা মণিপিসি আমার ব্যক্তিগত ইস্যু হয়ে দাঁড়িয়েছে। না, এবারেও কোনো সাড়া পাওয়া গেল না। পনরদিন পর আরও একবার, এবং এই শেষবার। তৃতীয় বিজ্ঞাপন বেরোনোর পরেও এক দেড়মাস কেটে গেছে। অগত্যা হাল ছেড়ে দিয়ে নিজেই চেষ্টা করি ওকে যতটা ভালো রাখা যায়। প্রায় প্রতিমাসেই এরকম বিজ্ঞাপন দিই আমরা। গত পরশুও অন্য একটা মেয়ের ব্যাপারে বিজ্ঞাপন গেছে কাগজে।
দুপুরবেলা লাঞ্চ করতে কোয়ার্টারে এসেছি, দারোয়ান এসে খবর দিলো, ম্যাডাম এক ভদ্রলোক দেখা করতে চান আপনার সঙ্গে।
— আধঘন্টা অপেক্ষা করতে হবে। ভিজিটরস রুমে বসাও।
ভাবলাম, যাক একটা মেয়ের অন্তত গতি হলো।
মিনিট কুড়ি পর অফিসে গিয়ে পিন্টুকে বললাম ভদ্রলোককে ডেকে আনতে। ভদ্রলোক কুন্ঠিত পায়ে ভেতরে ঢুকলেন।
— বসুন। অনেকক্ষণ অপেক্ষা করতে হলো।
— না, না। আমি তো অসময়ে এসেছি। আজ ট্রেনটা প্রায় তিনঘন্টা লেট ছিল।
— আপনি থাকেন কোথায়?
— জলপাইগুড়ি।
চেয়ার টেনে বসার আগে ভদ্রলোক নিজের ব্যাগ খুলে একটা খবরের কাগজ বার করলেন। হাত বাড়িয়ে কাগজটা নিলাম। এ তো একমাস আগের কাগজ, তার মানে… বুকের ভেতর ছাঁৎ করে উঠলো। এবং এতক্ষণে এই প্রথম ভালো করে তাকালাম ভদ্রলোকের দিকে। উজ্জ্বল রং, মাথায় সামান্য টাক, চোখে সুন্দর কালো ফ্রেমের চশমা, সব মিলিয়ে চেহারায় মার্জিত স্বাচ্ছন্দ্যের ছাপ। কে ইনি? মণিপিসির দাদা, মানে অরিন্দমকাকু? মনে করতে চেষ্টা করলাম প্রায় কুড়ি বছর আগের অরিন্দমকাকুর চেহারাটা। আমি যেহেতু মনেপ্রাণে চাইছিলাম মণিপিসির আপনজন কেউ আসুক অকে ফিরিয়ে নিতে, তাই আমার চোখে আর স্মৃতির সমঝোতায় মুখ দিয়ে সানন্দে বেরিয়ে এলো অরিন্দ্মকাকু, চিনতে পারছো আমি অনন্যা, মানে মিঠি... উল্টোদিকের মানুষটি আরো সঙ্কুচিত হয়ে মাঝপথে আমাকে থামিয়ে দিলেন, আমি সুকান্ত ঘোষ।
আমার সামনে যেন বজ্রপাত হলো। মুহূর্তে নিজেকে গুটিয়ে নিয়ে ফরমাল হলাম, সরি। বলুন কেন এসেছেন?
— আমাকে আপনি হয়তো মনে করতে পারবেন না। আমি যখন এখানে চলে আসি, আপনি তখন অনেক ছোট। আপনার দাদা অনির্বাণ আমার কাছে পড়তে আসতো।
— এখানে কেন এসেছেন?
— মণিদীপার সঙ্গে একবার দেখা করতে চাই।
— কেন?
— ওর সঙ্গে একবার একটু কথা বলতে চাই।
আমার ভেতরটা বিতৃষ্ণায় ভরে আছে। তবু নিজেকে সংযত করলাম। ভেতরে ক্ষীণ আশা, সুকান্তদাকে দেখে মণিপিসির যদি কোনো রিঅ্যাকশান হয়। ওর বিভ্রান্তির উৎসে যে মানুষটি, তাকে দেখে যদি ও নিজেকে খুঁজে পায়।
— মণিদীপার ব্যাপারে কিছু জানেন আপনি?
একটু চুপ করে থেকে সুকান্তদা বলল, কিছুটা শুনেছিলাম আমার এক বন্ধুর কাছে।
আবার কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে স্বগতোক্তির মতো করে বললেন, একটা পারিবারিক সঙ্কটের কারণে কাউকে কিছু না জানিয়ে আমাদের চলে আসতে হয়েছিল দেশ ছেড়ে। সেসব আপনাকে বোঝানো যাবে না। কিন্তু একটু স্থিতিশীল হওয়ার পর মণিকে অনেকবার চিঠি দিয়েছি। অনেক অনেকবার।
— আপনার চিঠি পড়ার মতো অবস্থা ওর ছিল না।
— হ্যাঁ শুনেছি, একটু মাথার গোলমাল হয়েছিল।
— আর কিছু?
— আমার বন্ধু বলেছিল, মণি নাকি সুইসাইড করতে গিয়েছিল...
আমি বুঝতে চেষ্টা করছিলাম আর কতটা জানে সুকান্তদা। কিছু বলছে না, টেবিলের ওপর কনুইয়ের ভর রেখে মুঠো করা হাতের ওপর মুখ রেখে মেঝের দিকে তাকিয়ে আছে। আমার মনে হচ্ছিল এসেছে যখন মণিপিসির কথা ভেবে, তখন সবটা তার জানা দরকার।
— মনিপিসি কনসিভ করেছিল, আপনি জানতেন?
এবার বিমূঢ়ের মতো আমার দিকে তাকালো সুকান্তদা। আমি সাবলীলভাবে কথাটা বলতে পারলেও ওর চোখ থেকে চোখ সরিয়ে নিলাম। মনে হলো ঘটনাটা ওঁর অজ্ঞাত হলেও খুব বিস্মিত নয়। আমার মনে হলো মণিপিসি হয়তো চিঠিতে না লিখে কাছে এসে ব্যাপারটা জানাতে চেয়েছিল। তখন ওইরকম একটা ঘটনা খুব সহজ ব্যাপার ছিল না।
— নিজের স্বপক্ষে বলার মতো কিছু নেই আমার, আমি জানি। শুনেছিলাম মণির মা-বাবা ওদেশেই মারা গেছেন। ওর দাদা বারাসাতে থাকে। আমি অনেক চেষ্টা করেছি ওদের ঠিকানা জোগাড় করতে। পাইনি।
— বিজ্ঞাপনটা তো অনেকদিন আগে থেকে বেরোচ্ছিল… এটা থার্ড টাইম।
— আমি আগে দেখিনি। এটাই প্রথম চোখে পড়েছে। কাগজটার দিকে ইশারা করলো।
— এটাও তো প্রায় দেড় মাসের ওপর হয়ে গেল…
— কী করব ভেবে ঠিক করতে পারছিলাম না।
সোমাকে বললাম মণিপিসিকে ডেকে আনতে। সোমা বেরিয়ে যেতে এতক্ষণে সুকান্তদা বেশ দৃঢ়তার সঙ্গে বলল,
— আমি এখান থেকে ওকে নিয়ে যেতে চাই।
— কিন্তু কেন?
নিজের কানেই রূঢ় আক্রমণাত্মক শোনালো নিজের কন্ঠস্বর। সামলে নিয়ে বললাম, এভাবে চাইলেই তো নিয়ে যাওয়া যায় না। আপনাকে তো প্রমাণ দিতে হবে যে ওর নিজের লোক আপনি।
অসহায়ের মতো তাকালো সুকান্তদা।
— আর শুধু আপনি প্রমাণ দিলে হবে বা, মণিদীপা যদি আপনাকে নিজের লোক বলে স্বীকার করে, তবেই… দেখুন। আরও কথা আছে, ওকে নিয়ে যেতে যে চাইছেন, আপনার পরিবারের ডিটেলস তো জানতে হবে আমাকে। আপনি কী করেন?
একটা স্কুলে পড়াতাম। গত বছর রিটায়ার করেছি। মা মারা গেছেন, বাবা আছেন। আমার সঙ্গে থাকেন।
— স্ত্রী, ছেলেমেয়ে।
— নেই।
— নেই কেন?
— বিয়ে করিনি। পরিবারকে দাঁড় করিয়ে দিতে দিতে অনেকটা সময় চলে গেছে। নিজের কথা ভাব হয়নি।
মনে পড়লো ওরা অনেকগুলো ভাইবোন মিলে দুটো ঘরে থাকতো। একচিলতে বারান্দায় মাদুর পেতে বসে ছাত্র পড়াতো সুকান্তদা।
মণিপিসিকে নিয়ে ঢুকলো সোমা। পিছনে পিন্টুর হাতে এক কাপ চা আর দুটো বিস্কুট। এই ক’মাসে মণিপিসির চেহারা অনেক পালটে গেছে। হলুদ পাড়ের সাদা শাড়িটা বেশ পরিপাটি করে পরে আছে। চোখে প্রবলেম হচ্ছিল বলে ওকে চশমা দেওয়া হয়েছে। নির্ণিমেষে তাকিয়ে আছে সুকান্তদা। চোখ একটু সজল কি? হয়তো তা নয়, আমার ভাবতে ভালো লাগছে বলে মনে হচ্ছে।
— ইনি তোমার সঙ্গে দেখা করতে এসেছেন। দেখো তো চেনো কি না।
মণিপিসি মাথা নাড়লো, চেনে না। তারপর হাত তুলে নমস্কার করলো। সুকান্তদা ধরা গলায় ডাকলো, মণি!
ওই ডাকে কোনো প্রতিক্রিয়া দেখা গেল না। জানালার সামনে সরে গিয়ে ও ব্যস্ত হয়ে নিজের ঘরের দিকে উঁকি দিলো, তারপর আমার দিকে তাকিয়ে অনুমতি নেওয়ার সুরে বললো, --সুকান্ত একা আছে, আমি যাই? ওর শরীরটা ভালো নেই, জ্বর হয়েছে।
বেরিয়ে গেল। হতভম্ব হয়ে আমার দিকে তাকালো সুকান্তদা। বললাম, পুরোনো মানুষগুলো ওর মন থেকে মুছে গেছে, শুধু কিছু নাম এখনও জড়িয়ে আছে ওকে। নাম দিয়ে কাউকে আইডেন্টিফাই করতে পারে না। আপনি আসুন।
— আমি যদি আবার আসি?
— ইচ্ছে হলে আসবেন। আপনি চা টা খেলেন না?
উত্তর না দিয়ে ক্লান্ত হতাশভাবে উঠে দাঁড়ালো সুকান্তদা।
অলংকরণ (Artwork) : অলংকরণঃ অনন্যা দাশ - এই লেখাটি পুরোনো ফরম্যাটে দেখুন
- মন্তব্য জমা দিন / Make a comment
- মন্তব্য পড়ুন / Read comments
- কীভাবে লেখা পাঠাবেন তা জানতে এখানে ক্লিক করুন | "পরবাস"-এ প্রকাশিত রচনার দায়িত্ব সংশ্লিষ্ট রচনাকারের/রচনাকারদের। "পরবাস"-এ বেরোনো কোনো লেখার মধ্যে দিয়ে যে মত প্রকাশ করা হয়েছে তা লেখকের/লেখকদের নিজস্ব। তজ্জনিত কোন ক্ষয়ক্ষতির জন্য "পরবাস"-এর প্রকাশক ও সম্পাদকরা দায়ী নন। | Email: parabaas@parabaas.com | Sign up for Parabaas updates | © 1997-2025 Parabaas Inc. All rights reserved. | About Us