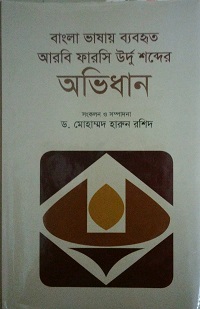 বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত আরবি ফারসি উর্দু শব্দের অভিধান---সংকলন ও সম্পাদনাঃ ড. মোহাম্মদ হারুন রশিদ; বাংলা একাডেমি ঢাকা; প্রথম প্রকাশঃ জ্যৈষ্ঠ ১৪২২ (মে ২০১৫); ISBN: 984-07-5287-1
বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত আরবি ফারসি উর্দু শব্দের অভিধান---সংকলন ও সম্পাদনাঃ ড. মোহাম্মদ হারুন রশিদ; বাংলা একাডেমি ঢাকা; প্রথম প্রকাশঃ জ্যৈষ্ঠ ১৪২২ (মে ২০১৫); ISBN: 984-07-5287-1
নাহ্, পরীক্ষায় এমন প্রশ্ন এলে নির্ঘাৎ ফেল করতুম। হ্যাঁ, বাঙলায় ডাহা ফেল!
ব্যুৎপত্তি নির্ণয় করঃ
ছত্র, ছ্যাবলা, তাক, পলক, আসবাব, দোয়াত, হুঁকো, মেথর, স্যাকরা, সাবেক, রবি ...
কী সব শব্দ রে বাবা! ছ্যাবলা, হুঁকো তো দেশি শব্দ বলে মনে হয়। রবি, সাবেক, সাবালক মনে হয় তৎসম ...
এই প্রকার নানান ‘অজানা’ শব্দ ঢুঁড়ে ঢুঁড়ে চলিঃ জমি, মিহির, দ্বার, আবীর, রায়, মোছা, মামা, ছবি ...
কী বললেন, শব্দগুলি অজানা নয়? সবই চেনা? তাহলে আর ফেল মারার প্রসঙ্গ তুললুম কেন? জানতুম না যে ‘ছত্র’ শব্দটি এসেছে আরবি ‘ছতরুন’ থেকে; বা ‘রবি’ (শস্য) এসেছে আরবি ‘রবি’ (বসন্ত) থেকে, ‘বিদায়’ এসেছে ‘বিদা’ [আ.] থেকে, দৌড় [আ.দওর], ‘ময়না’ (তদন্ত) [আ. ‘মুআয়িনহ্’] ‘সাবেক’ [আ. সাবিক্ব] বগর বগর...।
যেকোনো জীবন্ত ভাষা যে বহতা নদীর মত, গতিপথে তার নানান শব্দ এসে মেশে ও তাকে পুষ্ট করে করে তোলে---এসব কথা জানা। কিন্তু সেই পুষ্ট ভাষা খুঁড়ে সেই সেই মিশে যাওয়া শব্দাঞ্জলিগুলি ঝেড়েবেছে রাখা ও চিনিয়ে দেওয়া প্রকৃত ভাষাবিজ্ঞানীর কাজ।
মান্য হিসেবমত, সেই একাদশ শতাব্দী থেকে ক্রমে ক্রমে আজকের রূপ পাওয়া বাঙলাভাষার হাজার পঁচাত্তর শব্দের ভাণ্ডারে প্রায় নয় হাজার (১২%) বিদেশি শব্দ মিশে রয়েছে---তার বেশিরভাগই পঃ এশিয় ভাষা আরবি-ফার্সি। এবং ঐ মিশে থাকাটা ‘পইপই’ ‘সন/সাল’ ‘শাকসবজি’ বা ‘তাক’-এর মত। অর্থাৎ, এমনই সে মিশে যাওয়া যে চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে না দিলে সনাক্তকরণ মুশকিল। এবং এখানেই এক ‘আরবি-ফার্সি’-বঙ্গাভিধানের প্রয়োজন।
বস্তুতঃ, বাঙলাভাষার প্রথম মুদ্রিত অভিধানখানি বৈদেশিক ভাষা নিয়েই। ১৭৪৩ খৃ. লিসবন থেকে বাঙ্গালা-পর্তুগীজ শব্দকোষ ছেপে বেরোয় রোমান হরফে। এর ত্রিশ বছর পরে যে অভিধানের সন্ধান পাওয়া যায় সেটি ‘বাঙলা-ফার্সি শব্দকোষ’ (১৭৭৪ খৃ.)। কিন্তু এরপর সারা ঊনবিংশ-বিংশ শতাব্দী জুড়ে সেই মোহন ঠাকুর-উইলিয়ম কেরি-রামকমল সেন থেকে ১৯৯৯-এ প ব বাংলা আকাদেমি নির্মিত অভিধানমালার মধ্যে কাজী আবদুল ওদুদ ও আচার্য মু. শাহিদুল্লাহ্ ভিন্ন আর কেউ বাঙলাভাষায় আরবি-ফার্সি শব্দের প্রাপ্য গুরুত্ব দিয়েছেন বলে মনে পড়ে না (এক ব্যতিক্রম ছিল কাজী ওয়াজেয়উদ্দীন আহমদ প্রণীত ‘মক্তব অভিধান’, ১৯২৩), অন্ততঃ কলিকাতা-কেন্দ্রিক পশ্চিম বাংলায়। ঢাকা-কেন্দ্রিক পুববাংলায় অবশ্য হিলালীসাহেব, হরেন্দ্র পাল মহাশয় বাংলায় আরবি-ফার্সি শব্দের প্রামাণ্য অভিধান রচেছেন। রফিকুল হক-সাহেবের এ’হেন চমৎকার কোষখানি পাঠাগারে পেয়েছি, কিন্তু কিনতে গিয়ে জানি, বর্তমানে ছাপা নেই, অনুপলব্ধ। তাই বইমেলা ঢুঁড়ে রশিদ-সাহেবের আলোচ্য কোষখানির ক্রয় ও মুগ্ধতা।
ড. মোহাম্মদ হারুন রশিদ সাহেব ‘বাংলা একাডেমি ঢাকা’-র মহাপরিচালক, এক মান্য ভাষাবিজ্ঞানী। বহুব্যবহৃত বিপুলকলেবর ‘ব্যবহারিক বাংলা অভিধান’-এরও তিনি অন্যতম স্থপতি ছিলেন। কিন্তু কেবল আরবি-ফার্সি শব্দের খোঁজে এক সুঠাম অভিধানের প্রয়োজনে এই কোষখানি যা লিখেছেন ... ঐ ... মস্তকোপরি রাখার মত।
চারিসহস্র আরবি, সাড়ে চারহাজার ফার্সি ও শতখানিক উর্দু শব্দ স্থান পেয়েছে বর্তমান অভিধানখানিতে। মূল ভুক্তি(entry)টি মোটা টাইপে, তারপর শব্দখানির তিন-চারটি অর্থ ১ ২ ৩ করে করে দেওয়া রয়েছে। এরপর বন্ধনীর মধ্যে কোনো সাহিত্যিক উদ্ধৃতি বহুক্ষেত্রেই দেওয়া আছে। তারপর উৎপত্তিঃ আ. ফা. হি/উ, এবং আরবি/ফার্সি হরফে শব্দটি লেখা। গড়গড় করে এমনিই পড়ে চলে যাওয়া যায় অভিধানখানি। চমৎকার!
না, হোঁচট আছে। মনে। প্রথমেই যেখানে ঠোক্কর সেটা হলঃ
আচ্ছা, ‘উর্দু’ শব্দ বলে আদৌ কিছু হয় নাকি? উর্দুভাষা অবশ্যই এক অসাধারণ সুললিত কাব্যিক ভাষা, এবং শত প্রতিশত ভারত-উপমহাদেশীয় ভাষা। উর্দুর ক্রিয়াপদ পুরোপুরি হিন্দিরই (প্রাকৃত)। কিন্তু তার শব্দাবলী তো প্রায় পুরোটাই আরবি-ফারসি, কিছু আছে হিন্দি (মূলে সংস্কৃত)। তাই খাঁটি উর্দু শব্দ বলে কিছু হয় কি? তাই, অভিধানখানির শিরোনামে আরবি-ফারসি যখন রয়েইছে, ফের ‘উর্দু’ শব্দ বলে পৃথক চিহ্ণিতকরণ বিভ্রান্তিকর। এটাও লক্ষণীয়, শহিদুল্লাহ্-সাহেব (১৯৫৮), হিলালি-সাহেব (১৯৬৭) বা শামছুল হক ছিদ্দিকী-সাহেব (২০০৮), অতীন্দ্র মজুমদার-মশায়ের (২০১২) এ’গোত্রের কোনো অভিধানেই কিন্তু ‘উর্দু’ শব্দটি শিরোনামে অন্তর্ভুক্ত নয়।
রফিকুল হক-সাহেবেরটি ব্যতিক্রম। বর্তমান অভিধানটি সম্পূর্ণ ঢুঁড়েও খাঁটি উর্দুশব্দের রেফারেন্স কিন্তু একটিও পাচ্ছি না, প্রায় সর্বত্রই হি/উ। বলবেন, বলছ কী হে? তবে যে ইয়া মোটা মোটা উর্দু-অভিধান বেরোয় ... উর্দুশব্দই নেই তাতে? আছে, আছে, কিন্তু সে-সকল শব্দই হয় আরবি নয় ফার্সি (কিছু হিন্দি)-উদ্ভুত। আজকের এই বাঙলা অভিধানটিতে সেই সেই আরবি-ফারসি শব্দ যখন সেই সেইভাবেই পাচ্ছি, সেখানে ‘উর্দু’ শব্দ বলে আলাদা করে আর কী থাকতে পারে? [আচ্ছা, স্যর, শিরোনামের বানানে আরবি হল, ফারসি হল, বেশ। কিন্তু উর্দুর বেলায় রেফ্ কেন?]
দ্বিতীয় প্রসঙ্গঃ তুর্কি শব্দ। আরবি-ফার্সির মত অত না হলেও বাঙলাভাষায় বেশ কিছু তুর্কি শব্দ তো অনায়াসে মিশে রয়েইছে। যেমন, ‘বেগম’ শব্দটি এই অভিধানে নেই, থাকার কথাও নয়, কারণ এটি একটি তুর্কিশব্দ (‘বাদশা’ কিন্তু ফার্সি শব্দ। আছে।), এবং ঘোষণামত অভিধানটিতে তুর্কির স্থান নেই। ‘বাবুর্চিখানা’ রয়েছে এখানেঃ তুর্কি শব্দ ‘বাবুর্চি’ ও ফার্সি ‘খানহ্’-র মিলে। ‘বাবা’ আরেকটি তুর্কিশব্দ, ঢাকার ‘ব্যবহারিক অভি.’-তে তাই আছে; কিন্তু, হারুন রশিদসাহেব এখানে একে ফার্সি বলেছেন। দ্বিমত পোষণের ভিক্ষা মাঙি।
তৃতীয় প্রসঙ্গঃ বিতর্কিত শব্দসূত্র। পালকি, ছোঁয়া, ছবি, গোঁড়া, নাম/নামী, দ্বার, আবীর, মিহির, শিরোনাম ইত্যাদি ৫৭-খানি শব্দ এ’অভিধানে পাওয়া যাচ্ছে যাদের তৎসম-উদ্ভব সর্বজ্ঞাত, কিন্তু এখানে তাদের (বিতর্কিত?) আ/ফা উদ্ভবের উল্লেখই রয়েছে, সংস্কৃতজটি নয়। উদা.
| শব্দ | তৎসম উৎপত্তি | আ/ফা উৎপত্তি (যা এ’অভিধানে লিখিত) |
| ছোঁয়া | সং ছুপ্+বাং আ | হি/উ. ছুনা |
| ছ্যাবলামি | সং চপল | আ. সিফালাহ্ |
| নাম/নামী | নামন্ | ফা. নাম |
| দ্বার | দ্বারি + অ | ফা. দার |
| আবির | সং. অভ্র হি. অবীর | আ. অবীর |
| মিহির | মিহ্+ইর | ফা. মিহির |
| শিরোনাম | শিরস্+নামন্ | ফা. সর্নামহ্ |
এই নয় যে তৃতীয় স্তম্ভের উৎপত্তির উল্লেখ ভ্রান্ত। কিন্তু এই এই শব্দগুলির যে সংস্কৃতজ উদ্ভবও মান্য, সেটা এক অভিধানকারের নৈর্ব্যক্তিকতায় উল্লেখনীয় ছিল।
কিছু তথ্যগত বিচ্যুতি/বিতর্ক উল্লেখ্যঃ
(১) এককালে পশ্চিমা হিন্দুরমণীদের দ্বারা পালিত ‘জহরব্রতে’র সঙ্গে ফার্সি ‘জহর’ (গরল, বিষ) শব্দ সম্পর্কহীন। এ’শব্দ ‘জী/জৌ’ (জীবন-অর্থে) ও ‘হর’ (হরণ) মিলে হয়েছে। বিষপানে কদাচ এ’হেন প্রাণত্যাগ করা হত না, হত চিতাগ্নিতে। কলকাতার ‘সংসদ’ অভিধানের ৫ম সংস্করণেও এ’ভুলতথ্য রয়েছে (সম্ভবতঃ, ঢা ব্য বাং অভি থেকে নেওয়া); এঁদের পূর্বতন তৃতীয়-চতুর্থ সংস্করণ পর্যন্ত এই ভুলটা ছিল না।তিনটি মাত্র ছাপার ভুল চোখে পড়েছেঃ গোস্ত-কাবার (পৃ ৭০), নাল-এ [খুরে রাগানো] (পৃ ১২৬) এবং হালুইকর (পৃ ২১৫)---তেমন কিছু নয়।(২) ‘অম্বর’ শব্দার্থ যখন ‘আকাশ’, তার সং.ব্যুৎপত্তি হয় ‘অম্ব্+রা(-ধাতু)+অ(ক)’। ‘সুগন্ধদ্রব্য’-অর্থে শব্দটি আরবিজাতঃ আম্বর (যা থেকে অম্বুরি তামাক ...)
(৩) কায়রোর ‘জামিউল আজহার’ (প্র. ৯৭০ খৃ.)কে বিশ্বের প্রাচীনতম বিশ্ববিদ্যালয় বলা হয়েছে (পৃ. ৮৬)। এটি অতি প্রাচীন ও সম্মানীয় পাঠস্থল হলেও তথ্যবিচারে মরক্কোর আল কারাউইন বিশ্ববি. প্রাচীনতম, প্রতিষ্ঠা ৮৫৯ খৃ.।
(৪) ‘খেয়াল’ গানের উদ্গাতা হিসেবে কোনো সুলতান হোসেনের নাম (পৃ.৫৮) কোত্থাও কখনও পাইনি। মধ্য-অষ্টাদশ শতকে দিল্লিসম্রাট মুহম্মদ শাহ্ রঙ্গিলার সভাগায়ক নিয়ামত খাঁন ‘সদারঙ্গ’ ও তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্র ‘অদারঙ্গ’-ই সঙ্গীতের এ’ধারার স্বীকৃত উদ্গাতা। পঞ্চদশ শতকের জৌনপুরের সুলতান হোসেন শার্কির কথা যদি বোঝানো হয়ে থাকে, তো তিনি তো জৌনপুরি রাগের স্রষ্টা হিসেবে খ্যাত, খেয়াল অঙ্গের উদ্গাতা হিসেবে নয়।
নাদিদা, জওজিয়ত, কায়েস, নাশিত, খিজালত, গনিমত, দুরদানা ... এ’রকম বহু বহু আ/ফা শব্দাবলী স্থান পেয়েছে এ’অভিধানে বাঙলায় যার ব্যবহার পাওয়া যায় না, না কোনো সাহিত্যিক উদা. দেওয়া আছে।
তা হোক, মানে-ধারে-জরুরতে একখানি শরতাজ কিতাব এ’খানি। বাঙলাভাষা নিয়ে নাড়াচাড়া করা যে-কারোর জন্যেই বেহদ্ জরুরি!!!
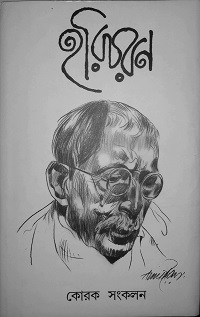 হরিচরণঃ কোরক সংকলন--সম্পাদনাঃ তাপস ভৌমিক; কোরক প্রকাশনা; বাগুইহাটি, কলকাতা-৫৯; প্রথম প্রকাশঃ জানু ২০১৬; ISBN: নেই।
হরিচরণঃ কোরক সংকলন--সম্পাদনাঃ তাপস ভৌমিক; কোরক প্রকাশনা; বাগুইহাটি, কলকাতা-৫৯; প্রথম প্রকাশঃ জানু ২০১৬; ISBN: নেই।
ধবধবে নাতিপৃথুলা কেতাবখানি হাতে নিলেই শ্রদ্ধা জাগে মনে, নামখানি দেখলে তো আরও! হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় নামখানির সঙ্গে এক সত্যযুগীয় ঋষির মূর্তি আসে কল্পনায়, বাঙলাদেশে যার তুলনা আচার্য সুনীতিকুমার বা দার্শনিক হীরেন্দ্রনাথ বা গুরু আলাউদ্দিন খানের মত গুটিকয় প্রবাদপ্রতিম ব্যক্তিত্বের সঙ্গে। অথচ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের তকমায় কিন্তু হরিচরণের সেই প্রবাদপ্রতিমত্ব গোড়াতে কিছুই জানা ছিল না, বা ধরা পড়েনি, গুরুদেবের জহুরী-নজরগুণটি ছাড়া। শান্তিনিকেতন ব্রহ্মচর্য আশ্রমের যুবক-শিক্ষকটিকে ডেকে রবীন্দ্রনাথ যেদিন তাঁকে এক বাঙলা অভিধান লেখার দায়িত্ব দেন, সলতে পাকানো সেদিন থেকেই কি শুরু হয়েছিল, তার আগে নয়? অর্থাভাবে স্নাতকপরীক্ষাটা যে তাঁর দেওয়াই হয়নি। ঠাকুরদের পতিসর সেরেস্তায় খাতা লিখতেন যুবক হরিচরণ। রবীন্দ্রনাথ দুটি কথা বলেই চিনতে পারেন ও শান্তিনিকেতনে ডেকে নেন হরিচরণকে, শিক্ষকতার কাজে। বাকিটা ইতিহাস।
কী প্রবল প্রতিকূলতার মধ্যে, শারীরিক (ক্রম-দৃষ্টিক্ষীণতা) প্রতিবন্ধকতা নিয়ে, কী অনন্য ধৈর্য, সংকল্প ও নিবেদিতপ্রাণতায় হরিচরণ প্রায় চার দশক ধরে সম্পূর্ণ একক প্রচেষ্টায় ‘বঙ্গীয় শব্দকোষ’ প্রণয়ন করেন, সেটা ইতিহাস, বা রূপকথাসম অবিশ্বাস্য গল্প---আমবাঙালীর অজানা নয়। বিশেষতঃ সৌমিত্রকৃত সেই অনবদ্য চরিত্রচিত্রণে ‘গুরুচরণ’ বাঙালীর ড্রইংরুমে-রুমে পৌঁছে গেছেন, পড়ার ঘরে ঘরে না হোক। দুঃখুটা সেখানেই। একে তো বুদ্ধদেব ‘একটি জীবন’-গল্পে অবাধ স্বাধীনতা নিয়েছেন কল্পনায়ঃ মূল ভাবটি ছাড়া বাস্তব হরিচরণের সঙ্গে গল্পের গুরুচরণের কোনো মিল নেই। সে-অর্থে কাহিনীটি অতিনাটকীয়। তা বেশ তো, এর মাধ্যমে যদি এক ঋষিকল্প মানুষ ও তাঁর কর্মকাণ্ডের সঙ্গে ‘ইতিহাস-বিস্মৃত’ বাঙালীর পরিচয় হয়, ক্ষেতি কী? কিন্তু এখানেই থেমে গেলে চলবে কেন? লিও তলস্তয়ের ইয়া ইয়া উপন্যাসের মত কেবল (গুণীজনে বলে বলেই) তারিফই করে যাবো (পড়িনি কিন্ত!)?! The Oxford English Dictionary-র প্রথম সংস্করণ বেরোতে শুরু করেছিল খৃ. ১৮৮৮তে, শেষ ১৯২৮-এ। হ্যাঁ, প্রথম সংস্করণের কথাই বলছি। এরপর ১৯৮৯-এ বেরিয়েছে এর বিশ-ভল্যুমের দ্বিতীয় সংস্করণ। এক সারস্বত-সম্পাদকমণ্ডলী নিয়ত OEDর পুষ্টিতে নিবেদিত। ভাষা যদি বহতা নদীর মত হয়, তার অভিধান স্থবির বসে থাকবে? ‘বঙ্গীয় শব্দকোষ’-এর ক্ষেত্রে কিন্তু এইটিই হয়েছে। ১৯৩২ সালে বিশ্বকোষকার নগেন্দ্রনাথের বাগবাজার প্রেস থেকে প্রথম ছেপে বেরোনোর পরে বিশ্বভারতীও এর এক সংস্করণ প্রকাশ করে, ১৯৪৫ সালে, পাঁচ খণ্ডে। ১৯৬৬-৬৭-সালে ভারতীয় সাহিত্য একাদেমি সেই যে দু’খণ্ডে প্রকাশ করেছিলেন এই অভিধান, ব্যাস, সেই শেষ। প্রথম প্রকাশের পর থেকে গত নব্বুই বছরে এই অভিধানের আর কোনো পরিমার্জিত সংস্করণ বেরোয়নি। আমরা কেবল, ‘আহা, হরিচরণ কী লিখে গেছেন কী লিখে গেছেন’ বলে ঢক্কানিনাদ করেছি---মাথায় তুলে রেখেছি, হাতে ধরে নিইনি। করিনি নিত্য-ব্যবহার, রয়ে গেছে লাইব্রেরির তাকে। এই শীতের দোশালাই কি হরিচরণ দিতে চেয়েছিলেন, রোজের গামছা নয়? কোনো লেখকই কি চাইতে পারেন তাঁর বই পাঠক শুধু মাথায় করে রাখুক কিন্তু পড়ুক না, দৈনন্দিন কাজে ব্যবহার করুক না? বিশেষতঃ, এক অভিধানকার? ১৯৭৪-এ’ প্রথম-প্রকাশিত বাংলা একাডেমী (ঢাকা)-র ‘ব্যবহারিক বাংলা অভিধান’ আজকের দিনে সর্বাধিক প্রচারিত ও বিক্রীত বাংলা অভিধান; তারপরেই সংসদের বাংলা অভিধানটির স্থান (শৈলেন্দ্র বিশ্বাসকৃত)। দু’টিরই পরের পর সংস্করণ বেরিয়ে বেরিয়ে প্রাসঙ্গিক হয়ে রয়েছে, তাই এত চাহিদা ও বিক্রি। হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় তোলা রয়েছেন তাকে, পরম শ্রদ্ধায়!
এ’সব চিন্তা ‘কোরক’-ই উস্কে দিল মাথায়। কী পরম মমতায়-যতনে বইটির নির্মাণ করেছেন সম্পাদক তাপস ভৌমিক মশায়---যতই সাধুবাদ দেই, কম পড়ে যাবে [এ’লেখার শিরোনামটিও তাঁর থেকেই না-বলে-নেওয়া]। আর কী সব লিখনের সমাহার এখানে ... কত কত যতনে গাঁথা রতনহারঃ আচার্য সুনীতিকুমার থেকে দার্শনিক হীরেন্দ্রনাথ দত্ত থেকে পুলিনবিহারী সেন থেকে প্রমথ বিশী-পরিমল গোস্বামী! বস্তুতঃ, হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় ও তাঁর প্রবাদপ্রতিম সৃষ্টি ‘বঙ্গীয় শব্দকোষ’-গ্রন্থের ওপর নানা বিদ্বজ্জনের নানা সময়ে লেখা ১৮টি নিবন্ধের সংকলনই হল এটি। পরিশিষ্টে হরিচরণের নিজকলমে জীবনস্মৃতিও রয়েছে এবং বুদ্ধদেবের অসামান্য গল্পটি। এর মধ্যে শ্রেষ্ঠ রচনার দর্জা দিই নবীন গবেষক/জীবনীকার দেবাঙ্গন বসুকে—তাঁর বারোপাতার ‘আকীর্ণ সৃষ্টির পথ’-এর পেছনের গবেষণা বারোমাসেরও বেশির, মনে হয়। অনেকগুলি চিঠি ও গ্রন্থপটের প্লেট মান বাড়িয়েছে সংকলনটির, যেমন তাঁকে লেখা রাজশেখর, সত্যেন বসু, রামানন্দ চট্টো, সুধীরঞ্জন প্রমুখের চিঠিপত্রগুলি। কয়েকটি ফোটোগ্রাফ রয়েছে---আচার্য জবাহরলাল ‘দেশিকোত্তম’ দিচ্ছেন, বা ক্ষীণালোকে নিবিষ্টিমনে লিখনরত হরিচরণ---ছবিগুলি মন কাড়ে---অসিত হালদারের প্রার্থনার স্কেচটিও।
লিটল ম্যাগাজিন বলতে সাধারণতঃ যে চিত্রটা মনে ভেসে ওঠে, ‘কোরক’-এর বইগুলির মান চিরকালই তার থেকে অনেক উপরে---বহিরঙ্গে, অন্দরে। বস্তুতঃ, কোরক, অনুষ্টুপ, অনীক-কে ‘লিটল’ বা ‘থার্ড’-ম্যাগাজিন আদৌ বলা যায় কিনা সেটাই বিচার্য (যদিও ‘এক্ষণ’ নিয়ে সেই দোলাচল কিন্তু কদাচ ছিল না)। চমৎকার ছাপাই-বাঁধাই এ’বইখানির। মুদ্রণপ্রমাদ চোখে পড়েনি। অনুপ রায়-কৃত প্রচ্ছদচিত্র এতো সুন্দর ভাবটি ধরেছে ঋষিবরের ... অন্দরে ইন্দ্রনীল-প্রকাশ-রমাপ্রসাদ-কৃত স্কেচগুলিও চমৎকার। তখনই প্রকাশিত/প্রচলিত সুবল মিত্র ও জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাসের বাঙ্গালা অভিধানদ্বয়ের সঙ্গে তুল্যমূল্য আলোচনায় লেখিকা অলিভা দাক্ষী দেখিয়েছেন হরিচরণ কতটা গভীরতর ছিলেন পুরাণ ও সংস্কৃত কাব্য-নাট্যের সন্দর্ভে। হরিচরণকে তাই প্রাচীন/সংস্কৃতপন্থী আখ্যায়িত করেছেন। ঠিক তার পরের প্রবন্ধই হল শ্রীসাহিদুল ইসলামের ‘বঙ্গীয় শব্দকোষ’-এ’ ঠাঁই পাওয়া আরবি-ফারসি শব্দের দীর্ঘ আলোচনা---বেশ উপভোগ্য।
স্যামুয়েল জনসন তাঁর Dictionary of Eng Language প্রসঙ্গে বলেছিলেন, ‘... a large work is difficult because it is large’. হরিচরণের কীর্তি কতটা large সে তো গ্রন্থটি হাতে নিয়েই বোঝা যায়। আর difficult? নাঃ, মনে হয়না আদৌ difficult ছিল কাজটা তাঁর কাছে। নৈলে, ... কবি অমিয় চক্রবর্তীর কথাতেই বলি, ‘মনে হয় যেন বইয়ের পাতায় সকালের আলো এসে পড়েছে’!
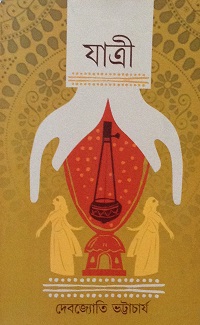 যাত্রী—দেবজ্যোতি ভট্টাচার্য; সৃষ্টিসুখ প্রকাশন; বাগনান, হাওড়া; প্রথম সংস্করণঃ ডিসেম্বর ২০১৫; ISBN 978-81-932146-5-7
যাত্রী—দেবজ্যোতি ভট্টাচার্য; সৃষ্টিসুখ প্রকাশন; বাগনান, হাওড়া; প্রথম সংস্করণঃ ডিসেম্বর ২০১৫; ISBN 978-81-932146-5-7
তবে যে বললে, তুমি সে ঘরের মালিক নও ?
সে ছিল আরেক যাত্রীর কথা, সে ‘কবি’। কিশোরকালে ‘বসন’-এর দুঃখে কেন্দেছি হপ্তাভর, উপন্যাসপাঠান্তে হপ্তাভর ঘোরঘোর ভাবে। আর, এই ‘যাত্রী’ তো পড়াশেষ করে উঠলুম মাত্র কাল মাঝরাতে। না, তিনবছর ধরে ঠুকরে ঠুকরে পড়া নয়, এক নিঃশ্বাসে সারাদিনব্যাপী নিবিড়পাঠ। এর একটা আলাদা আনন্দ আছে। সেই ঘোর কাটিয়ে, দেখি, এ’ গ্রন্থ-সমালোচনাখানি লিখে উঠতে পারি কিনা।
বস্তুতঃ, দেবজ্যোতি ভট্টাচার্য বা তাঁর ‘যাত্রী’ উপন্যাসের সঙ্গে ‘পরবাস’-এর পাঠককুলের নতুন করে পরিচয় করিয়ে দেবার কিছু নেই, কারণ ধারাবাহিক প্রকাশকালে এ’-উপন্যাস আম-পাঠকের উৎসাহ-ভালোবাসা অর্জন করে নিয়েইছে ইতোমধ্যে। তা’লে ফের এ’ ‘সমালোচনা’ কেন? তার প্রধান কারণ, ইদানীংকালের এক শ্রেষ্ঠ উপন্যাস ‘পরবাস’-এর সারা অঙ্গ জুড়ে রয়েছিল তিন বৎসর ধরে, এবার একস্থানে তার এক নজর হৌক। যাঁরা এখনও উপন্যাসখানি পড়েননি বা খেই হারিয়েছেন দীর্ঘচলনে, তাঁরাও একবার ফিরে দেখুন। আর দ্বিতীয় কারণটি নিছক ব্যক্তিগত। এ’হেন এক উপন্যাসের সঙ্গে এই কলমচির নামটাও জড়িয়ে থাকুক ‘পরবাস’-এর পাতায়, না-হয় সমালোচকরূপেই, সেটাও চেয়েছি বইখানির ক্রেতা-পাঠকের সামান্য অধিকারের একটু ঊর্ধে উঠে। পালায় যে প্রহ্লাদ সাজে, সে-ই কেবল তাঁর ভজনা করে, যে কংস সাজে সে নয়?
আরেকটি অসুবিধেও আছে। সুরলোকের যে অসীম সমুদ্দুরে লেখকের পূর্ণ অবগাহন, তার পাড়েই তো মাত্র বসে আছি, সে-পানি অঞ্জলিভরে ছিটিয়েছি মস্তকোপরি, গলাজলে নামারও ভরোসা হয়নি। তবে? তবে এ’-চাপরাশ দিলে কে যে ফস্ করে কলম বাগিয়ে ...। উত্তর আপনারা দেবেন, আমার কাছে নেই।
উপন্যাসের সমালোচনায় কিন্তু গল্পটি বলে দেওয়া চলে না, তা’লে আগামী পাঠকের প্রতি বঞ্চনা হয়। আবার গল্পটির গা না ছুঁয়ে সমালোচনা লেখাই বা যায় কী করে? এই ভয়েতেই ৪৭-সংখ্যায় আফসার আহমেদ সাহেবের সেই অনন্য উপন্যাসটির পরে বিগত পাঁচ বছরে আর কোনো বাঙলা-উপন্যাসের সমালোচনা লিখতে বসিনি। ‘যাত্রী’ ব্যতিক্রম।
তার যাত্রা শুরু কবে হয়েছিল? সে কি বাপ হরকান্ত যখন “অন্তরে বাহিরে জ্যোতি ...” পদ বেন্ধেছিলেন, তখন? না, তারও অনেক অনেক আগে সুদূর খোরাসানে মরমীকবি জামি-সাহেব বেঁধেছিলেন প্রেমের পদ? বা, তারও পূর্বে? আর, শেষ? শেষ যে এখানে নয়, সে তো গ্রন্থ-সমাপ্তিতে উনি লিখেই দিয়েছেন, এ’খানি মাত্র প্রথম খণ্ডের পরিসমাপ্তি।
এক দরিদ্র গ্রাম্যকবির পুত্র, যে স্বীয় প্রচেষ্টায় বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষায় শীর্ষস্থান হাসিল করে, এবং তা করেও, শুধু নাড়ির টানে ফিরে আসে ঘরের মাটির কাছে, সুরের কাছে। এটা করতে তাকে ত্যাগ করতে হল প্রেমাস্পদাকে, যদিও মাদৃ-র ভালোবাসার আসল তাকতটা বুঝতে তাকে ঠেলে যেতে হয় উপন্যাসের প্রায় শেষাবধি, যখন সে ধরা পড়ে গেছে ... হল্ট, না, আরও বেশি এখানেই বলে দিলে ...
নায়কচরিত্রটি বড্ড বেশি সন্ত-সন্ত হয়ে পড়েনি? সব ভালো সব ভালো দোষ নেই একরত্তিও? ক্রোধ কিছু থাকলেও কাম নেই কোনো, যদিও পরিবেশ তার পরিপক্ক হয়ে উঠেছিল ঘটনাপ্রবাহে বেশ কয়েকবারই। কেবল প্রথমদিকপানে ঐ গানের আসরের ঠিক বাইরেই সেই স্বর্গ নেমে আসা ও দুটি শরীর ... (পৃঃ ৭১) একটু অবোধ্য ও অবাস্তব রয়ে গেল। অবিশ্যি, স্বর্গ নেমে আসার অর্থ যদি একেকজনের কাছে একেক হয় তা’লে বলার কিছু নেই। উপন্যাসের সারা অঙ্গ জুড়ে চরিত্রদের অত ইংরিজি বাক্য ব্যবহার বেমানান হয়েছে, এমনকি শোভন-প্রভাত বা শোভন-ফরিদার মধ্যেকার বাক্যালাপেও। হ্যাঁ, চরিত্রদের মুখের বুলি বড় বেশি মার্জিত হয়ে পড়েছে।
নায়ক তো হল, নায়িকা কে উপন্যাসটার? না মাদৃ, না মরণ, এ’উপন্যাসের নায়িকা কি হেমলতা দিদিমণি, যিনি কাহিনীর সারা অঙ্গ জুড়ে অন্তর্লীন থেকে উপন্যাসটির চালিকাশক্তি রয়ে গেছেন? আর ‘বিবেক’ ভুবনদাদা? সে না থাকলে চাবিটা কুড়িয়ে হাতে দিত কে? সত্যি, নায়কের দরমাবেড়ার আশ্রমে তালাচাবি পড়ার রূপকখানি অনবদ্য হয়েছে, দেবজ্যোতির জাত চেনায়।
‘ভাবের গান’ যেমন পরতে পরতে খোলে, ওপরের খোলখানি খুলতে পেলেই ভেতরের শাঁসে দখল, ‘যাত্রী’-ও তেমনি যত এগিয়েছে জারিয়েছে ততই। ‘পর্ব-এক’ এর গা-গরম করা না থাকলে ‘পর্ব-দুই’-এর ঐ পরিপক্কতা আসে? ধারে-ভারে-গভীরতায় দ্বিতীয় পর্ব প্রথমের চাইতে ৪০% এগিয়ে আছে। কেবল, প্রথম খণ্ড যতই এগোচ্ছিলো পরিসমাপ্তির দিকে, মন চুলবুলে, শেষটা কী হবে, শেষটা কী হবে? মিলনান্ততা উপন্যাসখানির কমতি না আভরণ হয়েছে সেটা সাহিত্যতাত্ত্বিকরা বিচার করুন, আমরা আমপাঠককুল পড়ে তো আনন্দ পেয়েছি। শেষলাইনের ঐ ‘এ-ই, কী হচ্ছে’ টা তো বাঙালীর চিরকালীন অতি প্রিয় উত্তু-সুচির ঢঙে হয়ে গেছে। আর, এখানেই আকাঙ্খাটা আরও জোরদার হল, ‘যাত্রী’তে এক অসামান্য চলচ্চিত্রের উপকরণ আছে। চিত্রসত্ত্বটা, দেবজ্যোতিবাবু, একটু বেয়েচেয়ে দ্যান’খনি। অপাত্রে না পড়ে।
উপন্যাসের ঊর্দ্ধে ‘যাত্রী’-র এক আর্কাইভাল ভ্যালুও আছে, যেটা প্রণিধানযোগ্য। ভাওয়াইয়া, চটকা, পাল্লাগান ইত্যাদি ইত্যাদির এতরকম উল্লেখ ও উদাহরণ রয়েছে এই বইয়ে যে হঠাৎ রেফারেন্স হাঁটকাতে এবার থেকে শক্তিনাথ/সুধীরের পাশাপাশি ‘যাত্রী’-কেও রেখে দিতে হবে। স্বল্পায়াসে বড় কিছু করা যায় না, স্বেদ ঝরাতে হয় ভালোই,---পড়তে পড়তে সেই বোধটারই পুষ্টি হয়।
নতুন প্রকাশনালয় ‘সৃষ্টিসুখ এল এল পি’-র বইয়ের কথা আগেও এই কলামে লিখেছি [‘আঠারো পর্ব’, সং ৫৭]। চমৎকার কাজ এনাদের। এই যে এনারা কভারটিকে হার্ড না রেখে সেমিহার্ড রাখেন, পেপারব্যাকের ফিলিংটা সঠিক আসে, ‘পেঙ্গুনীয়’! যে তিনটি মাত্র মুদ্রণপ্রমাদ চোখে পড়েছে, উপেক্ষণীয় তা। ছাপাই-বাঁধাই চমৎকার। অতি সুন্দর প্রচ্ছদ এঁকেছেন শ্রীপার্থপ্রতিম দাস। ‘অভ্র’-দিয়ে লেখা বইটি (যেমন এই ‘পরবাস’ ওয়েবম্যাগও)---তাই বইটির ক্রেডিট পেজে অভ্রের স্রষ্টা মেহদী হাসান খানসাহেবের প্রতি লিখিত কৃতজ্ঞতাজ্ঞাপনটি বড্ড ভালো লাগলো।
শেষে দেবজ্যোতির প্রতি এই নিবেদনঃ সব লেখকেরই কলমটাই কেবল নিজের হয়, দেহ-মন-আত্মা পুরোটা নিজের নয়। কিন্তু সেই দেহমনের সালোকসংশ্লেষ করে মস্ত বটবৃক্ষখানি যে নির্মল অম্লজান ছড়িয়ে দেয় ঘরে-দুয়ারে-দিকচক্রবালে, সেটাই প্রাণের শক্তি! সে-ঘরেরও তুমি মালিক হয়েছ, সে-দুয়ারেরও, সে-জমিরও। জমিদারের দেখা তাই পাওয়াই গেছে, হুকুমও হয়েছে জারি।
আমরা নিছক ফলাহারি মাত্র।
 মহাদেবী রচনা সঞ্চয়ন (হিন্দি)—সম্পা. বিশ্বনাথ প্রসাদ তিওয়ারী; সাহিত্য অকাদেমী; রবীন্দ্র ভবন, নঈ দিল্লী-১; প্রথম প্রকাশঃ ১৯৯৮, বর্তমান সংস্করণ/পু.মুদ্রণ ২০১২; ISBN: 81-260-0437-1
মহাদেবী রচনা সঞ্চয়ন (হিন্দি)—সম্পা. বিশ্বনাথ প্রসাদ তিওয়ারী; সাহিত্য অকাদেমী; রবীন্দ্র ভবন, নঈ দিল্লী-১; প্রথম প্রকাশঃ ১৯৯৮, বর্তমান সংস্করণ/পু.মুদ্রণ ২০১২; ISBN: 81-260-0437-1
১৯২৩-২৪ নাগাদ বুদ্ধদেব বসু যখন ‘কল্লোল’ পত্রিকায় লিখতে শুরু করলেন, বয়স তাঁর ষোল পুরোয়নি। ‘কল্লোল’-এর পরিধি ছাড়িয়ে তাঁর প্রভাব বঙ্গসাহিত্যে আরও কতদূর বিস্তৃত হয়েছিল, ইতিহাসে লেখা আছে তা। আর এরই বছর চার-পাঁচের মধ্যে তাঁর ঠিক সমবয়সী এক তরুণীর হিন্দি কবিতা ছেপে বেরোয় ইলাহাবাদ থেকে। হিন্দি-উর্দু সাহিত্যে ইলাহাবাদ তখন চাঁদের হাট! ‘প্রবাসী’-সম্পাদক রামানন্দ-সুহৃদ চিন্তামণি ঘোষের (ইন্ডিয়ান প্রেস—ভারতে রবীন্দ্রনাথের ‘গীতাঞ্জলী’ এঁরাই ছাপেন প্রথম) ‘সরস্বতী’-পত্রিকা ইতোমধ্যেই হিন্দি-সাহিত্য/সাময়িকের ভগীরথরূপে দেখা দিয়েছে। চিন্তামণির আহ্বানে যুগপুরুষ মহাবীরপ্রসাদ দ্বিবেদীজী এ’পত্রিকা সম্পাদনের দায়িত্ব কাঁধে তুলে নিয়েছেন (১৯০৩-২০), শুরু হয়ে গেছে আধুনিক হিন্দিকাব্যের দ্বিতীয় অধ্যায়ঃ ‘দ্বিবেদী যুগ’ (১৯০০-১৯১৮)! নাগরী অক্ষরে হিন্দোস্তানী ভাষার সাহিত্যকর্মপ্রকাশ থেকে শুরু করে তার আত্মা ও অবয়বের মানচিত্র এঁকে দিতে অভিজাত, রুচিশীল ‘সরস্বতী’-পত্রিকার যুগান্তকারী ভূমিকা থাকলেও কোথাও যেন এক নিগড় অনুভূত হওয়া শুরু হয়ে যায়—তৎসম ভাষায়, পরিশীলনে। তাই প্রথম-বিশ্বযুদ্ধপরবর্তীকালীন হিন্দি সাহিত্যে, ‘প্রতিবাদ’ বললে বড্ড কড়া হয়ে যাবে, এক ‘অন্যরকম’ শৈলীর প্রকাশ দেখা দিতে থাকেঃ ১৯১৮এ প্রকাশিত জয়শঙ্কর প্রসাদজী (১৮৯০-১৯৩৭)-র ‘ঝর্ণা’ কাব্য প্রকাশনা দিয়ে এই ধারার শুরু, নামটা দিলেন প. মুকুটধর পাণ্ড্যে। ক্রমে এই ‘অন্য’ধারার কাব্য-আন্দোলনের স্তম্ভগুলি গড়ে উঠতে থাকেঃ জয়শঙ্কর প্রসাদজীর সাথে সাথে সূর্যকান্ত ত্রিপাঠী ‘নিরালা’ (১৮৯৬-১৯৬১), সুমিত্রানন্দন পন্ত (১৯০০-৭৭), ও ঐ তরুণী আজকের ‘মীরা’ মহাদেবী বর্মা (১৯০৭-৮৭)-র কলমে! শুরু হয়ে যায় আধুনিক হিন্দিকাব্যের শ্রেষ্ঠসুষমাময় অধ্যায় ‘ছায়াবাদ’ পর্যায় (১৯১৪-৩৮)। হ্যাঁ, কবি দীনকরজী, বচ্চনজী, মাখনলাল চতুর্বেদী প্রমুখও এই ধারার কবি বলেই মান্য।
লক্ষৌর নিকটবর্তী জেলা ফাররুখাবাদের যে প্রাচীন কায়স্থ পরিবারে মেয়েটির জন্ম, ১৮৫৭-র মহাবিদ্রোহে প্রতিবাদী ভূমিকার জন্য শাস্তি পেতে হয়েছিল তাদের। আন্দামান কারাগারে হত মহাবিদ্রোহের অন্যতম মন্ত্রগুরু ফজলে-হক-খয়রাবাদী (আজকের কবি জাবেদ অখতরের প্র-প্রপিতামহ)-র সখ্যতা ছিল মহাদেবীর প্রপিতামহের সঙ্গে। মহাদেবী নামটিও পিতা দিয়েছিলেন বড় আদরে, বংশে তিন-চার প্রজন্মের মধ্যে প্রথম কন্যাসন্তান জন্মেছে বলে!
মহাদেবী! শিক্ষারাম্ভ, যখন ইন্দৌরে ছিলেন কিছুদিন। চারজন গৃহশিক্ষকঃ এক পণ্ডিতমশায়, এক মৌলবীসাহেব, একজন ছবি আঁকার ও গানের মাস্টারমশায় চতুর্থজন। নয়বছর বয়সে ঠাকুর্দা বিয়ে দিয়ে দেন পুণ্যলাভার্থে, কন্যে অবশ্য সেদিন চাকুম-চুকুম মেঠাই চেখেছে ব্রতকে বুড়োআঙুল দেখিয়ে, আর ‘বর এসেছে....বর এসেছে’ ডাক শুনে আর-সকলের সঙ্গে ছুটেছে বর দেখতে। বর ফার্স্ট কেলাসের ছাত্র! পরের দিন শ্বশুরবাড়ি গিয়ে এমন কান্না জোড়ে সে-বালিকা যে শ্বশুরমশায় সেই যে ‘এই রৈল তোমাদের মেয়ে’ বলে ঠক করে বসিয়ে দিয়ে গেলেন, আর ও’মুখো হননি। মহাদেবী ততদিনে অমিতাভ বুদ্ধের প্রেমে নিমজ্জিত ... তিনিই তাঁর জীবনের ধ্রুবতারা ... মীরার কৄষ্ণের মত! আশ্চর্য, পতি ডাঃ স্বরূপনারায়ণ বর্মার সঙ্গে আজীবন তাঁর বন্ধুত্ব রয়ে গিয়েছিল। মহাদেবীর উপর্যুপরি অনুরোধ সত্ত্বেও তিনি পুনর্বিবাহ করেননি। মহাদেবী তখন ভিক্ষুণী হবার বাসনায় নৈনিতালের এক বৌদ্ধসঙ্ঘের দ্বারে উপস্থিত। হননি, সেখানে গান্ধীজীর সঙ্গে দেখা ও তাঁর ডাকে সাড়া দিয়ে গ্রামশিশুদের পড়ানোর জন্যে ঘরে ফিরে এলেন বলে।
কবি-লেখক কেহই স্বয়ম্ভূ হন না, প্রভাব সকলের ওপরই আছে, থাকে। ঈশ্বরচিন্তায় নিবেদিতা মহাদেবী বর্মা কী করে ‘ছায়াবাদ’-এর মত এক আধুনিক কাব্য-আন্দোলনের পুরোধা হতে পারেন—ভাবনার বিষয়ঃ যে-আন্দোলন ভাবে-ভাষায়-প্রকাশে একদিকে সংস্কৃতের নিগড় ভাঙে তো ওপাশে ঈশ্বরকে দেখে মানুষের চোখে। প্রকৃতিপ্রেমের পাশাপাশি সৃষ্টির প্রতি গভীর বিস্ময় (স্রষ্টার প্রতি ততটা নয়)—ছায়াবাদের অন্যতম প্রধান লক্ষণ। পন্তজীকে তো ‘হিন্দিসাহিত্যের ওয়ার্ডসওয়ার্থ’-ই বলা হয়। প্রসাদ-পন্ত-নিরালার ওপর বাঙলাসাহিত্যের প্রবল প্রভাব, কিন্তু আশ্চর্য, মহাদেবীর ওপর একেবারেই নয়। মহাদেবীজী যখন লেখেন “তুম অসীম বিস্তার জ্যোতি কে, ম্যায় তারক সুকুমার /তেরী রেখারূপহীনতা, ম্যায় জিসমেঁ সাকার” [‘রশ্মি’] ... তার প্রকাশে-ছন্দে মাতোয়ারা হয়ে যেতে হয়, আর পণ্ডিতেরা খুঁজতে বসেন কোথা থেকে পেলেন উনি এই ভাব এই ভঙ্গী?
মহাদেবী পরমকরুণাময়কে দেখেছিলেন মানুষের মধ্যেই প্রকাশিত। তাই মনুষ্যজীবনের প্রতিদিনের প্রত্যুষ থেকে নিশা—চারিপ্রহরের চারকাব্য লিখে গেছেন ‘যামা’ সংকলনেঃ ‘নীহার’ (১৯৩০ খৃ.), ‘রশ্মি’ (১৯৩২ খৃ.), ‘নীরজা’ (১৯৩৪ খৃ.), ‘সান্ধ্যগীত’ (১৯৩৬ খৃ.)। ‘নীহার’-এ’ লেখেন “ম্যায় অনন্ত পথ মেঁ লিখতি জো /সস্মিত সপনোঁ কী বাতেঁ...”, তো ‘নীরজা’-য় “বীণ ভী হুঁ মৈঁ তুমহারী রাগিনী ভী হুঁ...” তো ‘সান্ধ্যগীত’-এর পরিপক্কতায়ঃ “ক্যোঁ মুঝে প্রিয় হোঁ ন বন্ধন /বন গয়া তম-সিন্ধু কা, আলোক সতরঙ্গী পুলিন সা...”। এ’সব অবশ্য আমার সমালোচনা পড়েশুনে লেখা, কারণ কাব্যের অত গভীরে ঢুকে তাঁর এই ক্রমপুষ্টতা বুঝি, হিন্দিসাহিত্যে অত এলেম নেই এই সমালোচকের। কবিতা পড়ে ভালো লাগে তাই পড়ি, আপনাদের সঙ্গে গল্পসল্পের ঢঙে ভাগ করে নিই। একটা বিষয় অবশ্য অবাক লাগেঃ মহাদেবী বর্মার সমবয়সী বাঙালী কবি-সাহিত্যিক সতীনাথ (জ. ১৯০৬), আশাপূর্ণা (জ. ১৯০৯), বিষ্ণু দে (জ. ১৯০৯) বা সুফিয়া কামালের (জ. ১৯১১) সঙ্গে একই সঙ্গে কত মিল ও অমিল তাঁর! অসহযোগ-আইন অমান্য আন্দোলনের কালে পরাধীনদেশের একই রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে লেখা শুরু তো এঁদের ... তবুও ... এ’বিষয়টার আলোচনা বর্তমান নিবন্ধে আঁটবে না, যাহোক। গান্ধীজীর কাছে ফিরে ফিরে গেছেন মহাদেবী, প্রভাবিত হয়েছেন। রবীন্দ্রনাথ প্রয়াগে এসেছেন (১৯৩৩ খৃ.), তরুণী মহাদেবী এসে বসেছেন পায়ের কাছে, পরে শান্তিনিকেতনেও। সে তো ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে পারস্পরিক স্নেহ-ভক্তি। রবীন্দ্র রচনার ছায়া মহাদেবীতে পড়েনি, যেটা পন্তজী বা নিরালাজীর ক্ষেত্রে অত্যুচ্চ।
মহাদেবী বর্মার কবিতার সঙ্গে আবাল্য পরিচয় থাকলেও ওনার ছোটগল্প আগে পড়িনি, এক ‘চীনী ফেরিওলা’ ছাড়া (মৃণাল সেনের ছবি ‘নীল আকাশের নিচে’), যদিও সাহিত্যের এই ক্ষেত্রেও ওনার খ্যাতির কথা শুনে থেকে পড়ার ইচ্ছেটা জমে ছিল। ইচ্ছেটা বলবতী হল পরবাস-৫৮-এ তাঁর এক গল্পসংকলনের সমালোচনা পড়ে। খুঁজে খুঁজে সাহিত্য অকাদেমীর মন্দির মার্গের বুকস্টোর থেকে বর্তমান সংকলনটির ক্রয় ডিসে.২০১৪এ’ এবং মুগ্ধতা! এমন চমৎকার গেটআপের একখানি সংকলন, এক মহাকবির, হাতে নয়, বুকে রাখার মতঃ শুধু তাঁর ছয়খানি কাব্যগ্রন্থ থেকে সুচিন্তিত চয়নই নয়, ‘রামা’ ‘ভক্তিন’ ‘গুঙ্গিয়া’ ‘গিল্লু’-র মত তাঁর তেরোটি ছোটগল্প ঠাঁই পেয়েছে এখানে, সঙ্গে তাঁর সমালোচনা-নিবন্ধগুলিও। কতবার যে পড়লাম ছোটগল্প ‘ঘীসা’ ও ‘নীলকণ্ঠ মোর’! আজকাল যে ‘দলিত’ বা ‘নারীবাদী’ রচনা নিয়ে এতো কচাকচি, কত অনায়াসে মহাদেবী তাঁদের গল্প শুনিয়েছেন ‘রামা’ বা ‘সুভদ্রা’তে। তাঁর সাথীকবির কথা কী চমৎকার লিখেছেন--‘নিরালা ভাঈ’। নিরালাজীকে উনি রাখী পরাতেন, পন্তজীকেও। পথের টানে হরিদ্বার থেকে পায়ে হেঁটে বদ্রীতীর্থে ঘুরে এসেছেন, দু’বার। সে অবিশ্যি বয়সকালে। সংখ্যায় কিন্তু বহু লেখেননি উনি, দীর্ঘ সময় ধরেও নয়। ১৯৩০-৩৬-এ লেখা ‘যামা’ ও ‘দীপশিখা’ (১৯৪২ খৃ.) কাব্যগ্রন্থের জন্যে অর্ধশতাব্দী পরে ১৯৮২তে পেলেন জ্ঞানপীঠ পুরস্কার। সে তো প্রণম্যা হারপার লি দিদিমণিও আজীবন ‘মকিংবার্ড’ ছাড়া আর কিছু লেখেননি, সম্মানের শিখর ছুঁয়েছেন। সমর সেনও ১৯৪৬-র পরে আর কবিতা না লিখেও আজীবন কবি হিসেবেই বেশি স্মরণীয়, সাংবাদিকের চেয়েও। সংখ্যা ও দৈর্ঘ্য দিয়ে কবে আর সৎ সাহিত্যের বিচার হয়েছে, না কি সেটা হওয়া উচিৎ?
জানা গেছে, মহাদেবী বর্মাজী অসাধারণ আবৃত্তিও করতেন এবং এক বৈঠকী ব্যক্তিত্ব ছিলেনঃ কোনো ‘কবি-সম্মেলন’এ তাঁর উপস্থিতি যেন চারচাঁদের উদয় ঘটাতো। এ’প্রসঙ্গে আমার এক ব্যক্তিগত না-প্রাপ্তি আছে। ১৯৮৪তে চাকুরি পেয়ে কানপুর গেলাম ট্রেনিং নিতে। সেখানে হঠাৎ শোনা গেল মহাদেবী বর্মাজী আসছেন এক ‘কবি-সম্মেলনে’ যোগ দিতে! হিন্দিভাষী সহকর্মীদের চেয়ে আমিও কম উৎসাহিত হইনি। বাল্যকাল থেকে কত রাতে তাঁর ‘নীহার’ /‘রশ্মি’ কাব্য পড়তে পড়তে সে-বই বুকে নিয়ে ঘুমিয়ে পড়েছি, মাথায় তাঁর সস্নেহ হস্তপ্রলেপ অনুভব করতে করতে (নাম দু’খানি আমার ঠাকুরমা ও বৌদিদিমণির কিনা!)। কিন্তু বিধি বাম। অনুষ্ঠান শনিবার, যে-সন্ধ্যার ট্রেনটিকিট কাটা আমার নেক্সট ট্রেনিঙে দিল্লি যাবার। যাইতেই হইবো। এবং হৈলও। টেরেনিং তো সারাজেবনভর কম লইলাম না, কিন্তু মহাদেবীজীকে সামনাসামনি একবার দেখবার-শোনবার ও পদধূলি নেবার সুযোগ জম্মের মত হারিয়ে গেল। আফশোষ। আফশোষ। আরেকটা আফশোষঃ শুনেছিলাম মহাদেবী বর্মা আপনমনে চমৎকার চমৎকার ছবি আঁকতেন জলরঙে, পেন্সিল-স্কেচও, বিশেষতঃ, বৃদ্ধাবয়সে। কোত্থাও দেখতে পাইনি কভু। সাহিত্য অকাদেমীর মত সংস্থা যদি তাঁর এ’হেন এক সংকলনে কয়েকখানি ছবি জোগাড় করে পাঠকদের সামনে তুলে ধরতে না পারে তো আর কে পারবে?
পঁচিশ বছরের এক সুন্দরী, উচ্চশিক্ষিতা তরুণী যখন লিখেছিলেন, “চুকা পায়েগা কৈসে বোল, মেরা নির্ধন সা জীবন তেরে বৈভব কা মোল (মূল্য)” [‘রশ্মি’, ১৯৩২] ... তাঁর প্রভাব যেন বহুদূর বিস্তৃত হবার জন্যেই! রাজাগোপালাচারীর দৃষ্টিতে তাঁর তুলনা ‘দক্ষিণের মীরা’ মহিলা-কবি ও অবতার আন্ডালের সঙ্গে। প্রভাকর মাচবে ও জগদীশ গুপ্তের ন্যায় পণ্ডিত-সমালোচকের কলমে জ্যেষ্ঠতর সরোজিনী নায়ডুও এসেছেন। কৈ, আমি তো তেমন কিছু বুঝতে পারিনি। প্রভাব কি অমন দুয়ে দুয়ে চার হয় গো? আজ যখন কোনো বাঙালী কবির লাইন পড়িঃ ‘এ শুধু করুণা নয়, এ শুধু শুশ্রূষা নয়, হয়তো আরোগ্য একে বলে’ ... কোথায় যেন মহাদেবী বেজে ওঠেন!!!
(পরবাস-৬২, মার্চ - এপ্রিল, ২০১৬)






